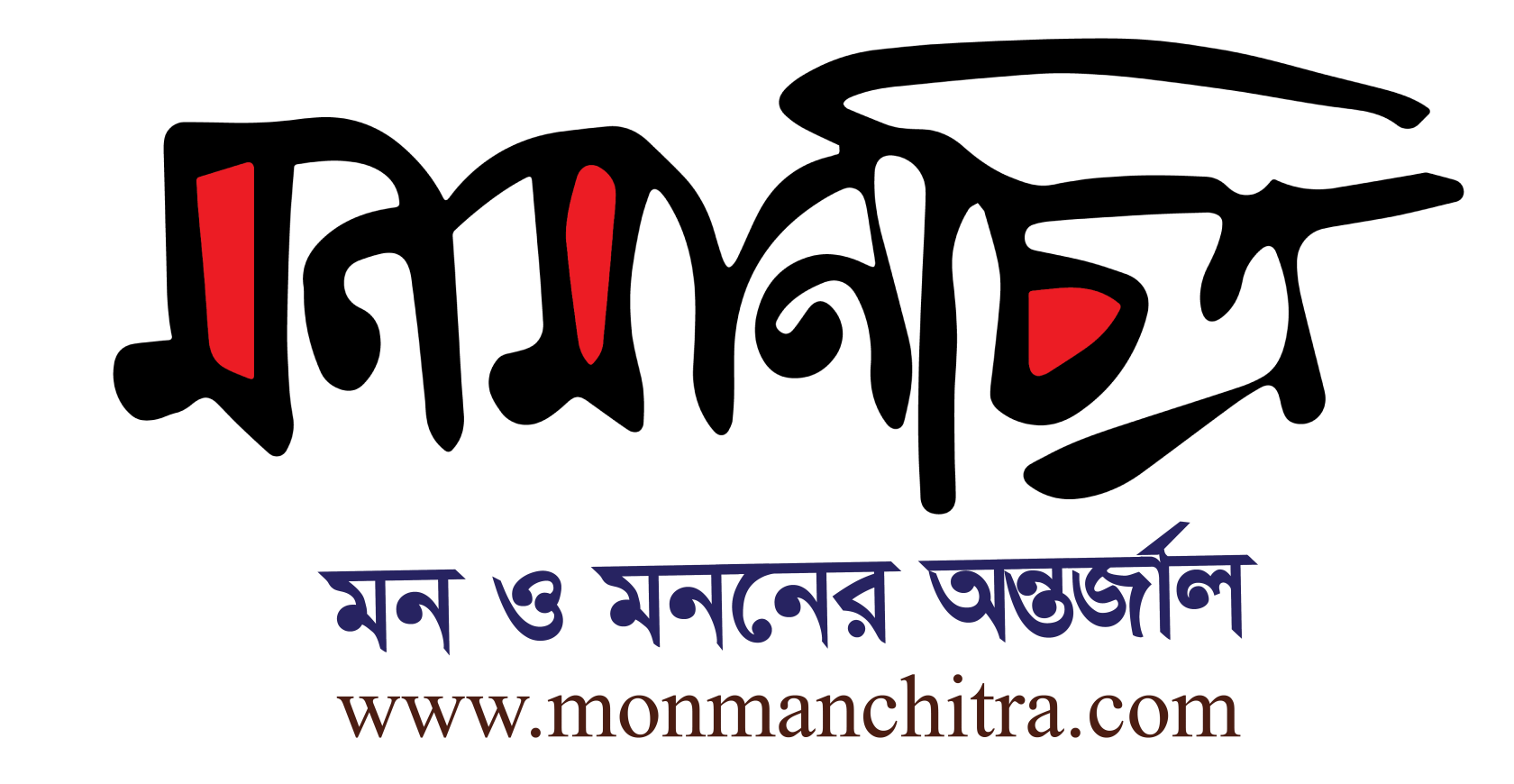খালেদ হামিদী
রোববার মৃত্যুবার: নিবিড় সমীক্ষা
অনেক লেখক তাঁদের ডিটেইল বা গল্পে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের জন্য পরিচিত। কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে চার্লস ডিকেন্স, যিনি তাঁর স্মরণীয় চরিত্র এবং সামাজিক ভাষ্যের জন্য সুবিদিত। বিস্তারিত গল্প বলার জন্য অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ভার্জিনিয়া উলফ, লুসি মড মন্টগোমেরি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং মার্সেল প্রুশ্তসহ কয়েকজন। চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট, আ ক্রিসমাস ক্যারল, ডেভিড কপারফিল্ড এবং গ্রেট এক্সপেক্টেশনের মতো উপন্যাসগুলি চরিত্র এবং পরিবেশের বিশদ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, যা প্রায়শই তাঁর সময়ের সামাজিক সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করে। দ্য ব্রন্টে বোনেরা (শার্লট, এমিলি এবং অ্যান) প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় আখ্যান তৈরি করতে আবেগ এবং চরিত্র বিকাশের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। ‘দ্য লেটার রিভিউ’ কথার মাধ্যমে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখিত লেখকদের দক্ষ হিসেবে বর্ণনা করে এবং তাঁরা পাঠককে তাঁদের গল্পে ডুবিয়ে রাখার জন্য বিস্তারিত বর্ণনা ব্যবহার করেন বলে অভিমত প্রকাশ করে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ফেলুদা গল্পের জন্যও পরিচিত, যেখানে গোয়েন্দা এবং তার পারিপার্শ্বিকতার বিশদ চিত্রায়ণ, সেইসাথে তার সহকর্মী তোপসে এবং লালমোহন গাঙ্গুলির চরিত্রগুলিও বিশদভাবে রয়েছে। আরও অনেকের মধ্যে আমাদের লেখক মহীবুল আজিজ সমৃদ্ধ এবং পাঠকচিত্তে প্রভাববিস্তারী গল্প লেখার জন্য বিস্তারিত বিবরণের নিজস্ব শক্তি কাজে লাগান যা, বলা বাহুল্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং মামুন হুসাইনের ডিটেইলস থেকে ভিন্ন। ইলিয়াসের গল্পে উপগল্পও অন্তর্ভুক্ত, যে-রীতি মহীবুলের নয়।
অপরদিকে গী দ্য মোপাসাঁর গল্পের মতো শুরুর আকস্মিকতা এবং শেষের নাটকীয় সমাপ্তি আমরা মহীবুলের কিছু গল্পেও লক্ষ করি। এই রীতি অবশ্য প্রায় প্রচলিতই হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও আন্তন চেখভের গল্পের ধরনে আলোচ্যমান বইয়ের কিছু গল্পের ঘটনাও স্বাভাবিকভাবে ঘটে এবং শেষ হয়, যা বাস্তব জীবনের মতোই। তবে এ ক্ষেত্রে চেখভের কথাসাহিত্যের মতোই, তাঁর অনুবর্তী না হলেও (উভয়ে দুই ভিন্ন দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির যে বিশেষ রূপকার তা মনে রেখেই বলা হচ্ছে), মহীবুলের গল্পের আরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ বাস্তবসম্মত পরিস্থিতি চিত্রণ, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতাভুক্ত নানা অনুঘটনার মধ্যেও জীবনের গভীর সত্য উন্মোচন। তিনি সমাজের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অস্তিত্বের সংকট-সমস্যা (মধ্যরাতের লিখন), প্রত্যাশা এবং নিরাশা অনুবাদ করেন। তাঁর গল্পগুলোতে সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত-নিম্নতমবিত্ত সকলের জীবনযাত্রা বাঙময় হয়। তবে অধিকাংশতই তাঁর বিচরণ বঞ্চিত-দলিতদের অঞ্চলেই।

মহীবুল চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্ব, লৌহকঠিন গল্পে দলিত মধ্যবিত্তেরও আতঙ্ক এবং আবেগ খুবই মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতি এমন একাগ্রতাযোগে অনুবাদ করেন যে তা পাঠককে গল্পের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে উল্লেখিত গল্পে দুই পুরুষের ধর্ষণপ্রচেষ্টার সম্মুখীন নিরার মনোজাগতিক অবস্থা বর্ণনাকালে গল্পকার তাঁর সাথে, এবং পাঠকও, জীবন বদল করেন বলে অনুভূত হয়। রোববার মৃত্যুবার নামগল্পে ১৫ বছরের শিশু টুনির ধর্ষিত হওয়ার সময়কার মানসপট উন্মোচনের ক্ষেত্রেও লেখক-পাঠকের একই বিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ-গল্পের শেষে মহীবুল জগদীশ গুপ্ত’র কাছে আঙ্গিক-ভাবনার ঋণ স্বীকার করেছেন। জগদীশের পাঁচ পৃষ্ঠার দিবসের শেষে গল্পটিতে ৫ বছরের ছেলে পাঁচু তার বাবার সাথে নদীতে স্নান করতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে কুমীরের শিকার হয়। আর টুনি মা-বাবার অনুপস্থিতিতে বলাৎকৃত ও নিহত হয়। উভয় মৃত্যুই ভয় ধরিয়ে দেয়। বিস্ময়কররূপে এ-দুটি গল্পেই এই দুই শিশু নিজেদের মৃত্যুর আগাম ঘোষণা দেয়। রোববার মৃত্যুবার ১৯ পৃষ্ঠার তীব্র সংবেদী গল্প। এতে টুনিদের অব্যবহিত প্রতিবেশ চিত্রায়ণে যেমন প্রাগুক্ত ডিটেইল বা বিবরণ পাঠককে টুনির ঠিকানার সঙ্গে একাত্ম করে তেমনি প্রতারণামূলক উপায়ে অবৈধভাবে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত চক্রের বর্ণনা তাদের ওই আস্তানায় বুঝি বাস্তবিকই নিয়ে যায় পাঠককে। এখানেই জগদীশের গল্পটির সাথে এই গল্পের পার্থক্য যা মহীবুলের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখে।
আমরা জানি, আন্তন চেখভের গল্পগুলোতে লেখক নিজে খুব কম কথা বলেন, বরং তাঁর চরিত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের গল্প বলে। তাদের কথা, আচরণ, এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকেই গল্পের মূল বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন ধারার এবং অনুস্মৃতি ঘরানার কাছাকাছি হলেও বিলেত-প্রবাসের অভিজ্ঞতা মহীবুলের আত্মজবানীতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আলোচ্যমান গ্রন্থভুক্ত পাঁচটি গল্পে। এই পর্যায়ে, ব্রিটিশ জীবনাচরণের গল্পে পশ্চিমা সংস্কৃতির রূপায়ন পাঠককে ক্লিক করে। ফিওনা ভেলভেডিয়ার গল্পে স্প্যানিশ ফিওনা ভেলভেডিয়ারকে ব্রিটিশ বন্ধুর সাথে পার্কে ও অন্যত্র অনেকবার নিবিড়ভাবে আলাপরত দেখেন গল্পের বাঙালি কথক। তিনি ধরেই নেন যে ফিওনা ঘনিষ্ঠ যুবকটিকেই বিয়ে করবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে অন্য তরুণের সাথে দেহ বিনিময় করতে দেখে অবাক হন। এ নিয়ে অনেক ভাবনার পর তিনি, ফিওনা জনকে কেন বিয়ে করবে না জানতে চাইলে উত্তর মেলে: ‘আরে, ওর তো দাঁড়ায়-ই না! একটি আকস্মিক উদ্ধারপর্ব সম্পূর্ণই ক্যাম্ব্রিজের একটি ঘটনার গল্প। শীতের শুরুতে বরফ হতে থাকা ক্যাম নদীতে আটকে যাওয়া একটি রাজহাঁসকে উদ্ধারের অনুপুঙ্খ বিবরণ গল্পকারের আনুভূমিক অভিজ্ঞতার বিস্ময়কেই প্রতিষ্ঠিত করে। আরেক গল্পে জানা যায়, ইংল্যান্ডের রানিই সব রাজহাঁসের অধিকর্তা। তাই অতো প্রশাসনিক তৎপরতা। তবে সেই হাঁসকে উদ্ধারের মূল প্রেরণাদাতা বৃদ্ধার নিঃসঙ্গতাও এখানে লক্ষণীয়। বাকি তিনটি গল্পে যথাক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যেও রাজনৈতিক বিভেদ (ক্যাথারসিস এবং একটি সন্ধ্যা), দেশের ঐতিহাসিক এক অপরাধীর সন্তরূপী ছদ্মবেশ ও ক্যামোফ্লেজ (অন্য রূপ) এবং বিলেতের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে সংশ্লিষ্টদের অজ্ঞাতসারে একজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তনের ( মোবারক আলী’র সংক্ষিপ্ত বিদেশবাস) বিষয়গুলি আমাদের কথাসাহিত্যে নতুন, বলা যায়।
লৌহকঠিন গল্পে নিরা শেষ পর্যন্ত বলাৎকৃত হওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় তালাবদ্ধ স্টিলের অন্তর্বাসে নিম্নাঙ্গের প্রতিরক্ষাহেতু। যদিও এতে সৈয়দ শামসুল হকের খেলারাম খেলে যা উপন্যাসের জাহেদাকে মনে পড়ে, যার উরুসন্ধিস্থলের উপরকার অসম্ভব জটিল ও দুর্বোধ্য অনেক গিঁট খুলতে পারে না বাবর। বস্ত্রখণ্ডের এমন আবরণ বাবরকে ব্যর্থ করে দেয়। যদিও, সে ঠিক ধর্ষক ছিল না। তবুও নিরায় এসে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন পুঁজিবাদের সহায়ক পুরুষতন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা ভয়ংকরতর আস্ফালনেরই প্রতিক্রিয়া, যা, বলা যায়, কল্পনাতীত। অবশ্য ঢের আগে থেকে আফ্রিকী কুমারীদের যোনিমুখ ভিন্ন পদ্ধতিতে রুদ্ধ রাখার সমালোচনায় নারীবাদী লেখক-চিন্তকগণ সরব হন, তাও বহু আগে। কিন্তু মহীবুল দেখান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্তেও নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের আগ্রাসন সামন্তীয় বর্বরতাকেও কীভাবে হার মানিয়ে চলেছে। পাশাপাশি উল্লেখ্য, নিরার ঐ ধর্ষকামী যুবকদের (মূল ও সহায়ক চরিত্র মিলে) জৈবিক লোলুপতাও মহীবুল অনুবাদ করেন যথার্থরূপে, শেক্সপীয়রীয় কৃতিত্বযোগে। ওথেলো নাটকের খলনায়ক ইয়াগো স্মর্তব্য, নাট্যকারের যে চরিত্রপাঠ ও চিত্রায়ণ এখনও বিস্ময়কর।
এই বইয়ে মহীবুল আজিজ হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি চিহ্নিতকরণের, যা একই সঙ্গে কৌতুক ও বিষণ্ণতা তৈরি করে, চেকভীয় পদ্ধতির পরিবর্তে মোপাসাঁ-অঙ্গীকৃত নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও পরের নিম্নবিত্ত শ্রেণি এবং বিত্তহীনের দুর্দশা চিত্রণের দায়বদ্ধতা অনুভব করেন। এ জন্যই প্রেমিক শোভনলালের বিপন্নতা গল্পে ধাঙড়পট্টির তরুণ শোভনলালের পেশার পরিচয় পেয়ে হতবাক প্রেয়সী বীণা অনতিক্রম্য শ্রেণিদূরত্বে নিজেকে সরিয়ে নেয়। যুগান্তকারী রুশ কথাসাহিত্য যে মহীবুলের প্রেরণাস্থল তা তো বলাই বাহুল্য।
আর, মহীবুলের ভাষা কেমন? তিনি জেমস জয়েসের পরীক্ষামূলক ভাষারীতির দ্বারা কি অনুপ্রাণিত যে জয়েস শব্দার্থের নিরীক্ষার সমান্তরালে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশ এবং রূপক-প্রতীকের গভীর ব্যবহারসহ ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যিক উপাদান ও আধুনিকতাবাদী পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে স্ট্রিম অফ কনশাসনেস বা চিৎস্রোত নামধেয় আখ্যানকৌশল ব্যবহার করেন? না, অধিকাংশতই না। তবে সমৃদ্ধি অর্থে জয়েসের (এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়াং ম্যান এবং ইউলিসিস-এর মতো কাজগুলোতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট) মতো মহীরুহের ছায়ার ঠিক বাইরেও নন মহীবুল। তবে তিনি অন্য গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাসেও কথা বলেন, সাধারণত, দীর্ঘ যৌগিক বাক্যে, যা অনুরূপ না হলেও কমলকুমার মজুমদারকে মনে পড়িয়ে দেয় যাঁর ভাষা বিষয়ে ফরাসি বাক্যগঠনরীতির কথা বলা হয়। এ-প্রসঙ্গে কেউ কেউ স্মরণ করেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যরূপ। যদিও, জয়েসের মতো কমলকুমারও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটান। সেই সাথে কিছু স্বতন্ত্র শব্দের পাশাপাশি চিত্ররূপময়তা ও রঙের বৈচিত্র্যও সুলভ তাঁর কাজে, বিশেষত, অন্তর্জলী যাত্রা উপন্যাসে। মহীবুল তাঁরও অবিকল অনুসারী নন। তবুও তরুণ কথাসাহিত্যিকদের চোখে মহীবুল আজিজের ভাষা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক ঘরানার। আলোচ্যমান গল্পগ্রন্থে, তাঁর অন্যান্য গল্পে-উপন্যাসেও কথ্য কিংবা আঞ্চলিক ভাষার দুয়েকটা সংলাপ যে নেই তা নয়। তবে তিনি ন্যারেশনেও কথ্য বা উপভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার সামান্যতা (ইংরেজি কমননেস অর্থে) বিঘ্নিত করেন না। কেননা প্রমিত ভাষা জনগণেরই ভাষা, জোসেফ স্ট্যালিন যেমন বলেনঃ ‘ভাষা উপরিকাঠামো থেকে পুরোপুরি আলাদা। উপস্থিত সমাজের অভ্যন্তরে ভাষা এই বা ঐ, পুরনো বা নতুন কোনো ভিত্তিরই ফল নয়; পরন্তু তা সংশ্লিষ্ট সমাজটির ইতিহাসের সমগ্র বিকাশধারার, বহু শতাব্দি-ব্যাপ্ত বিবিধ ভিত্তির ইতিহাসের, উৎপন্ন ফল।…এর সৃষ্টি হয়েছিলো কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, গোটা সমাজের, গোটা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর প্রয়োজন পূরণের জন্য।’ (ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে; শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও; পীযূষ দাশগুপ্ত সম্পাদিত)
শুধু জয়েস, কমলকুমার এবং মহীবুল আজিজের মতো লেখকদের ভাষার সম্পূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন পাঠকের insightfulness বা অন্তর্দৃষ্টি।
বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়ঃ বইটির বাঁধাই এবং প্রকাশক মঈন ফারুককৃত (চন্দ্রবিন্দু’র স্বত্বাধিকারী) প্রচ্ছদ চমৎকার। আরেকটু সচেতন হলে কিছুটা অস্বস্তিকর মুদ্রণপ্রমাদগুলি এড়ানো যেত।
************************