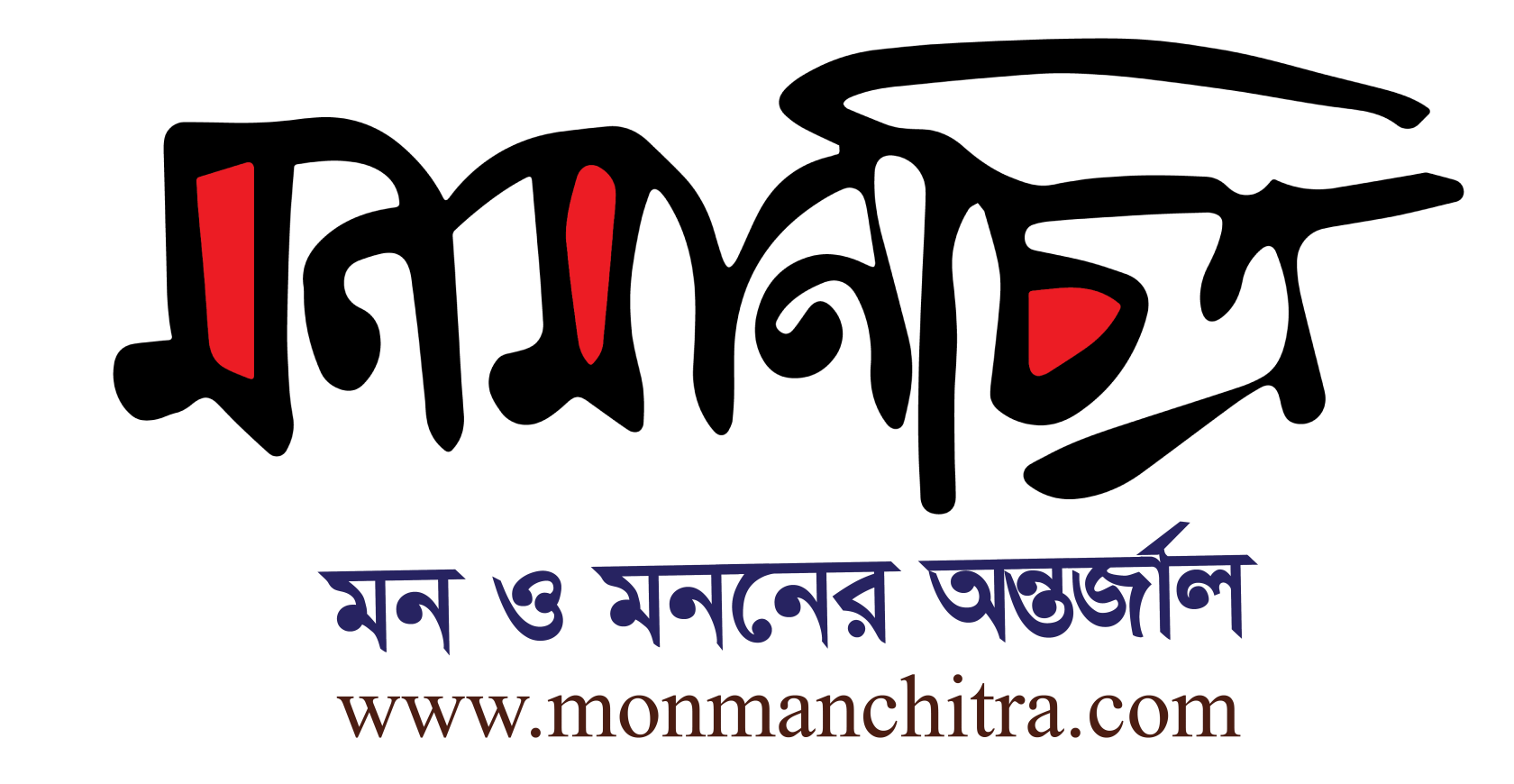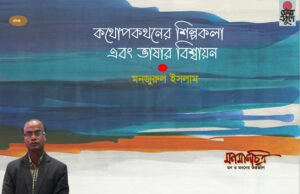শাহ মো. জিয়াউদ্দিন
আর্য অনার্য যুদ্ধ
আর্য-অনার্য যুদ্ধ” বলতে ভারতী উপমহাদেশে প্রাচীন কালে আর্য এবং অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বা সংঘর্ষকে বুঝায়। অনেকের মতে এই যুদ্ধ বা ঘটনাটি কাল্পনিক। আবার কেউ কেউ মনে করেন এটা একটি বিবর্তনের ধারা। তবে এই বিষয়টি সত্য যে, আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশের আদি অধিবাসী নন। এই ধারণা অনুযায়ী, আর্যরা সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসে । তখনই ভুমি দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অনার্য জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতে আর্যরা জয়ী বা সন্ধি করে অনার্যদের সাথে। এর ফলে আর্য সংস্কৃতি ভারতে প্রসার লাভ করে । আর্য সংস্কৃতির মাধ্যমে অনার্য সংস্কৃতিটাও আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়। আবার ঐতিহাসিক ধারনা মতে বলা হয় কিছু কিছু অনার্য সংস্কৃতি বিলুপ্তও হয়ে যায়। তবে, এই ধারনাটি বা তত্ত্বাটি বিতর্কিত এবং ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে এটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত নয়। আর্য-অনার্য যুদ্ধ” ধারণাটি মূলত ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক বিতর্কের একটি অংশ। এই ধারণাটি বেশ কিছু বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত । আর্যদের আগমনের পুর্ব ভারতী উপমহাদেশে দ্রাবিড়, কোল, মুন্ডা, এবং সাঁওতাল সহ বিভিন্ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, যাদের অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং আর্যরা ভারতে আসার পর অনার্য জনগোষ্ঠীর সাথে ক্ষমতা, ভূমি, এবং সংস্কৃতির আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ বা সংঘাত সংঘটিত হয়ভ এই যুদ্ধ বা সংঘাতের সপক্ষে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া না গেলেও যুদ্ধ বা সংঘাত হয়েছিল এটা সত্য । “আর্য” শব্দটি একটি জাতি বা ধর্মকে বোঝায় না, বরং এটি একটি ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী বা সংস্কৃতি নির্দেশ করে। যা অনার্যদের সাথে মেলে না। আর্য অনার্য সংঘাতটি নানা ধরনের উপাখ্যান রয়েছে। কেউ কেউ রাম-রাবণের যুদ্ধকে আর্য-অনার্য যুদ্ধের একটি রূপক হিসেবে দেখেন, যেখানে রাম আর্য এবং রাবণ অনার্যদের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা হয়। আর্যরা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারত উপমহাদেশে এসেছিল বলে মনে করা হয়।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় , আর্যরা ছিল মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী যাযাবর গোষ্ঠী। আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করে। একটা পর্যায়ে এসে সিন্ধু উপত্যকা এবং গাঙ্গেয় সমভূমিতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস আরাম্ভ করে। আর্যরা যে ভারতীয় উপমহাদেশের না তার নানা প্রমান আছে। তারা তাদের সাথে সংস্কৃত ভাষা এবং বৈদিক সাংস্কৃতি নিয়ে আসে। যা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ পরিণত হয় এবং গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে নেয়। কারণ এই সংস্কৃতিটা অনার্যদের প্রচলিত সংস্কৃতি থেকে অনেক ভিন্ন। অনেকের মতে আর্য সংস্কৃতিটা একটু উন্নত ছিল। আর্যদের আগমন নিয়ে কিছু বিতর্ক ও গবেষণা রয়েছে। কিছু গবেষক মনে করেন যে, আর্যরা বহিরাগত ছিল না, বরং ভারতীয় উপমহাদেশেই তাদের উদ্ভব হয়েছে। তবে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, তারা মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিবাসন করেছিল। অনেকেই আবার একে ইন্দো-আর্য অভিসান বলে থাকেন। একটা সময় মানুষের ধারণা ছিল যে, আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে এই ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হয়। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে ভারতীয় উপমহাদেশে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছে আর্যদের ভারত আগমনের পর থেকেই। আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ও ধর্মবিশ্বাস আলোচনা পর্যালোচনা করলে আর্য সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য সমাজে ধর্ম ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে জন্ম নিয়েছিল দুটি নতুন ধর্মমত- জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। সংস্কৃতে আর্য শব্দের অর্থ সৎ বংশজাত ব্যক্তি। ম্যাক্সমুলার, স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি পন্ডিতের মতে,আর্য একটি ভাষা জনগোষ্ঠীর নাম। যারা আর্য ভাষায় কথা বলে তারাই আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। ফিলিপ্পো স্যাসেটি নামের ফ্লোরেন্সের একজন বণিক গোয়াতে পাঁচবছর অবস্থান করছিলেন (১৭৮৩-১৭৮৮ খ্রিঃ) । তারপর তিনি মন্তব্য করেন , প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপের প্রধান কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্যের কথা । কিন্তু অনেক গবেষক এমন প্রশন্ন তুলেছেন যে , আর্যরা যদি বহিরাগত হয়, তাহলে তাদের আদি বাসভূমির কথা গুলো কেন বেদের মত কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি? এসব যুক্তির মাধ্যমে কিছু ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতবর্ষ। কারণ বেদ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন গ্রন্থ। যা ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।
কিন্তু কোনো কোনো পন্ডিত এ মতের বিপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিগুলো হলো, ১. বেদে উল্লেখিত গাছপালা ও পশুপাখির নাম থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সপ্তসিন্ধু অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে তারা ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করায় ঐএলাকার গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে তাদেরই প্রথম পরিচয় ঘটে। এ কারণেই এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বেদও রচিত হয়েছিল ঐ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ২. এমনও হতে পারে যে আর্যরা দীর্ঘকাল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বাস করার ফলে তাদের আদি বাসভূমির সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল বলেই বেদে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৩. নদী স্রোত দিয়ে আর্যদের উত্তর-পশ্চিম ভারতয় আদিবাসী হিসাবে বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে ৩৯ টি নদীর নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে ঋগে¦দেই পাওয়া যায় ২৫টি নদীর নাম, কিন্তু গঙ্গা নদীর নাম শুধুমাত্র একবার উল্লেখিত হয়েছে। আর্যরা ভারতের আদিবাসী হলে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে অভিপ্রয়াণ ঘটে থাকলে গঙ্গা নদীর সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা । সে ক্ষেত্রে গঙ্গার নাম বারবার উল্লেখিত হওয়া উচিৎ ছিল। ৪. ঋগে¦দের মত কোন গ্রন্থ অন্য দেশে রচিত হয়নি বলেই বলা যাবে না যে ভারতই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। এমনও হতে পারে যে ভারতে আসার আগে বেদের মত গ্রন্থ রচনা করার মত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উন্নয়ন অনার্যদের ঘটেনি। ৫. তাছাড়া বলা যায় যে ভারতবর্ষ আর্যদের আদি বাসভূমি হলে তারা গোটা ভারতবর্ষে আর্য বসতি ও সংস্কৃতি বিস্তার করতো। কিন্তু উত্তর ভারতের বেশ কিছু এলাকা এবং দক্ষিণ ভারত এখনো আর্য সংস্কৃতির বাইরে রয়েছে। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে সাওতাল কোল মুণ্ডাসহ বিভিন্ন আদিবাসীদের প্রভাব এখনো ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত। যা কি না আদি ভারতীয় সংস্কৃতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। (চ) সংস্কৃত ভাষায় তালব্য বর্ণের (ন, ং, ৎ) প্রাধান্য দেখা যায় যা ইউরোপীয় অন্য কোন ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় নেই। পন্ডিতেরা মনে করেন যে, ইউরোপ থেকে ভারতে আসার পর দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবে এরকম হয়েছে। ৬. বৈদিক সাহিত্যে সিংহের উল্লেখ থাকলেও বাঘ ও হাতির উল্লেখ নেই। আর্যরা ভারতের আদিবাসী হলে ভারতের এই দুটি প্রাণীর নামের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে অবশ্যই থাকা উচিৎ ছিল। এসব যুক্তির বলে পন্ডিতেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতের বাইরে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আর্যরা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিল। তাঁদের যুক্তিগুলো হলো, (ক) আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সাতটি ভাষার মধ্যে পাঁচটি এখনও ইউরোপের ভাষা, শুধু সংস্কৃত ও পারসিক ইউরোপের বাইরের। ইউরোপে গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি আর্য ভাষাগুলোর যে রকম ঘন সন্নিবেশ দেখা যায় ভারতে তা দেখা যায় না। ইউরোপে আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার আধিক্যের কারণে পন্ডিতেরা মনে করেন যে, আদিতে আর্যরা ইউরোপেই বাস করতো।
(খ) বৈদিক সাহিত্যে ওক, উইলো, বার্চ ইত্যাদি গাছ এবং ঘোড়া, গাভী, ষাঁড়, শুকর প্রভৃতি জন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচ্য দেশের জন্তু হাতি, বাঘ, উট ইত্যাদির কোনো উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নেই। (গ) অধ্যাপক গাইলস মনে করেন যে, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ। আদি ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় সমুদ্রের কোন উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে আর্যদের আদি বাসভূমি কোন দ্বীপে বা সমুদ্র তীরে ছিল না। তারা যে সব গাছপালা ও পশুপাখির নাম উল্লেখ করেছে সেগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের। আর্যরা যখন স্থায়ীভাবে বসবাস এবং কৃষিকাজ শুরু করে। তখন তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া ও ভেড়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন ছিল। তাহলে মনে করতে হবে যে আর্যদের আদি বাসস্থান এমন একটি স্থানে ছিল যেখানে কৃষি ও চারণযোগ্য পরিবেশ কোনটিরই অভাব ছিল না । সেখানে কৃষিযোগ্য জমি, ঘোড়ার জন্য বিস্তীর্ণ স্ত্রেপ এবং ভেড়া চরানোর জন্য উঁচু জমি সবই ছিল। এসবের দিকে লক্ষ্য রেখে ড. গাইলস বলেন , বর্তমান অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অঞ্চলকেই আর্যদের আদি বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক ব্র্যান্ডেস্টাইন মনে করেন যে, উরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরঘিজ স্ত্রেপ অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদিবাসভূমি। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি শব্দতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রথম দিকের ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীতে কোন পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ স্ত্রেপ ভূমিতে আর্যদের আদি বাসভূমির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জমি, গাছপালা এবং জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে শুষ্ক স্ত্রেপ ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলীর পরিবর্তে জলাভূমির স্পষ্ট।
স্বাদেশিকতাবাদের সমর্থকেরা বংশগতিবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল গুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কয়েকটি পুরনো ডিএনএ-গবেষণায় ইন্দো-আর্য অভিপ্রয়াণের তত্ত্বটি নিয়ে প্রশ্ন ঊঠে। ২০১৫ সাল থেকে যদিও বংশগতিবিদ্যা গবেষণা “বৈপ্লবিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে , তারা প্রমান করেন যে , স্ত্রেপ পশুচারকেরা পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় অভিপ্রয়াণ করেছিল। এর ফলে অনেক বিজ্ঞানী যাঁরা ব্রোঞ্জ যুগে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রয়াণ নিয়ে সংশয়ী বা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতেন তাঁরাও মত পরিবর্তন করেন।
ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও ভাষার পরিবর্তন সাধন করতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বাদেশিকতাবাদীরা। মূলধারার গবেষকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উপমহাদেশের ছোট ছোট সংস্কৃতির ও ভাষার পরির্বতন হয়েছিল অভিজাতদের আধিপত্য বিস্তার ও ভাষা স্থানান্তরণের মাধ্যমে। ছোটো ছোটো গোষ্ঠীও একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করতে পারে, যখন এক অভিজাত পুরুষ গোষ্ঠী ছোটো ছোটো স্থানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মিশে যায় এবং সেই সব ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী অভিজাত গোষ্ঠীটির ভাষা গ্রহণ করে। এই ঘটনার ফলে উত্তর ভারতে একটি ভাষা স্থানান্তরণের ঘটনা ঘটেছিল। এরপর সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈদিক-ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে ইন্দো-আর্য ভাষাগুলি আরও ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পরম্পরাগুলি (“ছোটো পরম্পরাসমূহ”) ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের “মহৎ পরম্পরা”-র সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যায়। ফলে সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যান ধারণাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। যার জন্য ফলে হিন্দু সংশ্লেষণও ত্বরান্বিত হয়। যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী পরম্পরা “আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার স্থানীয় জনপ্রিয় পরম্পরাগুলি”কে আত্মীভূত করেছিল। আর্যরা মুলত সনাতন ধর্মের নানা প্রথার প্রবর্তন করে। তবে আর্যরা যে ভারতীয় উপমহাদেশে সভ্যতার প্রাচীন ধারক বাহক নয় তার প্রমান পাওয়া যায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা থেকে। তার কারন হল খৃষ্টপুর্ব ৫৬০০ হরপ্পা মহেঞ্জোধারো সভ্যতার প্রমান পাওয়া যায়। অপর দিকে আর্যদের আগমন খৃষ্ট পুর্ব ১৫০০ অব্দে। হরপ্পা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার একটি প্রাচীন শহর । হরপ্পা বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অবস্থিত। হরপ্পা শহরটি প্রায় ১৫০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই শহরটি সিন্ধু নদের উপনদী রাভি নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯২১ সালে হরপ্পা শহরটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। অপরদিকে মহেঞ্জোদারো সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার একটি প্রাচীন শহর, যা বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত। মহেঞ্জোদারো শব্দের অর্থ “মৃতের স্ত্রূপ”। এই শহরটি সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত। ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদারো শহরটি আবিষ্কৃত হয়। মহেঞ্জোদারো শহরটি তার পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, স্নানাগার এবং উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার জন্য পরিচিত।
মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিবকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সিন্ধুর এই সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ সঠিক জানা যায় নি এর বিলুপ্তির বিষয়ে ঐতিহাসিকদের নানা ধরনের মতবাদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় দীর্ঘদিন ধরে চলে এবং একসময় এখানকার অধিবাসীরা এই স্থান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। কেন এই স্থান পরিত্যাগ করে তার নানা ব্যাখ্যা থাকলেও বহিঃশত্রুর আক্রমণে তারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় , তারও প্রমান পাওয়া যায় । আবার অনেকেই মনে করেন যে , প্রাচীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবসা, জলবায়ু পরিবর্তনও সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ হতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম দিক হতে ক্রমাগত নানা বিদেশী শত্রুর আক্রমণের ফলেই হরপ্পা সভ্যতার বিনাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে আর্যদের অভিযানের কথা বলা হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলেস্ মন্তব্য করেছেন যে ”ব্যাাবিলনের সম্রাট হামুরাবির আমলে আর্যভাষী জনগোষ্ঠী পারস্য ও আফগানিস্তান দখল করে উত্তর-ভারতের কৃষ্ণবর্ণের জনগোষ্ঠীকে বিধ্বস্ত করে সমগ্র অঞ্চলে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে।” উল্লেখ যে, সিন্ধু অঞ্চলে যে কুঠারের প্রতিচ্ছবি নির্মিত সীলমোহরটি পাওয়া যায়, সেটি বৈদিক আর্যদেরই ছিল কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।
সর্বোপরি, হরপ্পা সভ্যতার উত্থানের ন্যায় এদের বিলুপ্তির কাহিনী আজও রহস্যাবৃত। তবে মহেঞ্জো-দারোর সমাপ্তির বিষয়টিতে যা জানা যায় , তা অনেকটা নাটকীয় এবং আকস্মিক ঘটনার মত ছিল। মহেঞ্জো- দারোতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আক্রমণকারীরা আক্রমণ করেছিল, যারা শহরটি আক্রমণ করে লুটপাট করে সম্পদ নিয়ে নেয় । তারপর তারা শহরটি ছেড়ে চলে যায় বলে ধারনা করা হয়। কারণ আক্রমনকারীদের আক্রমনে যারা মারা গিয়েছিল। তাদের মৃতদেহ ঐই স্থানে পড়েছিল কেউ সমাহিত করে নাই। বা লাশ গুলো কেউ সরিয়ে নেয়নি। এই ঘটনা থেকে ধারনা করা হয় যে , মহেঞ্জোদারোর প্রায় অধিকাংশ মানুষকেই মেরে ফেলছিল আক্রমনকারীরা। আক্রমণকারীরা কারা ছিল তা অনুমান করা হয় তবে সুনিদির্ষ্ট ভাবে কাউকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে এই ঘটনাটি সময় এবং স্থানের দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, থেকে সিন্ধু অঞ্চলে উত্তর থেকে আসা ( ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী বলে মনে করা হয়) লোকজনই । যা আর্য জনগোষ্ঠিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই আক্রমনের ঘটনা যেমনটি প্রাচীন বইগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ঋগ্বেদে বর্ননায় নবাগতরা আদিবাসীদের “প্রাচীর ঘেরা শহর” আক্রমণ করেছে বলে বলা আছে। বইটিতে আক্রমণকারীদের প্রধান যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র এর দুর্গ ভাঙার মতো ঘটনার বর্ননা দেয়া হয়। একটি অভুত্থানের মাধ্যমে মহেঞ্জদারোর পট পতন হয়। তবে, একটি বিষয় সুস্পষ্ট: তা হল অভ্যুত্থান লাভের আগেই শহরটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে চলে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক দুযোর্গ হয়েছিল বার বার। বড় ধরনের বন্যায় এর বিশাল অংশ একাধিকবার ডুবে গিয়েছিল। বাড়ি গুলি নির্মাণের বয়স হয়ে ছিল অনেক । তাই ঘরবাড়ি গুলি ক্রমশ নিম্নমানের হয়ে পড়ে। তাছাড়া এখানে জনসংখ্যাও আধিক্য লাভ করে। অর্থ্যাৎ বসবাসের স্থানের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী হয়ে যায়। তাছাড়া চূড়ান্ত আঘাতটি হঠাৎ করেই এসেছিল তাই শহরটি নগর কর্তা রক্ষা করতে পারেননি ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ধারনা করা যায় যে, আর্যরা ভারতে প্রবেশে সময় এই সভ্যতাটা ধ্বংস করেছিল। আরেকটি সুত্র থেকে জানা যায় যে , আধুনিককালে গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বের প্রাচীন জাতিগুলি একে অপরের সহিত বিছিন্ন ছিল না। সেই সুপ্রাচীন কালে স্থলপথে ও জলপথে মানবজাতির গমনাগমন ছিল এক ণগর থেকে অন্য নগরে । সুতরাং সেই যুগে প্রতিবেশী জাতিগুলির সহিত সিন্ধু উপত্যকার জনগণের যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, চিত্রমূলক বর্ণমালা প্রভৃতি-মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলি হরপ্পা, সিন্ধু সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। এর ফলে মনে হয় পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। এখানকার সভ্যতা এতই উন্নত ছিল যে , তা নিজেদের আয়ত্ব করার জন্য আর্যরা এই দুইটি শহর দখল করে ভারতে প্রবশে করে। আর প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে শহর দুটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
সাওতালী ইতিহাসের গবেষনা অনুযায়ী , আর্য ( ইন্দো-ইরানীয় আরইয়া) হচ্ছে একটি প্রাচীন জাতিবিশেষ। আর্যরা প্রাচীনকালে ইন্দো-ইরানীয় জনগোষ্ঠীর। এই জনগোষ্ঠি নিজেদেরকে দেওয়া একটি স্ব-পদবি হল আর্য। যা দিয়ে অ-ইন্দো-ইরানীয়” বা অ-ইরানী” বা “অনার্য” ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করে দেয়া হয়। আর্য হওয়ার ধারণাটি জাতিগত নয়, বরং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত। যদিও এর মূলধাতু *য₂বৎ(ু)ষ্টং (‘নিজ দলের সদস্য’, বহিরাগতদের সঙ্গে তুলনা করে) হল খুব সম্ভব আদি-ভারতীয়-ইউরোপীয় ভাষা থেকে এসেছে। এছাড়াও ভৌগোলিক অঞ্চলের নামেও যেমন আর্যবত্ত যেখানে ইন্দো-আর্যদের সংস্কৃতির ব্যুৎপত্তি । ইন্দো-আর্য এবং ইরানীয়দের জন্ম হয়েছিল প্রত্ন-ইন্দো-ইরানীয় সংস্কৃতি থেকে। ২১০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে মধ্য এশীয় চারপাশ এন্দ্রোনোভা সংস্কৃতিতে প্রোটো-ইন্দো-ইরানীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। ঐ অঞ্চলে বর্তমান রাশিয়া এবং কাজাখস্তান অবস্থিত। পরবর্তীতে ১৮০০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আরাল সাগরের চারপাশে তা এন্দ্রোনোভো সংস্কৃতি হিসেবে আরও বিকশিত হয়। এই প্রোটো-ইন্দো-ইরানীয়রা দক্ষিণ দিকে অভিপ্রায়ণ করে ব্যাকট্রিয়া-মারজিয়ানা সংস্কৃতি তৈরি করে। আর এই সং¯কৃতি থেকে তারা তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার নিয়ে আসে। ১৮০০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইন্দো-আর্যরা ইরানীয়দের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর ইন্দো-আর্যরা আনাতোলিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়া (বর্তমান আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল) এর উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। আর্য অনার্যদের যুদ্ধের আরেকটি কারণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় তহল ,আর্যরা প্রথমে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা দলবদ্ধ হয়ে পশু দল গুলকে সাথে নিয়ে ঘাস আচ্ছাদিত অঞ্চলে বসবাস করত । এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে এরা ঘুরে বেড়াত। এক স্থানের ঘাস পশু খাদ্য হিসেবে শেষ হয়ে গেলে , তারা অন্য অঞ্চলে চলে যেতেন। এভাবে আর্যরা প্রতিনিয়ত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে সাময়িক বসতি গড়ে তুলতেন। এক পর্যায়ে এসে আর্যদের এক রকম বার বার স্থান পরিবর্তন খুবই কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। তারপর আর্যরা এক স্থানে অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ সমস্যা সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা চালায়। কৃষি উর্বর ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যরা বসতি স্থাপনের প্রস্ততি নেয়। তাই তারা ভু খণ্ডের দখলের জন্য অনার্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
ভারতের প্রাচীন আধিবাসী সাওতালদের বিভিন্ন উৎসব রীতিনীতি থেকে পাওয়া যায় আর্য অনার্য যুদ্ধের নানা তথ্য। সাঁওতালি দাঁশাই নাচের ইতিহাসে অনেক প্রাচীন। দাঁশাই নাচটা শুধু নাচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এটা একজন বীরকে স্মরন করে উদযাপন করা হয। তিনি ছিলেন সাওতালদের শাসন কর্তা হুদুঢ় দুর্গা । যখন ভারতবর্ষে আর্য বা দিকু দের আগমন হয় নি, সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করতেন হুদূড় দূর্গা নামে এক মহান সাঁওতাল রাজা। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা । তিনি সেনাপতিসহ ভারত বর্ষের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। “হুদূড়” শব্দ টি সাঁওতালি শব্দ; উদাহরণ- ‘হুদূড় হুদূড় হয় এদা (জোরে বাতাস) ‘হুদূড় হুদূড় এ উদুর এদা(জোরে নাক ডাকা) এবং “দূর্গা ” শব্দ টিও পুংলিঙ্গ । এই “দূর্গা” শব্দ টি সাঁওতাল শব্দ ভাণ্ডারে ও নামকরণ এ পাওয়া যায় । তাই হুদূড় দূর্গা যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর রাজা ছিলেন বিয়টি নিশ্চিত করেই বলাই যায়। সাঁওতালি কথায় এর অর্থ দাড়ায় যে “রাজ” বা “শাসক ” । সাওতাল আধিবাসীদের মধ্যে কিস্কু সম্প্রদায় যে , রাজ্যের রাজকার্য পরিচালনা করতেন তার প্রমান পাওয়া যায় সাওতালী গল্প গান থেকে । সাঁওতালদের ইতিহাসে “রাজা” বা ‘যোদ্ধা’ “বীর” “শাসক” “গুরু” এই উপাধী গুলি দেয় হত তাদেরকে , যারা সাওতাল জাতির বিভিন্ন স্তরের শাসকের ভুমিকা পালন করতেন। তবে এই শব্দ গুলো এই উপমহাদেশের আদি এবং নিজস্ব শব্দ। এগুলো প্রাচীন পালি শব্দ, শব্দ গুলো আগত না। সাওতাল জাতির মঝে হুদূড় দূর্গা কিন্তু খুব সৎ স্বাধীনচেতা স্বদেশপ্রেমী প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনেই উপমহাদেশের মানুষেরা সুখে শান্তিতে বসবাস করত। ভারতবর্ষ তখন ছিল শস্য শ্যামলতায় পরিপূর্ণ । এই প্রাচুর্যের কারণেই বহিরাগতদের আগমন ঘটে । বহিরাগত বলতে এখানে আর্যদের কথা বলা যায়। সাওতালী ইতিহাস প্রাচীন বিষয় গুলো বিশ্লেষণ করলে পাওয়ায় যে , আর্যদের সাথে এই দেশের মানুষ (যাদের আর্যরা অনার্য বলে) দের সরাসরি সংঘর্ষ হয় । এই সংঘর্ষ বা যুদ্ধ অনেক দিন ধরে চলেছিল কিন্তু আর্যরা অনার্যদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি। বার বার অনার্যদের দ্ধারা আর্যরা প্রতিহত হয়ে বিকল্প পরিকল্পনা নেয়। অনার্যদের সাথে আর্যদের অনেক দিন ধরেই খন্ড যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজা হুদুঢ় দুর্গাার রণকৌশলের কাছে আর্য শক্তি পেরে উঠেনি। তখনকার দিনে কেল্লা বা ভড়ৎঃ ; (সাঁওতালিতে “গাড়”) নির্ভর যুদ্ধ ব্যবস্থা ছিল তাই বহিরাগত শত্রুরা প্রবেশ করতে পারে নি হুদুঢ় দুর্গার রাজ্যে। এই ” গাড়” গুলির নাম এখনো সাঁওতাল ইতিহাসে আছে। সাঁওতাল ১২ টি উপাধি এর জন্য বারো টি গাড় এর নাম আমরা পাই দেখতে পাই। যা সাওতাল আধিবাসীদের বারটি সম্প্রদায়ে ভাগ করেছে। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে, আদি মানব ও মানবী পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির সাত জোড়াা সন্তান থেকেই তাদের উদ্ভব। এজন্যই সাঁওতালরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালি ভাষায় এ গোত্র গুলো ‘পারিস‘ নামে অভিহিত করা হয়। গোত্র (পারিস) গুলো হলো-হাঁসদা, সরেন, টুডু, কিসকু, মুর্মু, মাণ্ডি, বাস্কে, বেসরা, হেম্বরম, পাউরিয়া, চঁড়ে ও বেদেয়া । প্রথমে সাতটি গোত্র ও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে আরও পাঁচটি গোত্রের উদ্ভব ঘটে মোট বারটি গোত্র হয় । সাঁওতালদের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। প্রতিটি গোত্র তাদের পূর্ব পুরুষ কিংবা গাছপালা, জীবজন্তু ও পশুপাখী ইত্যাদি নামে পরিচিত। হাঁসদা গোত্রের লোকের বিশ্বাস তাদের উদ্ভব ঘটেছে হাঁস থেকে। তাই হাঁসদা গোত্রের সাঁওতালদের হাঁস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আবার সরেন গোত্রের উৎপত্তি হরিণ থেকে তাই তাদের হরিণের মাংস খাওয়া নিষেধ। প্রতিটি গোত্র একত্রিত রাজা ছিলেন হুদুড় দুর্গা। তার নেতৃত্বে আর্যদের প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে নামে আধিবাসীরা।
ক্রমাগত আক্রমণ করেও যখন আর্যরা এই দেশের অধিবাসীদের রক্ষণ ভাগকে ভাঙতে পারে নি । তখন তারা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে। রণের নতুন কৌশল হিসাবে আর্যরা নারী সৈন্যদেরকে লড়াইয়ের এ সামনে নিয়ে আসে। আর্যরা এই যুদ্ধে নারী সৈন্যদেরকে নিপূণভাবে ব্যবহার করে। হুদূড় দূর্গা একজন সৎ, স্বাধীনচেতা, বীর ও মহানুভব যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরপুরুষ , তাই তিনি নারী সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতেন চাননি।তাই আর্যরা হুদুঢ়দুর্গাকে মারার জন্য গণিকা নারীকে দায়িত্ব দেন। এই গণিকা সুন্দরী নারী শান্তি প্রক্রিয়র স্থাপনের উদ্যেশ্যে নিয়ে হুদুঢ় দুর্গাার প্রসাদে যায়। এটা ছিল আর্যদের একটা কুট চাল। এই নারীকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল হুদূড় দূর্গার গোপন শক্তির রহস্য ভেদ করা। নারী তার রুপ যৌবন দিয়ে রাজাকে বশে আনার চেষ্টা চালান। একটা পর্যায়ে এসে নারীর প্রেম ভালোবাসার জালে হুদূড় দূর্গা আবদ্ধ হয়ে পড়েন। হুদূড় দূর্গা এতই সরল মহানুভব ছিলেন যে প্রতিপক্ষের কুট চালটি তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি যে সরল ও মহানুভব ছিলেন তা এই গণিকা নারীও বুঝতে পারেন। তাই শত্রু মিত্র না ভেবে এই নারীও হুদুড় দুর্গাার প্রেমে পড়ে যান। তিনি ভালবেসে ফেলেন হুদুড় দুর্গাকে । ঐ নারী ও হুদুঢ় দুর্গা সাথে বাপা(বিবাহ) বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর ফলে এই আর্য নারী হুদূড় দূর্গার স্ত্রী হয়ে যায়। এবং এখনাকার আধিবাসীদের সাথে মিশে যান। কিন্তু ঐ নারী তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি দুতের মাধম্যে অনার্য রাজার শক্তির তথ্য আর্যদের কাছে প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে যুদ্ধে অনার্যরা পরাস্ত হতে থাকে এক পর্যায়ে এসে সন্ধি স্থাপন হয় দুই পক্ষের মাঝে। এভাবেই আর্যরা উপমহাদেশের নিজেদের কতৃত্ব স্থাপন করেন ।
ভারতীয় উপমহাদেশের শাস্ত্রগ্রন্থে কতগুলো উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য হিসাবে নির্দেশ করে। তবে আর্যরা ছিল চতুর জাতি। তাদের বৃদ্ধিমতাকে ভারতীয় প্রাচীন বই গুলোতে উৎকৃষ্ট গুণ হিসাবে বলা হয়েছে।
আর্য “অনুপ্রবেশনকারী”-এর ধারণাটি আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় সিন্ধু (হরপ্পা) সভ্যতার আবিষ্কারের মাধ্যমে। এক ধ্বংসাত্মক অনুপ্রবেশের ইঙ্গিতও মেলে হরপ্পার ধ্বংসাবেশ থেকে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার মহেঞ্জোদাড়োর উপরের শিলাখণ্ডের উপর আবিষ্কৃত অসমাহিত অনেক মৃতদেহ আবিস্কার করেন। তার মতে এ গুলো সংঘর্ষের শিকার হয়ে মারা যায়। কিন্তু আর্যরা দাবী করতেন , তারা অহিংস জাতি । তার প্রমান মেলে ত্রিপিটকে , এই গ্রন্থে বলা আছে যে, ন তেন আরিয়ো হোতি যেন পাপানি হিংসতি অহিংসা সব্বপাণানং আরিয়োতি পবুচ্চতি [ ত্রিপিটক, ধম্মপদ ১৯/২৭০] এর বঙ্গানুবাদ হলো , প্রানী হিংসা করলে কেউ আর্য হতে পারে না, যে সকল প্রাণীতে অহিংসা দৃষ্টি রাখেন তাকেই আর্য বলে।
বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে নির্বাণলাভের প্রধান আটটি নীতিকে একত্রে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আবার প্রাচী কোন কোন গ্রন্ধে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকদেরকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এ চার বর্ণের ভাগ করার কথা বলা আছে। যা আর্যদের আগমনের পরের গ্রন্থ গুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। আবার, কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য – এ তিন বর্ণকে আর্য এবং চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, শূদ্র বর্ণ আর্য বংশের নয়। আর্যেরা ভারতবর্ষে এসে শূদ্রনামক অনার্য জাতি বিশেষকে নিজেদের সমাজভূক্ত করে নেন। কিন্তু বর্ণিত অনার্য শূদ্র যে কারা, তা তারসঠিক নির্দেশনায় নানা তথ্য চলে আসে। তাই শুদ্র বর্ণটি নির্নয় করা কঠিন। ভারতীয় উপমহাদেশে ঘটে নানা ধরনের সংস্কৃতির বিবর্তন। প্রচলন ঘটে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের ধর্মের। ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে উপমহাদেশের মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘটে। ধর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের সংস্কৃতি ও প্রথার। তবে এই অঞ্চলের সাওতাল আধিবাসীদের সমাজে এখনো দশ থেকে পনর হাজার বছর আগের সংস্কৃতির ধারাটি বিদ্যমান । কিন্তু বর্তমানে সাওতালরা খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রথার কিছু কিছু বিষয় হারিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এই অঞ্চলে পনর বিশ হাজার বছরের ধাবমান সংস্কৃতির ধারাটি ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে । এই কারণে আর্য অনার্যের যুদ্ধের সঠিক তথ্য গুলো খুজে পাওয়াটা কষ্টকর হয়ে দাড়িয়েছে।
তথ্য সুত্র : ইন্টারনেটের ওয়েব সাইড গুলিতে প্রকাশিত এতদ সংক্রান্ত নিবন্ধ ও উইকিপিডিয়া থেকে সংগ্রহ করা তথ্য।
***********************