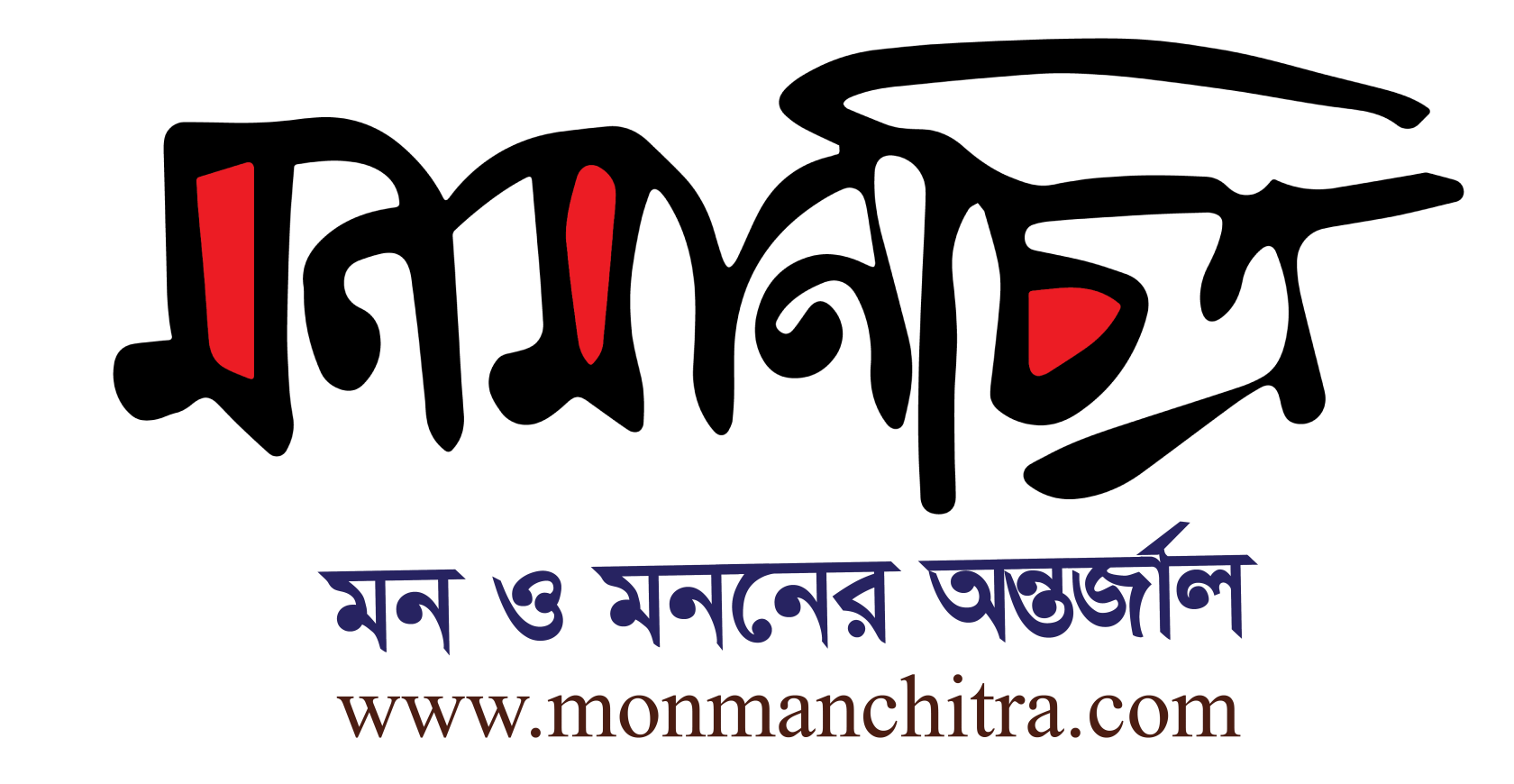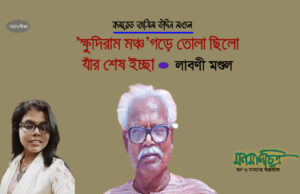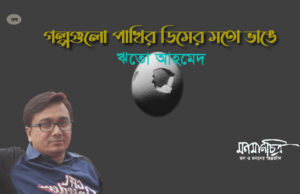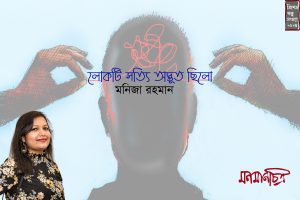পারমিতা ভৌমিক
জীবনের কবি জীবনানন্দ
জীবনানন্দের “‘ঝরাপালক'” থেকে “ধূসর পান্ডুলিপি” ‘”বনলতা সেন'” হয়ে “মহাপৃথিবী” অবধি সময়কালটি দুই মহামুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়। ঐ সময় ইউরোপের ইতিহাসে নেমে এসেছিল নৈরাশ্যবাদের আক্রমন। পৃথিবীর কথা যদি ছেড়েও দি, কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কথায় এসেও দেখেছি থমকে ভাবতে হয়।
টি, এস, এলিয়টেও দেখেছি তাঁর “দ্য ফোর কোয়াট্রেটস”-এ তিনি যুদ্ধের ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে স্মরণ করেছেন কৃষ্ণের বাণী। এরমধ্যে লুকিয়ে আছে আশাবাদের চারা।নিস্কৃতির আকুতি। জীবনানন্দের কবিতাতে সেসব দেখব। জীবনানন্দের কাব্যজীবনে এই কবির প্রভাব পড়েছে। কবিতা লেখার পক্ষে হয়তোবা এই সময়টা অসাধারণ কিন্তু ঠিক ততখানিই তাতে পরিপূর্ণ রয়েছেপ্রতীতীভঙ্গের যন্ত্রণা । ঐ সময়টা “সময় ও মানুষ”–এই দুয়ের প্রতিই বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে ছিল নিতান্তই অপ্রশস্ত।
জীবনানন্দে, পৃথিবীর ঐ সময়ের ক্ষান্তিহীন সংগ্রাম অস্পৃশ্য ছিল বলে অনেকেই মনে করেছেন।
কবি, প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় কিন্তু মনে করেছেন এই “সময়ছাপহীনতা”ই জীবনানন্দের নিজস্ব কবিধর্ম।”ক্যাম্পে” কবিতাটি তার জলজ্যান্ত আলেখ্য। রীতিমতো সময়ছাপহীন হয়েও কবিতাটি সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে মাংস ও মৃত্যুর গন্ধ যুক্ত করেছে। অদ্ভুতভাবে গুলি করে মারা হরিণের মৃত্যু থেকে মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গে অনায়াসে চলে গেছেন কবি।
এ এক অদ্ভুত উল্লম্ফন। কোয়ান্টাম লিপ । নিছক মৃত্যুবাসনা, মৃত্যুর রোমান্স নয়; এভাবেই কবি চলে যান সরাসরি মৃত্যুর নিষ্ঠুর জৈব বাস্তবতায়-
” বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই।”
প্রসঙ্গত জীবনানন্দের প্রকরণটিকেও সামনে আনতে হয়। তিনি প্রচলিত বানানকে ভেঙেছেন আবার নতুন করে গড়েছেন এবং এতেই কবির কাব্যশৈলীটি সম্যকভাবে প্রতিভাত হয়।
নিবিষ্ট উচ্চারণে কোনো “মনছবি”কে দৃশ্যযোগ্য করতে এবং সুরের প্রবাহকে অব্যাহত করে জীবনানন্দ মাত্রাকে সম্প্রসারিত করেছেন এই ধরণের ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে। এইট বিচ্যুতিই (Deviation from the Norm) তাঁকে আধুনিক কবির স্বীকৃতি দিয়েছে।
তিনি চিরাচরিত ‘ঐ’ বর্ণটিকে কে ভেঙে দিলেন। শুধু এ কবিতায় নয়, অন্যত্রও এমনটাই দেখেছি। এমন দেখেছি–“সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি;”– “ঐ”বর্ণটিকে ভেঙে “অই”‘ করলেন। সুর অনুযায়ী স্বরের মাত্রার সম্প্রসারণ ঘটল।
বিশ্বযুদ্ধের তুঙ্গ পর্যায়ে, ১৯৪২-এ জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব ইস্তাহারের মত ঘোষণা করলেন তাঁর অন্তর্লালিত নির্জনতার বৈভব “বনলতা সেন” কাব্যগ্রন্থে।
এখন দেখব কিভাবে কবিতাপাঠে উঠে আসবে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতর থেকে হঠাৎ মুক্তির বল্গাহীন আনন্দময় জয়গীতি।
যেন এখানেই Life of sensations আর life of thoughts এক অলৌকিক যোগাযোগ দৃশ্য করে তোলে কীটসের “অন ফার্স্ট লুকিং ইন্টো চ্যাপম্যানজ হোমর'” এর প্রতিধ্বনিকে——–
“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে।
অনেক ঘুরেছি আমি; “
এখানে আমি শব্দ টির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। জীবনানন্দে “বাক্যিক বিচ্যুতি”র প্রাচুর্য দেখা যাবে এ কবিতায় এবং অন্যান্য কবিতাতে।
দু’প্রকার বাক্যিক বিচ্যুতি হয়-
১) অর্থগত
২)গঠনগত।
আবহমান মানবতার অনুসন্ধানী এই ‘আমি’ এ কবিতায় হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে এ চলেছে। এটির অর্থগত বিচ্যুতি ধরলে উঠে আসে যোগ্যতার প্রশ্ন। সত্যিই কি এই আমি হাজার হাজার বছর পথ হাঁটিতেছি?? সম্ভব??
আমির এই ‘যোগ্যতা’না থাকলেও এখানে তা এই আমি’র ভাবসত্যকে প্রকাশিত করেছে এবং সেক্ষেত্রে কবি এই বিচ্যুতিকে অব্যর্থ ভাবে ব্যবহার করেছেন বলব।
তাঁর সময়কাল যেভাবে মৃত্যুলাঞ্ছিত হয়ে উঠেছিল, তাকে পরাভূত দেখার জন্যই তিনি ভাবতে পেরেছেন ব্যক্তির খন্ড খন্ড মৃত্যুর পরেও সমষ্টির মৃত্যু হয় না। এ এক অলৌকিক তীর্ণতা!!!
ইতিহাস তাঁকে সন্ধান দিয়েছে এই গভীর আশাবাদের এবং ঐ বিশ্বাসেরই মহত্তম উচ্চারণ শুনি তাই জীবনানন্দের কবিতাতে –
“মানুষের মৃত্যু হলে তবুও
মানব থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজাদের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।”
মানুষ ও মানবের এই বিশ্লেষটি সম্পূর্ণ গঠনগত এবং তাকে অতিক্রম করেও কিন্তু একটা ভাবসত্যগত অব্যর্থ বিচ্যুতিও রয়েছে।এটাই আধুনিকতা।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বা তারও পরে সমস্ত ধংসের মধ্যেও জেগে থাকছে একটা অদ্ভুত প্রত্যাশা –একটা প্রার্থনা –
“অভিভূত হয়ে গেল মানুষের উত্তরণ অভিভূত জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে অঙ্কেঃ গর্ভাঙ্ক তবু লুপ্ত হয়ে যাবে নাকি!
সূর্যে আরো নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও——- প্রাণ দাও পাখি।”
(মকর সংক্রান্তির রাতে”)
এই পাখিই তাঁর ইতিহাসচেতনা। এইসময়েই তিনি তিমির হননের গান করে তিমিরবিনাশী হতে চেয়েছেন এবং পরিশেষে উপলব্ধি করেছেন-
“আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।”
এসব উচ্চারণ হয়তো ধর্মভিত্তিহীন কিন্তু কিছুটা—-
তবুও কিছুটা রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসই তাঁকে এই প্রবল প্রত্যাশা এনে দিয়েছিল-
“আমি তবু বলি;
এখনও সে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে, চলি,”
“ভাবা যাক–ভাবা যাক—- ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত শত জলঝর্ণার ধ্বনি”
এখানে কবির প্রকরণ কৌশলে ঝর্না ও তার জলকে একসঙ্গে দৃশ্যময় ও শ্রুতিগোচর হতে দেখি। শত শত শত ধনাত্মক শব্দ না হয়েও তা থেকে উদ্গত ভাবধ্বনি অপ্রচলিত বিচ্যুতির সাক্ষর বহন করে। Sound বা শব্দ দিয়ে গাঁথা এ এক নতুন ধরণের চিত্রকল্প।
জীবনানন্দের মননে রয়েছে একটা চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ততার উপলব্ধি। এর নাম শূন্যতা। এইই তাঁকে ও তাঁর ভাষাকে এনে দিয়েছে পরমা নিবৃত্তি।
জীবনানন্দ এ সময়ের সর্বোত্তম পঠিত কবি। এবার জীবনানন্দের কবিতাপংক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করলে সে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হবে।
অতএব…….
তাঁর কবিতা থেকে এবার সরাসরি কিছু ভাষিক প্রকরণশৈলীর কথা বলি——
“কোনদিন জাগিবে না আর জাগিবার গাঢ় বেদনার। অবিরাম — অবিরাম ভার।
এই কথা বলেছিলো তারে।.
চাঁদ ডুবে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে। উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে ।
(আটবছর আগের এক দিন।)
রীতি ভাঙচুর এর কথা আগেই বলেছি। এখন আর একটু ভিতরে যাব। কবিতাতে প্রচলিত রীতিভাঙা বিচ্যুতি দিয়ে কবিকে চেনার কাজটি খুব সাম্প্রত জনপ্রিয় হয়েছে আর সে সুযোগ টি আমি নেব। উদ্ধৃত কবিতাটিতে প্রথম চারপংক্তিতে ‘আর’- এই- অন্তমিল রয়েছে (আর/ বেদনার / ভার/আর)।
খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের প্রত্যাশা থাকে বাকি পংক্তিতেও ওই অন্তমিল থাকবে। কিন্তু কবির এই প্রত্যাশা ভাঙার কৌশল কবিতাংশটিকে জীবনের প্রতীক করে তুলেছে। বিচ্যুতির পথ ধরে এসেছে এক নতুন শিল্পসুষমা।
‘র’ এর অন্তমিল।
বস্তুতঃ এই অনুপ্রাসে ‘র’ এর অনুপ্রাসে ধরা পড়েছে ধনিতাত্ত্বিক বিচ্যুতি যা জীবনানন্দকে চিনিয়ে দেয়। এটাই তাঁর phonastyle এর বিশেষত্ব।
এভাবেই ব্যাকরণ ও ধ্বনিলোপ এবং ভাষিক বিচ্যুতি দিয়েই জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব প্যারোলে তেরী করে নিলেন। প্রত্যয়, বিভক্তি, সন্ধি, সমাস নিয়ে কবি খেলা করেছে। এসব হয়ে উঠেছে কবির Stylistic Signature…. জীবনানন্দের শৈলীগত মুদ্রা এই Stylistic বিচ্যুতি। পরিচিত Norm ছক সব ভেঙে ফেললে দেখা গেল তাঁর রচনায় সসীম ব্যাকরণ হয়ে ওঠেছে অসীম, অবাঁধন। এমন হলে একটি নতুন বোধে উজ্জীবিত হয় প্রচলিত শব্দ।
জীবনানন্দে দেখি——
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখেয়াছি মেয়ে মানুষেরে।
(আট বছর আগের একদিন)
এখানে করি ‘রে’ বিভক্তির পরিবর্তে ‘এরে’ প্রয়োগ করে ‘মেয়েমানুষ’ শব্দটিকে বহুমাত্রিক করে দিয়েছেন । এই অতিরিক্ত স্বর ‘এ’ সংযোজিত হয়ে সুরের অনুরণন সৃষ্টি করেছে।-
এভাবেই প্রচলিত ব্যাকরণ সীমাকে, Norm কে- লঙ্ঘন করে জীবনানন্দ ভাব ভাষাশৈলী তৈরী করলেন , যাকে বলতে পারি জীবনানন্দীয় শৈলী। সমাসোক্তি অলংকারের প্রলোভনে তিনি পাঠককে জড়ান নি। জড়াতে চান নি। বরং বলতে পারি পরাবাস্তবকে রাপ দিতে তিনি ব্যাকরণগত বর্গের (genere) বা grammatical categories এর সরন ঘটিয়েছেন। এইটাই বিশেষভাবে জীবনানন্দের শৈলী।
যখন জীবনানন্দ বলেন স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে যায় স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো—- তখন স্পষ্টই দেখি অপ্রান ‘ধ্বনি’ তে ব্যক্তিবাচক ‘রা’ বিভক্তি (বহুবচন নির্দেশক) যোগ করে তিনি প্রাণ অপ্রানের সীমা মুছে দিলেন। এভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর চিত্রকল্পেরাও।
জীবনানন্দ যখন বলেন—-
‘বিকেল বলেছে এই নদীকে ‘শান্ত হতে হবে’—তখন লক্ষ্য করি কবিতা জন্মের আদিতম ক্ষেত্রের ইন্দ্রিয়বোধের বিপর্যয় ই সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার করেছে এই সরণকে।’
নদী’র সঙ্গে ‘কে’ বিভক্তি যোগ করে কবি নদীকে শ্রোতা করেছেন।
নদী কি শুনতে পায়? প্রশ্ন করেছেন বিকেল’ কে। অদ্ভুত বস্তা করেছেন পরত্ব আরোপিত হয়েছে তো বটেই বরং ব্যাকরণ, ইন্দ্রিয়বোধ বিপর্যয়, ও ফলতঃ ভাবনার বিপর্যয় ঘটেছে। এভাবেই জীবনানন্দের অনন্যবিরল শিল্প। ‘রক্তশব্দ’ ‘ভীতিশব্দ’ কবিতা হয়েছে জীবনানন্দের কাছে পেলাম, ‘আকাশগ্রন্থি’ ‘সময় গ্রন্থি’ ইত্যাদি শব্দ যা শাব্দিক সরনের পথে এসেছে।
এ একধরণের অর্থগত বিচ্যুতি যা জীবনানন্দকে কালান্তরিত করেছে । বিশ্লেষণের প্রায়োগিক বিচ্যুতি জীবনানন্দের অন্য শিল্পরীতি। তিনি লোকায়ত বিশেষণ ব্যবহার সদ্ধ বিশেষণকে ঠেলে ফেলে। করেছেন রীতিসিদ্ধ
অন্যত্র তিনি লিখেছেন-
“অলস- আঙুল কুমারীর আঙুল কুয়াশার”
শাব্দিক অন্বয়ের সীমা লঙ্ঘন করে কবি বিশেষণের বিশেষণ ব্যবহার করেছেন এবং অদ্ভুত ভাবে বিচ্যুতির আশ্রয় নিয়েছেন। -“অলস- আঙুল”।
শব্দকে নতুন তাৎপর্য দিতে অপ্রচলিত ধনাত্মক শব্দ ব্যবহারে কবি জীবনানন্দ তুলনা রহিত। তিনি যখন লেখেন ‘গভীর অন্ধকারে ঘুম থেকে নদীর কুল কুল শব্দে জেগে উঠলাম “
আবার
“টুপ-টুপ-টুপ-টুপ সারারাত ঝরে শুনেছি শিশিরগুলো’—ইত্যাদি
তখন দেখি এইসব ধনাত্মক শব্দে গড়ে উঠেছে নতুন ধরনের চিত্রকল্প যা কেবল sound দিয়ে গাঁথা। একথা আগেও বলেছি। কবিকে কখনও কখনও দেখেছি বিশেষণকে উপমার রূপে সাজিয়ে বিধেয় প্রসারক রূপে বাক্যে ব্যবহার করতে। এভাবে বাক্যিক চিত্রকল্পের অভিনবত্বের ক্ষেত্রেও প্রায়শই বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন কবি।
কবি জীবনানন্দ অনন্য শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, বিশেষত প্রেগন্যান্ট বাক্যের ক্ষেত্রে। সংরূপের বিচ্যুতিও জীবনানন্দকে বিশেষ ভাবে চিনিয়ে দেয়। প্রতিটি শিল্পের নিজস্ব গঠন আছে। কবিতা শিল্পেরও তাই। শিল্পী সেই- স্ংরূপ নিয়ে সৃষ্টিতে মগ্ন হন। এভাবেই বারবার দেখেছি সংরূপ ভেঙে জন্ম নেয় নতুন কবির শৈলী।
এই ভাঙাগড়ার পথে জীবনানন্দ আবার তৈরি নতুনতর চরণসজ্জা। কয়েকটি লাইন কবিতায় ডানসজ্জায় চমকে দেয়। অন্তর্মুখী প্রচার- বিমুখ জীবনানন্দের এই ডানসজ্জা তাঁর নিজস্ব সোচ্চার ঘোষণার সার্থক পথ হয়ে ওঠে-
“কেউ যাহা জানে নাই কোনো এক বাণী আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছি সেসব, সুরায়েছে, পুরানো তা – কোনো এক নতুন- কিছুর আছে প্রয়োজন তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন আর নাই কেউ। (কয়েকটি লাইন)”
জীবনানন্দে যতি চিহ্নের প্রয়োগেও আছে স্ব বিচ্যুতির প্রতিফলন। তাঁর নিজস্ব কবিতাংশে (-) ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার জীবনানন্দের উপরের বহুমাত্রিক প্রয়োগকে চিনিয়ে দেয়।
কত আর বলা যায়!!!?
শেষের আগে বলি,
মনে হয়, পাঠকের হাতের কাছে তিনি যেন এক আত্মঘাতী পানীয়—–
আর তার আকর্ষণ পাঠকদের প্রাণের গোপনে লতায়িত, যেন ব্যক্তি-আত্মার অন্তর্গূঢ় সে এক ভীষণ প্রয়োজন! জীবনানন্দপাঠ ও আত্মসাৎ করা তাই যেন মনে হয় পাঠকের, “জেনেশুনে বিষ করেছি পান।”
জীবনানন্দ অন্ধকারকে ভালোবেসে, মাটীর গভীরে প্রোথিত সত্তার শিকড়গুচ্ছে হাত রেখেছিলেন। ফলে সমূল অস্তিত্ব, চেতন ও অবচেতনের আলো এবং আঁধার তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল, জীবনানন্দে সিরিনিটির অভাব আছে।
আমাদের মনে হয়, আধুনিকের মূলকথাই ওই অভাববোধ, আর বোধ করি সেকারণেই জীবনানন্দ সর্বাধিক গৃহীত আ্লোকিত একালের কবি,যিনি একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণতার কবিও।
**********************