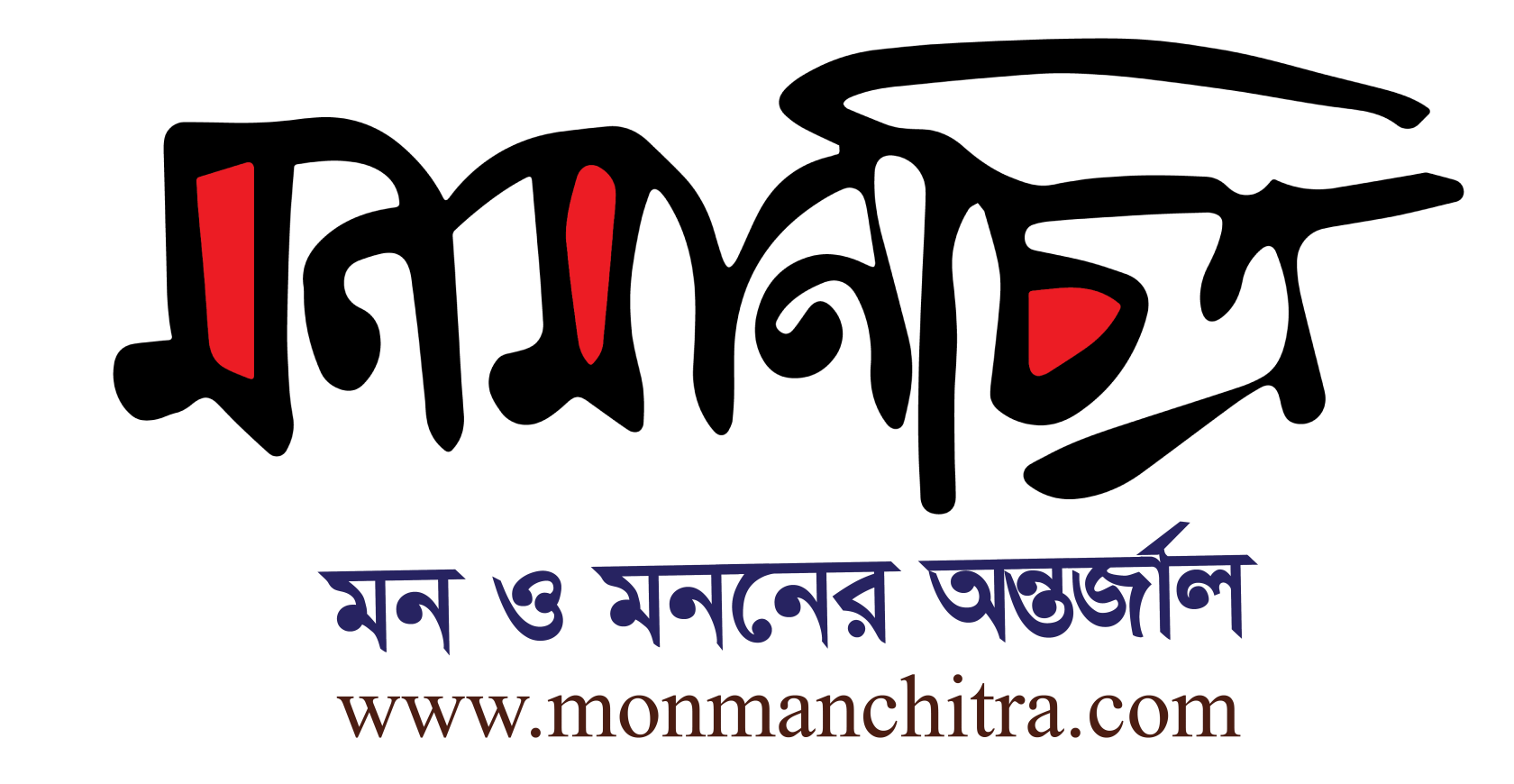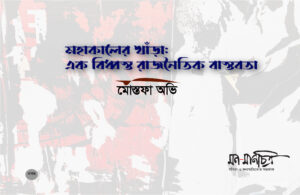একবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতায় দেশভাগের ছায়া: একটি সূচনালেখ
অংশুমান কর
উর্বশী বুটালিয়ার একটি বইয়ের নাম পার্টিশন: দ্য লং শ্যাডো। বইটির এই নামটিই বলে দেয় যে, দেশভাগকে উপমহাদেশের জীবন থেকে কোনোদিনই হয়তো বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই আর জীবিত নেই। কিন্তু জীবিত রয়েছেন তাদের সন্তান-সন্ততিরা, বংশধররা। তাঁদের মাধ্যমেইনদেশভাগের ছায়া ক্রমশ প্রলম্বিতই হচ্ছে। তাঁর বইটিতে বুটালিয়া লিখেছেন, “…as the numbers of those who retain direct, experiential memories diminish, as their stories recede, ways of remembering also change, the filters through which such memories are passed on–whether in and through literature, or music, or art and so much more — now begin to shape how they are passed on. With distance, the power and poignancy of the direct story are often muted, and what tends to acquire more importance is the business of living with thGKweske consequences of that history.” বুটালিয়ার বলা কথাগুলি বাংলা কবিতার জগত সম্পর্কেও সত্য। দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিলেন যে-সমস্ত কবিরা, তাঁদের প্রায় সকলেই আজ প্রয়াত। দেশভাগকে তাঁরা তাঁদের মতো করে লিখে গিয়েছিলেন বাংলা কবিতায়। একবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের কারোরই শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায় বা দেবদাস আচার্যর মতো দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তার মানে কিন্তু এটা নয় যে তাঁরা দেশ ভাগ নিয়ে কবিতা লিখছেন না। লিখছেন এবং সংখ্যায় তা নেহাত কম নয়। এ লেখায় সেরকম কিছু কবিতার সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। বলে নেওয়া ভালো যে, লেখাটি শিরোনামে ব্যবহৃত একবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা বলতে আসলে বোঝানো হচ্ছে এই নতুন শতাব্দীতে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন যে-কবিরা, তাঁদের কবিতা।
গত তিন দশক ধরে বাংলা কবিতা লিখছেন যে-তরুণরা, তাঁদের লেখায় দেশভাগ এসেছে পূর্ব প্রজন্মের অভিজ্ঞতার হাত ধরে। স্মৃতি হিসেবে। তাত্ত্বিকেরা এই স্মৃতিকে বলবেন ‘পোস্টমেমরি’। এই শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ম্যারিয়েন হার্শ। কাকে বলা হবে পোস্টমেমরি? হার্শ বলছেন, “Postmemory” describes the relationship that the “generation after” bears to the personal, collective, and cultural trauma of those who came before — to experiences they “remember” only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up. But these experiences were transmitted to them so deeply and affectively as to seem to constitute memories in their own right. As I see it, the connection to the past that I define as postmemory is mediated not by recall but by imaginative investment, projection, and creation. To grow up with overwhelming inherited memories, to be dominated by narratives that preceded one´s birth or one´s consciousness, is to risk having one´s own life stories displaced, even evacuated, by our ancestors. It is to be shaped, however indirectly, by traumatic fragments of events that still defy narrative reconstruction and exceed comprehension. These events happened in the past, but their effects continue into the present.” নতুন শতাব্দীর তরুণ কবিদের লেখায় দেশভাগ অনেকটা ঠিক এভাবেই উঠে এসেছে।
দেবপ্রতিম দেবের ‘শ্রুতি ও স্মৃতি’ কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবপ্রতিম লিখেছেন:
আমি যাদের কথা লিখছি
তাদের না আমি, না আমার বাবা দেখেছেন
ঠাকুরদার কাছ থেকে বাবা,
বাবার কাছ থেকে আমি
তাদের গল্প শুনেছি শুধু
যে বৃক্ষের পলাশে এই গল্প আঁকা সেখানে অগুনতি এরকম গল্প
বাবার পিসি ও তাঁর সন্তানদের গল্প—
প্রতি বছর যখন পলাশ শুকিয়ে ঝরে,
এঁরা মরে যান; আবার পলাশ ফোটে, কিছুদিন পর পুজো আসে, তার প্রাককালে তর্পণ—
এঁরা জীবিত হন
এভাবে আজও নতুন কিছু গল্প তৈরি হয়
রক্ত, মৃত্যু এবং হারিয়ে যাওয়ার গল্প
গল্প আঁকা থাকে পলাশে—
সাতচল্লিশের ইতিহাস, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি!
১৯৯৫ সালে জন্ম এই কবির। দেশভাগের তৃতীয় প্রজন্ম তিনি। দেশভাগের যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই এমনকি তাঁর পিতারও। কিন্তু, দেশভাগের ছায়া থেকে মুক্তি পান না এই কবি। কারণ যন্ত্রণার গল্পগুলো এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে প্রবাহিত হতেই থাকে।
দেশভাগের ফলে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসা তৃতীয় প্রজন্মের লেখা কবিতায় বারবার এভাবেই সহাবস্থান ঘটে একাধিক প্রজন্মের। স্মৃতির মধ্যে দিয়েই এঁরা অতীতকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। এবং বোঝান যে, আসলে মনে রাখা একটি রাজনৈতিক কাজ। অর্ণব চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৮৩) যেমন তাঁর ‘ঠাকুরদালানের মাটি’ কবিতাটিতে লেখেন:
দেশভাগের পর বাবা বুকের মধ্যে লুকিয়ে এনেছিলেন করতোয়া নদী আর অল্প কিছু ঠাকুরদালানের মাটি
সেই মাটি থেকেই তো এই জন্ম…
নদীর বাতাস এসে লাগে যখন
তুলসী, পুঁই, সন্ধ্যামণি আর চালকুমড়ো লতায়
চোখ বুজে দেখতে পাই
ঠাকুরদার হাত ধরে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন…
কপালে ঠাকুরদালানের মাটি দিয়ে ছোট্ট করে ফোঁটা কেটে দিলেন ঠাকুমা
কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় কীভাবে তৃতীয় প্রজন্মের একটি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তানও নিজের শেকড়ের যোগ খুঁজে পায় ওই বঙ্গে। স্মৃতির ভেতরে জীবন্ত করে রাখে পূর্ব প্রজন্মের পদ্মার ওপারে ফেলে-আসা জীবন। প্রায় একইভাবে সোহম চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৯৭) তাঁর ‘স্থাবর’ কবিতাটিতে দেশভাগকে কেন্দ্রে রেখে লিখে ফেলেন তিন প্রজন্মের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি:
আমার ক্লাস থ্রি-র ভাই
দুলে দুলে পড়ছে এখন নিল আর্মস্ট্রং-এর কথা ভাবছে, ও-ও একদিন পৌঁছে যাবে চাঁদে
আমার ইচ্ছা পিএইচডি, আমেরিকায়
টুকটাক পরীক্ষাও দিচ্ছি এদিক-ওদিক
নিতান্তই কিছু না-হলে মুম্বাই কি ব্যাঙ্গালোর
আমার বাবা দার্জিলিং যাননি কোনোদিন
মোবাইল-ভর্তি ট্যুর-অ্যাপে এই ট্রেন, ওই হোটেলের ভাড়া
সবকিছু দেখেশুনে রবিবার বাজারে বেরোন
আমার দাদু, অশীতিপর
টলমল পায়ে এসে উঠোনে দাঁড়ান, বিড়বিড় করেন
“দ্যাশে যামু, দ্যাশে যামু, দ্যাশে’
আমাদের যাওয়া আর হয় না কোথাও
চমৎকার এই কবিতাটি দেশভাগের শিকার প্রথম প্রজন্মের দেশে ফিরে যাবার অক্ষমতার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় পরবর্তী প্রজন্মের স্বপ্ন এবং সংলগ্ন আশঙ্কা। হয়তো ইঙ্গিত করে স্বপ্নভঙ্গেরও। নিশ্চিত করে বোঝায় যে, ফেলে-আসা দেশে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব কেবল স্মৃতিতে দেশটিকে বাঁচিয়ে রাখা।
স্মৃতির ভিন্নতর প্রকাশও ঘটেছে এই প্রজন্মের দেশভাগ নিয়ে লেখা কবিতায়। সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশিত দু-টি গ্রন্থে আঁচল মালহোত্রা দেশভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন মেটেরিয়াল মেমরির ধারণাটিকে। দেশভাগের কারণে নানা পর্বে দেশত্যাগ করার সময় উদ্বাস্তু মানুষগুলি সঙ্গে এনেছিল সামান্য কিছু জিনিসপত্র। কখনও শালগ্রাম শিলা কখনও থালা-বাটি-গ্লাস কখনও বা একটি দু-টি গয়না। দেশভাগের প্রত্যক্ষ শিকার
প্রথম প্রজন্মের সেই মানুষগুলি এখন আর বেঁচে নেই হয়তো। কিন্তু, তাঁদের ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় নিয়ে আসা বস্তুগুলি রয়ে গেছে। তারাই ধরে রেখেছে দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন আর স্মৃতিকে। সোজা করে বললে বলতে হয় বস্তুকেন্দ্রিক এই স্মৃতিকেই বলা হয় মেটিরিয়াল মেমরি। মালহোত্রা লিখেছেন, “Material memory works in mysterious ways. We surround ourselves with things and put parts of ourselves in them. It hides in the folds of clothes, among old records, inside boxes of inherited jewellery, between the yellowing pages of old books, in the cracks of furniture and the stitches of frayed, embroidered handkerchiefs. It merges into our surroundings, it seeps into our years, it remains quiet, accumulating the past like layers of dast, and manifests itself in the most unlikely scenarios, generations late. ”
এই বস্তুকেন্দ্রিক স্মৃতির উপস্থিতিও দেখা যায় একবিংশ শতাব্দীর তরুণ বাঙালি কবিদের লেখা কবিতায়। যেমন তন্ময় ভট্টাচার্যর (জন্ম ১৯৯৪) লেখা ‘কুলদেবতা’ কবিতাটি। তন্ময় লিখেছেন:
সত্তর বছরের পুরোনো বাসন
ঘষেমেজে চকচকে করেছি। এবার
ভোগ দেওয়া যেতে পারে। রুষ্ট হবেন কিনা
জানা নেই, তবে ভরসা, পুঁটুলি গুছিয়ে
তিনিও তো এসেছেন, সেবারেই, একই ট্রেনে চেপে
ছোট্ট এই কবিতাটি একইসঙ্গে ধারণ করে রেখেছে অতীত ও বর্তমান। কুলদেবতাকে সঙ্গে করেই দেশ ছেড়েছিল একটি উদ্বাস্তু পরিবার। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বাসনকোসনও। দীর্ঘদিন ব্যবহার হয়নি বাসনগুলি। এবার ব্যবহৃত হচ্ছে দেবতাকে ভোগদানের জন্য। এভাবেই কুলদেবতা আর পুরোনো বাসন ধারণ করে রাখছে দেশভাগের স্মৃতিকে। কবিতাটি বুঝিয়ে দেয় যে, উদ্বাস্তু পরিবারগুলির গৃহ আসলে একটি আর্কাইভ, একটি মিউজিয়াম, এখানে সযত্নে ধারণ করে রাখা আছে দেশভাগের নানা চিহ্ন।
স্মৃতি যেমন এই তরুণ কবিদের কবিতার বিষয় তেমনই এঁদের কবিতায় ধরা পড়েছে স্মৃতি আর বাস্তবের ফারাকটুকুও। পড়া যেতে পারে কস্তুরী সেনের (জন্ম ১৯৮৫) এই কবিতাটি:
ঢাকা সফরের চিঠি
থৈ থৈ মাঠ, সোনারং তারপাশা—
মেঘে মেঘে কালো লক্ষ্মীবিলাস ধান
কাঠ খেয়ে গেছে, পালকিটি উঠোনের
জ্যোৎস্না হলেই, দেবতাও জল পান
এইখানে ছিল শরিকের আটচালা
পথ উঠে যেত, জিলা স্কুল সামনেই;
বন্ধু লেখেন, ঢাকা সফরের চিঠি
‘স্মৃতি বাদ দিলে, চেনার উপায় নেই’।
ফিরে যাওয়া ভালো, ফিরে না যাওয়াও ভালো, হিজলের বাসে চোখ যাওয়া ভালোবেসে—
থৈ থৈ মাঠ, সোনা-রং… তারপাশা
শতক পরের নিবিড় বাংলাদেশে।
বাংলাদেশ ভ্রমণের পরে কবিকে তাঁর বন্ধু চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, পালটে গিয়েছে সবকিছু। তাঁর বাংলাদেশ বেঁচে রয়েছে কেবলমাত্র স্মৃতিতেই। ঠিক এমনই একটি কবিতা লিখেছিলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়ও। সেখানেও ছিল স্মৃতি বাস্তবের ফারাক থেকে জন্ম নেওয়া এই বেদনা, এই বোধ যে, ফেলে-আসা ঘর আসলে একজন মানুষ বহন করে কেবল তার স্মৃতিতে। বাস্তবে সেই ঘর বদলে যায় এতখানি যে, মাঝে মাঝে তাকে আর নিজেদের ঘর বলে চেনাই যায় না।
ফেলে-আসা ঘর একেবারে নতুনভাবে বিষয় হয়েছে এই তরুণ কবিদের লেখা কবিতাতেও। বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে দেশভাগ পরবর্তীকালে পাসপোর্ট-ভিসা চালু হওয়ার ফলে যোগাযোগ হওয়া খুব সহজ ছিল না। কিন্তু, পৃথিবী পালটে গিয়েছে এখন। আন্তর্জাল যুক্ত করে দিয়েছে দুই দেশের মানুষকেই। একটি কবিতায় দুই দেশের দুই বন্ধুর আন্তর্জালিক কথোপকথনে উঠে এসেছে ফেলে-আসা ঘরের প্রসঙ্গ। কবির নাম সঞ্জয় ঋষি(জন্ম ১৯৮৩), কবিতার নাম ‘তোমার বাড়িটাই আমার বাড়ি’’:
ঠাকুরদাদা, নিমাই কীর্তনিয়া,
বাংলাদেশ থেকে এসেছেন কয়েক বছর হল,
বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন ফতেমা বিবির কাছে। নাতি ফুরফুর কীর্তনীয়া। লুনার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব
তার, ফেসবুকে। ফুরফুর জানতে চাইল, আপনাদের
বাড়ি বাংলাদেশের ঠিক কোথায়? লুনার বিবরণে মিলে যায়, ঠাকুরদার বাড়ি ওটাই।
ফুরফুরে একটু আনন্দও পেল বটে, আবার দুঃখও…
লুনা বলে, জানেন, নানি এই বাড়িটা আমাদের প্রতিবেশী
নিমাই চাচার কাছ থেকে কিনেছিল।
বাড়ির ভেতরে অপূর্ব সিংহাসন, রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি…
ছোট্ট একটি কবিতা ধরে রেখেছে ইতিহাস, যে-ইতিহাসে কেবল অবিশ্বাস আর রক্তপাতই ছিল না, ছিল বিশ্বাস আর সম্প্রীতিও। ওপার বাংলা ছেড়ে আসার সময় নিমাই কীর্তনীয়া বাড়ি বিক্রি করে এসেছিলেন ফতেমা বিবির কাছে। ধর্মে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সেই বাড়িতে থাকা অপূর্ব সিংহাসন আর রাধা কৃষ্ণের মূর্তিগুলির কণামাত্র ক্ষতি করেননি ফতেমা বিবির পরিবার। বরং যত্নে রক্ষা করেছে তা। সেই মূর্তিগুলি নিয়ে একই রকমের মুগ্ধতা তাঁর নাতনি লুনার। স্মৃতি এই কবিতায় তাই কেবলমাত্র দগ্ধদিনের চিত্রই আঁকে না, আঁকে সম্প্রতি আর দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চিত্র, ভরসা যোগায় পাঠককে।
অবশ্য যদি এ কথা বলা হয় যে, দেশভাগ নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে তরুণ বাঙালি কবিরা যে-সমস্ত কবিতা লিখেছেন, তা কেবলই স্মৃতি-কেন্দ্রিক, তাহলে হয়তো সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। দেশভাগ নিয়ে বাংলা ভাষায় যত কবিতা লেখা হয়েছে, তার অনেকগুলিতেই থেকেছে দেশভাগকে অস্বীকার করার প্রবণতা, দেশভাগ হলেও দুই বাংলা যে আসলে এক – উঠে এসেছে এই ধরনের মত। কখনও বা আকাঙ্ক্ষাও জেগেছে পুনর্মিলনের। এই প্রজন্মের কবিদের লেখাতেও উঠে এসেছে এই বিষয়গুলি। পরপর পড়া যেতে পারে ঋক অমৃতর ( জন্ম ১৯৯৫) দু-টি কবিতা:
ঊনসত্তর বছর হয়ে গেল
অজন্তার মুরাল নাকি ভারতের মানচিত্র, তর্কটা ছিল কার শিল্পগুণ বেশি সেই নিয়ে। সুমনদা স্বভাবসিদ্ধ, চৈত্যের কথা বলতে গিয়ে খুব সহজেই পাঁচশো, হাজার বছর অতিক্রম করে যাচ্ছিল ইতিহাসের পাতা, উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল চোখ; অথচ দেশ-এর কথা বলতে গিয়ে, আমি উনিশশো সাতচল্লিশের পর আর একটুও এগোতে পারলাম কই!
ভাগে বাড়ছি দাদা। স্বাধীনতার এমন জন্মদিনে এসো, কেকটাও আমরা রাজ্যের মানচিত্রের মাপেই কাটি।
পাটিগণিত ২.০
এক থেকে এক বাদ দিলে যদি দুই হয়
যেন আমি দেশের কথা বলছি
দেশভাগকে মেনে না নিতে পারার যন্ত্রণা দু-টি কবিতারই অক্ষ। আসলে অসম্ভব জেনেও কখনো-কখনো এই তরুণ কবিরা স্বপ্ন দেখেন কাঁটাতার অতিক্রম করার। সেই স্বপ্নই ধরা পড়েছে কিশলয় ঠাকুরের (জন্ম ১৯৮৮) কবিতা ‘বাংলাদেশ আর বাংলা বিদেশ’-এ।
কে আঁচড়ে দিয়েছে বলো
আমার মায়ের মাথা?
আঁকাবাঁকা সিঁথি,
আর দুপাশ দিয়ে এলোমেলো সব চুল
তবুও আজ হাওয়া আসলে,
কেউ কি ঠেকাতে পারো?
উলটে এসে পড়ি
আমি, সিঁথির ওপার থেকে।
কোথায় এমন হাওয়া?
এসো, এলোমেলো করো চুল।
নারীর চুলকে দেশভাগের যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সাহস দেখানো সম্ভবত কেবল একজন কবির পক্ষেই সম্ভব। যে-সিঁথি আলাদা করে দিয়েছে দুই বাংলাকে, কিশলয় চাইছেন সেই সিঁথি মুছে যাক–হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিক চুল, উড়িয়ে নিয়ে যাক সিথির কাঁটাতার, মিলে যাক দুই বাংলা।
যে-সমস্ত কবিদের কথা এতক্ষণ বললাম তাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের কবি। উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রামের কথা এদের কবিতায় খুব বেশি উঠে আসেনি। কিন্তু উঠে এসেছে আসাম বা ত্রিপুরার তরুণ কবিদের রচনায়। স্বামীর তরুণ কবিদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতেই হয়। বাঙালি খেদাও আন্দোলন, নাগরিকত্ব আইনের নানা ধরনের জটিলতার কারণে আসামের বাঙ্গালীদের উদ্বাস্তুর দশা মনে হয় পুরোপুরি কাটেনি এখনও। সে কারণেই আসাম থেকে কবিতা লেখা এক তরুণ রাজেশ শর্মা (জন্ম ১৯৯১) নিম্ন তোদের যন্ত্রণার জীবনকে ধরে রাখেন তার কবিতায়। কবিতাটির নাম ‘টুটাফাটা বংগাল’’:
সাকিনা আর ঈশ্বরী পাটনির বাপজান মৈমনসিঙ্গি
বুড়া লোহিতের চরে ধান রুইত
সাকিনা আর ঈশ্বরী পাটনি এখন
টুটাফাটা বংগাল
তাদের ঘরে প্রতিরাতে বরদৈচিলা!
ব্রহ্মপুত্র নদীর নাম হল লোহিত। আর অসমিয়া ভাষায় বরদৈচিলা হল এক ধরনের কালবৈশাখী। বড়ো আর অসমিয়া লোককথায় ইনি একজন ঝড় জলের দেবীও। বোঝাই যাচ্ছে ময়মনসিংহ থেকে এসে আসামে নিবাস নেওয়া সাকিনা আর ঈশ্বর পাটনীর দিন কাটে কী কঠিন সংগ্রামে!
এভাবেই একবিংশ শতাব্দীর কবিদের কবিতায় এখনও ফিরে ফিরে তার ছায়া ফেলছে দেশভাগ। লেখা একটি প্রস্তাবনা মাত্র। ভবিষ্যতে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে দেখার ইচ্ছে রইল। আশা করি অন্যরাও বাংলা কবিতায় তরুণ কবিদের কবিতায় কীভাবে ছায়া ফেলেছে দেশভাগ, সে-বিষয়ে গবেষণা শুরু করবেন।
এই রচনায় ব্যবহৃত কবিতাগুলি সৃষ্টিসুখ প্রকাশিত ও তন্ময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত “দেশভাগ এবং…:নির্বাচিত কবিতা ও গান” বইটি থেকে গৃহীত।
******************************