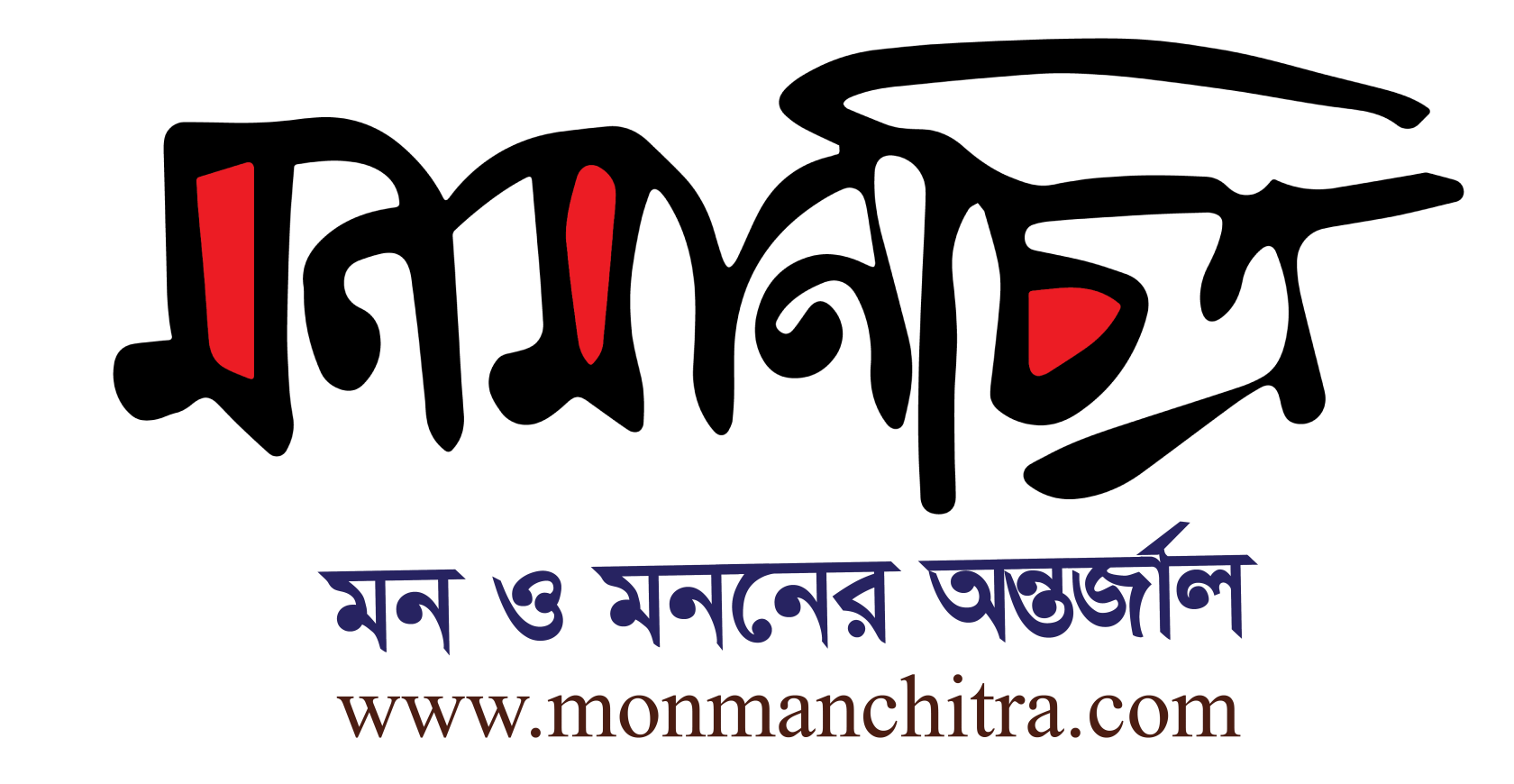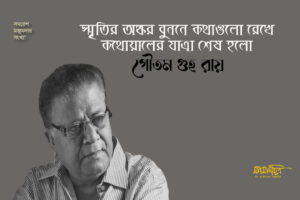আলী সিদ্দিকী
পরাবাস্তববাদ ও সুফিবাদ: দার্শনিক ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক বহুমাত্রিকতা
সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের আন্তঃসম্পর্কিত বিস্তারে পরাবাস্তববাদ এবং সুফিবাদ দুটি মৌলিক পথ, যা বাস্তবতার বাইরের জগৎকে অনুভব, উপলব্ধি ও রূপায়ণের এক অনন্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে। পরাবাস্তববাদ যেভাবে স্বপ্ন, অবচেতন ও যুক্তি-বহির্ভূত চেতনাকে প্রকাশ করে, সুফিবাদ ঠিক একই ভাবে আত্মার মুক্তি, একত্ব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর বা সর্বশক্তির সঙ্গে মিলনের প্রয়াস করে। আমরা এখানে বিশ্লেষণ করব কীভাবে এই দুই ধারা দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সংলগ্ন, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় ও ইউরোপীয়-আমেরিকান প্রেক্ষাপটে।
সুররিয়ালিজম: দার্শনিক ও সাহিত্যিক পটভূমি
১৯২৪ সালে আন্দ্রে ব্রেতোঁ তাঁর “Manifesto of Surrealism” প্রকাশের মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক ও চিত্রকলার আন্দোলনের সূচনা করেন, যার মূল ভিত্তি ছিল ফ্রয়েডীয় অবচেতন, স্বপ্নের রচনাবিধি, এবং যুক্তি-বহির্ভূত নির্মাণ। ব্রেতোঁর মতে, “Surrealism is based on the belief in the omnipotence of dreams, in the disinterested play of thought.” তার রচনায় ‘Nadja’ উপন্যাসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যেখানে স্বপ্ন ও বাস্তবতা একইসাথে মিলেমিশে যায়। সুররিয়ালিস্ট সাহিত্য, চিত্রকলা ও নাট্যকলায় যুক্তিবাদী ভাষার পরিপন্থী এক পরাবাস্তব অভিজ্ঞতার নির্মাণ ঘটে, যেখানে ফ্রয়েডীয় অবচেতনার বিশ্লেষণ, স্বপ্ন, যৌনতা, মৃত্যু, বিকার ও মুক্তির অন্বেষা মূলত প্রবল। সালভাদর দালি, পল এলুয়ার, লুই বুনুয়েল প্রমুখ শিল্পী-লেখকগণ এই প্রবণতাকে গভীরতর করেছেন। ডালির গলে যাওয়া ঘড়ি (The Persistence of Memory), ম্যাগ্রিটের প্যারাডক্সিকাল চিত্র, এলুইয়ারের প্রেম ও অস্থিরতার কবিতা, এবং ফ্রান্সিস পিকাবিয়ার বিমূর্ত রূপকল্প—all illustrate a dream-like dimension that deconstructs rationalist realism. পরাবাস্তববাদ এমন এক শিল্পধারা যেখানে যুক্তি ও বাস্তবতা পরাজিত হয় কল্পনা ও অবচেতনের কাছে।
সুফিবাদ: ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপ
সুফিবাদ ইসলামি আধ্যাত্মিকতার অন্তর্মুখী ধারা, যার মূল লক্ষ্য আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর সঙ্গে ঐক্যলাভ (Wahdat al-Wujud)। হজরত বায়েজিদ বস্তামী, রাবেয়া বসরী, মনসুর আল-হাল্লাজ, আবদুল কাদের জিলানী, শাহ আবদুল লতিফ, লালন সাঁই প্রমুখ সুফি সাধকেরা প্রেম ও আত্মোত্সর্গের মাধ্যমে অনন্তের সন্ধান করেছেন।
সুফি দর্শনের মূলত তিনটি স্তর লক্ষণীয়: তরিক্কি (Spiritual Ascent): আত্মার উন্নয়ন ও পথ চলা, ফানা (Self-annihilation): আত্মমোহ বিলুপ্ত করে ঐশিক সত্তায় বিলীন হওয়া, বাকা (Eternal subsistence): ঈশ্বরীয় চেতনার স্থায়ী উপলব্ধি।
সুফিবাদ ইসলামের অন্তর্দর্শনভিত্তিক আধ্যাত্মিক আন্দোলন, যার মূল অভিমুখ আল্লাহর সঙ্গে আত্মার ঐক্য। মনসুর আল-হাল্লাজ তাঁর বিখ্যাত “আনাল হক” ঘোষণার মধ্য দিয়ে আত্মার ঐশ্বরিকত্বকে ঘোষণা করেন। তার রচনায় “Tawasin” গ্রন্থে সূক্ষ্ম বর্ণনা রয়েছে ‘আমি’ ও ‘তুমি’ মিশে যাওয়ার এক অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার। জালালুদ্দিন রুমির “Masnavi” ও “Diwan-e-Shams” গ্রন্থদ্বয় সুফি দর্শনের নান্দনিক শৈলীকে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। লালন সাঁই তাঁর গানে বলেন, “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।” এই ধরনের রূপক কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাখ্যা নয়, বরং একধরনের দার্শনিক প্রতীক। তিনি যুক্তি ও আচারবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন, “ধর্মের কাঁধে পাপের বোঝা।” হাল্লাজ ও লালনের রচনায় রয়েছে আত্মার নিজস্ব অবলোকন ও যুক্তিহীন আস্থার উপস্থাপন।
সুররিয়ালিজম ও সুফিবাদের অন্তর্মুখী মিল
সুররিয়ালিজম ও সুফিবাদ উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটি মৌলিক মিল—বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অদৃশ্য, বিমূর্ত ও রহস্যময় অভিজ্ঞতার প্রতি আকর্ষণ। ব্রেতোঁ যেমন স্বপ্নকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎস বলেছেন, রুমি বলেছেন, “You were born with wings, why prefer to crawl through life?” এই উক্তিগুলো মানবচেতনার অন্তর্মুখী একাত্মতা প্রকাশ করে। হাল্লাজের আত্মাহুতি ও লালনের দেহতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্ব উভয়ই চিন্তার গণ্ডি ভাঙার আহ্বান। হাল্লাজ ছিলেন আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যের সাহসী উচ্চারণকারী। তাঁর জীবন ও মৃত্যুর ইতিহাস ইঙ্গিত করে যে, ঐশ্বরিক প্রেমের সাধনা কীভাবে ব্যক্তি-সত্তাকে অতিক্রম করে পরমের সাথে একাকার করে তোলে। তাঁর “আনাল হক” একটি বিপ্লবাত্মক বোধ—যা সুররিয়ালিস্ট চেতনাবিশ্বেও মেলে। জর্জ ব্যাটেইল “Inner Experience”-এ বলেন, “The mystic wants to see without knowing; the surrealist, to know without seeing.”—এখানে এই দ্বৈত চেতনার মধ্যেই সুররিয়াল-সুফি মিল নিহিত।
সুররিয়ালিজম ও সুফিবাদের মিল পরিলক্ষিত হয় নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে:
• উভয়ই বাহ্যিক যুক্তির বাইরের এক চেতনার স্তরে পৌঁছাতে চায়।
• তারা স্বপ্ন ও ধ্যানের মধ্যে সত্য অনুসন্ধান করে।
• উভয় ক্ষেত্রেই নিজস্ব ‘স্ব’কে বিলুপ্ত করে বৃহৎ সত্তার সঙ্গে একীভূত হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে।
• দর্শন ও ভাষা এখানে প্রতীকী, বিমূর্ত ও অন্তর্মুখী।
ড. শিবলী নোমানী বলেন, “সুফিবাদ হলো যুক্তিকে অতিক্রম করে উপলব্ধির সাধনা।” আর আন্দ্রে ব্রেতোঁ বলেন, “It is the unconscious that leads us to truth.”
সুফি কাব্যে সুররিয়ালিজমের উপাদান
সুফি কবিতা যেমন রুমির “দ্য সেলফ ওয়ে ফ্রম দ্য সেলফ”, হাল্লাজের “Tawasin”, এবং লালনের “যেখানে সাঁই নেই”—এইসব কবিতায় সুররিয়ালিস্ট ধাঁচে আত্ম-আলোচনার, গূঢ় চিত্ররূপের, প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, রুমি বলেন, “The wound is the place where the Light enters you.” এই ধরণের আত্মবিস্ময় পরাবাস্তবের ব্যঞ্জনা বহন করে।
দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুফি দর্শন ও তার প্রতিফলন
লালন, হাছন রাজা, বুল্লে শাহ, শাহ আবদুল করিম—এই সকল বাউলদের রচনায় ধর্ম, জাতপাত, বর্ণের সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষের ভেতরকার আত্মার স্বাধীনতাকে তুলে ধরা হয়। যেমন, বুল্লে শাহ বলেন, “মসজিদে খুঁজেছ ঈশ্বর, আমি খুঁজি আমার হৃদয়ে।” এর সঙ্গে মেলে ম্যাগ্রিটের ‘This is not a pipe’ বা ‘Ceci n’est pas une pipe’ চিত্রটি, যেখানে বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়।
ভাষা ও চিত্ররূপ: প্রতীকচর্চা ও বিমূর্ততা
সুররিয়ালিজমে ‘জিরাফ যার গায়ে আগুন’, ‘ছায়া যার মুখের পেছনে’, কিংবা ‘চোখের ভিতর গর্জন’—এইসব বিমূর্ত প্রতীক ভাষা ও বাস্তবতার সীমারেখা ভেঙে দেয়। লালনের গানেও “অচিন পাখি”, “নির্ঘুম নিশি”, “মন মাঝির নাও”—এইসব চিত্র বিমূর্ত, দর্শনসমৃদ্ধ ও প্রতীকপ্রধান। হাল্লাজের শব্দরূপ যেমন “আমি সেই যাকে আমি বলি”—এটি সুররিয়ালিস্ট ‘আমি’র ভাঙনের প্রতিচ্ছবি।
ইউরোপ ও আমেরিকায় পরাবাস্তববাদের প্রভাব ও প্রয়োগ: সাহিত্য, চিত্রকলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রসারে
পরাবাস্তববাদের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
পরাবাস্তববাদ (Surrealism) ইউরোপের বিশেষ করে ফ্রান্সের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক সৃজনাত্মক বিদ্রোহ হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, অস্তিত্ববাদী সংকট এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের প্রভাব এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চেতনায় অবদান রাখে। ১৯২৪ সালে আঁদ্রে ব্রেতঁ (André Breton) তাঁর Surrealist Manifesto-তে ঘোষণা করেন: “Surrealism is psychic automatism in its pure state… the dictation of thought in the absence of all control exercised by reason.” (André Breton, Manifesto of Surrealism, 1924)
এখানে যুক্তির বাহ্যরূপ ভেঙে অবচেতন মনের ভাষাকে প্রকাশ করাই ছিল লক্ষ্য, যা পরবর্তীকালীন আধুনিক সাহিত্যে এক মৌলিক বিপ্লব সৃষ্টি করে।
ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিত্রকলায় প্রভাব
পরাবাস্তববাদ শুধুমাত্র একটি সাহিত্যিক কৌশল নয়, এটি চিত্রকলা, নাটক, ও চলচ্চিত্রের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সালভাদোর দালি, ম্যাক্স আর্নস্ট, রেনে ম্যাগ্রিট প্রমুখ চিত্রশিল্পী “dream logic” ব্যবহার করে দর্শকের চেতনা ও অভ্যাসকে চ্যালেঞ্জ করেন। দালির “The Persistence of Memory” (1931) পেইন্টিংয়ে সময় ও বস্তুগত বাস্তবতাকে গলিত আকারে দেখিয়ে পরাবাস্তব অনুবর্তী সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।
সাহিত্যজগতে পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ, এবং ব্রেতঁ নিজেও তাঁদের কবিতায় অবচেতনের বিভ্রান্তি, ইন্দ্রিয়ের সংকট ও প্রেমকে এক অভূতপূর্ব বিমূর্ততাযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এঁদের রচনাকে ফ্রয়েডীয় যৌন-চেতন ও ল্যাকাঁ-প্রভাবিত ভাষাতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।
আমেরিকায় পরাবাস্তববাদের স্থানান্তর ও রূপান্তর
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাবাস্তববাদী শিল্পীরা ইউরোপ থেকে পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেন, যার ফলে এই ধারাটি উত্তর আমেরিকার চিত্রকলা ও সাহিত্যে গভীর ছাপ রাখে। নিউ ইয়র্কে Abstract Expressionism-এর প্রেক্ষাপটে Jackson Pollock ও Mark Rothko-র চিত্রকলা পরাবাস্তববাদের আবেগাত্মক ও আত্মবিশ্লেষণাত্মক রূপান্তর বহন করে। এছাড়া Allen Ginsberg, William S. Burroughs, এবং Lawrence Ferlinghetti-র মতো Beat Generation-এর কবিরা স্বপ্ন, হ্যালুসিনেশন, যৌনতা ও অবচেতন চেতনার এক বিশৃঙ্খল দৃশ্যবিশ্ব তৈরি করেন যা পরাবাস্তবতাবাদী সংবেদকে আধুনিক আমেরিকান বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।
পরাবাস্তববাদ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
পরাবাস্তববাদ রাজনৈতিক ও নৈতিক আদর্শগত এক বিকল্প চেতনার বাহক। ব্রেতঁ মার্ক্সবাদে আস্থা রেখেও স্তালিনবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরাবাস্তববাদ শ্রেণিবদ্ধ ও দমনমূলক চেতনার বিরুদ্ধে এক অন্তঃচেতন বিদ্রোহ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—
“The simplest surrealist act consists of going into the street, revolver in hand, and shooting at random.” একটি রূপকধর্মী বর্ণনা যা প্রতীকীভাবে সমাজের গঠিত যৌক্তিক কাঠামো ভাঙার আহবন। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময়ে ফোকলোর, দ্যোতনা-তত্ত্ব (semiotics), এবং উপনিবেশ-উত্তর সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় এক মৌলিক স্থান দখল করে।
সমকালীন প্রভাব ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার
পরাবাস্তববাদের উত্তরাধিকার বর্তমানেও জীবন্ত। হ্যারল্ড পিন্টারের নাটকে ভাষার অপ্রতুলতা, সালমান রুশদির উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনার সম্মিলন এবং মারিও ভার্গাস লোসা কিংবা ইটালো কালভিনোর লেখায় অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তি ও বাস্তবতার ভাঙন পরাবাস্তববাদী প্রভাব বহন করে। তদ্ব্যতীত, postmodern metafiction-এ যে “reality is a construct” ধারণাটি আসে, তার উৎসও এই আন্দোলনের ভিতরে নিহিত।
সুররিয়ালিজম ইউরোপে যেমন রাজনৈতিক দমন ও যুদ্ধপরবর্তী হতাশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে (ব্রেতোঁ, এলুইয়ার, আরাগঁ), আমেরিকায় তা যুক্তি ও বিজ্ঞানমুগ্ধ সমাজের বিরুদ্ধচেতনায় পরিণত হয়। এদিকে এশিয়ায় সুফিবাদ ও পরাবাস্তববাদ একত্রিত হয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক বিকারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গবেষক Arthur Clemetson, Carl Ernst, Sumita Chakravarty, এবং ইব্রাহিম কায়ালভি এসব মিলনপ্রবাহকে মূল্যায়ন করেছেন তাদের রচনায়।
সমাপ্তি ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
আজকের বিশ্বে যেখানে বাস্তবতার অতিরিক্ত ভার, সংকট ও বিভ্রান্তি বিরাজমান, সেখানে সুররিয়ালিজম ও সুফিবাদ আমাদের জন্য ভাষা, শিল্প, এবং আত্মজিজ্ঞাসার এক বিকল্প ক্ষেত্র উন্মোচন করে। যুক্তি ও বাস্তবতার সীমা ভেঙে ভাব, স্বপ্ন, প্রতীক, আত্মদর্শন—এই উপাদানগুলো আধুনিক বিশ্বে নতুন সাহিত্যিক ও দার্শনিক আবিষ্কারে পরিণত হয়েছে। সুররিয়ালিজম ও সুফিবাদ, উভয়ই মানুষের চেতনার গভীরে প্রবেশ করতে চায়। আজকের দার্শনিক সংকটে, অস্তিত্বের অসারতা, জাতিগত হিংসা, ভোগবাদী বিচ্ছিন্নতায় এই দুই ধারা এক নিরন্তর প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়: “মানুষ কে? তার অভ্যন্তরীণ জগত কোথায়?” রাবেয়া বসরী বলেন: “আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কারণ তিনি ভালোবাসা।” এবং সালভাদর দালি বলেন: “I do not take drugs. I am drugs.” এই উক্তিদ্বয় এক বিমূর্ত সত্তার একান্ত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে প্রতীক—কিন্তু দু’পথই পরাবাস্তব।
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি:
1. Breton, Andre. (1924). Manifesto of Surrealism.
2. Nicholson, R.A. The Mystics of Islam.
3. Shah, Idries. The Sufis, Anchor Books, 1971
4. Izutsu, Toshihiko. Sufism and Taoism, University of California Press, 1983
5. Ernst, Carl W. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam.
6. Chittick, W. C. The Sufi Path of Knowledge.
7. Clemetson, Arthur. Mysticism and Modernism.
8. Chakravarty, Sumita. Cultural Dialectics of Indian Poetics, 1999.
9. Kayalvi, Ibrahim. Lalon Darshan, 2002.
10. Ataur Rahman. Sufibad o Bangla Kabya, 1995.
11. Hallaj, Al Mansur. Tawasin, Diwan al-Hallaj, Tr. Herbert Mason, Princeton University Press.
12. Jalaluddin Rumi. Masnavi, Divan-e-Shams.
13. Andre Breton. Nadja.
********************************