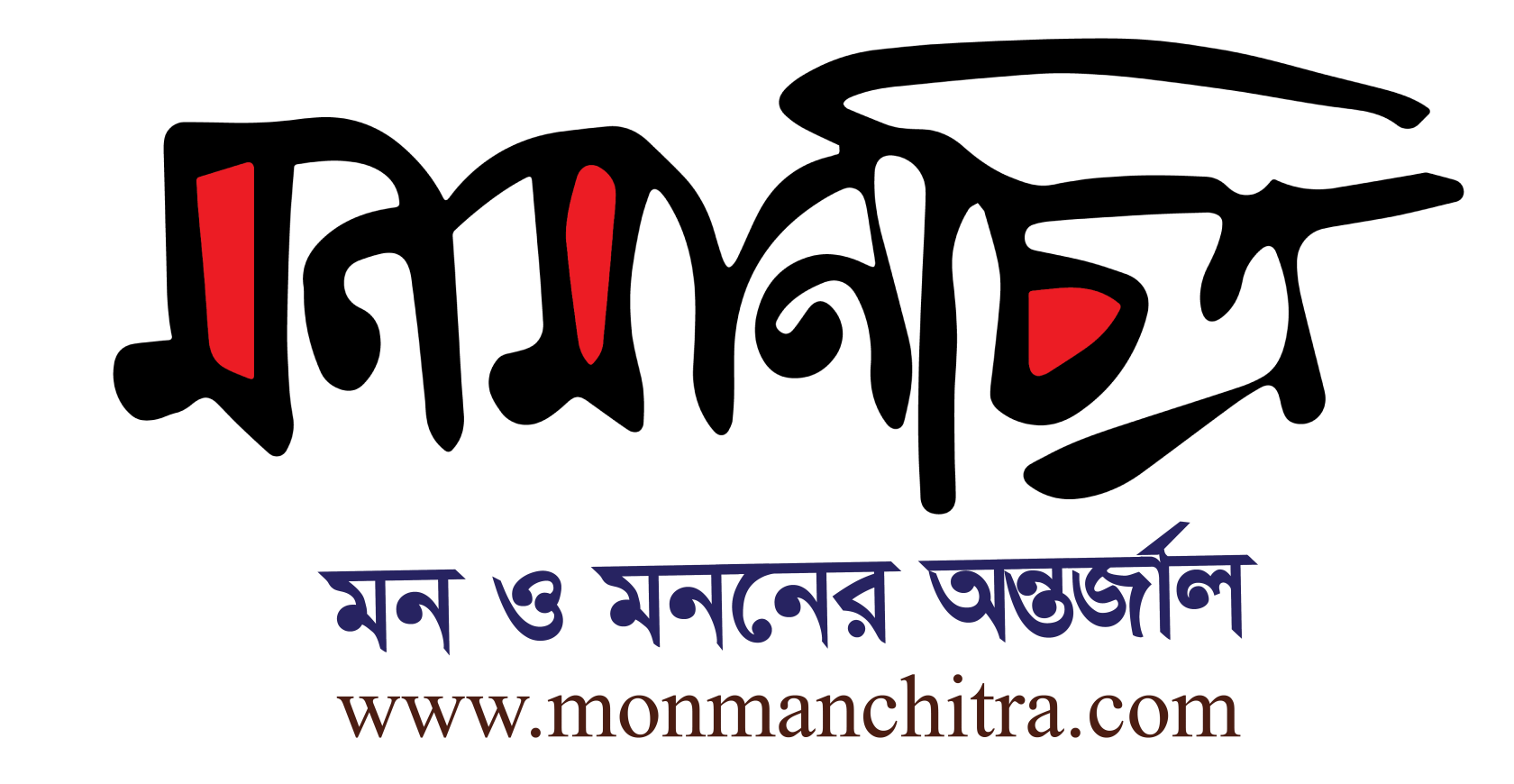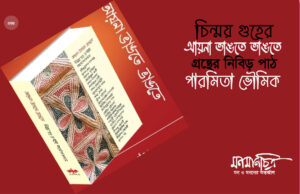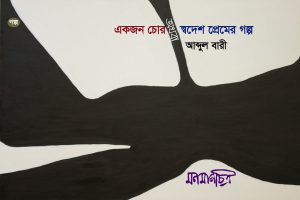শোয়েব নাঈম
‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ কী এবং কেন
একবিংশ শতকের শিল্প, সাহিত্য, সমাজচিন্তা ও সংস্কৃতিতে ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। একটি গভীরতর বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি, যা ইউরোপীয় রেঁনেসা ও তার পরবর্তী আধুনিকতার ঐতিহাসিক পরম্পরাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। পাশাপাশি এই চিন্তা ‘উত্তর-আধুনিক’ মতবাদের সীমাবদ্ধতাও উদঘাটন করেছে। রেঁনেসা এবং উত্তর-আধুনিকতাকে প্রশ্ন করাটা নিছক কোনো চিন্তার বিদ্রোহ নয়। বরং ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ হচ্ছে এক গভীর অনুধ্যানের ফল— যেখানে প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার রাজনীতিকে উন্মোচন করা হয়। আর খোঁজা হয় সেইসব কণ্ঠ, সেইসব স্মৃতি, সেইসব জীবনানুভব, যেগুলো চিরকাল প্রান্তিক বা আঞ্চলিক থেকেছে, নীরব থেকেছে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দেওয়া হয়েছে। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ শুধুমাত্র অতীত শিল্প-সাহিত্যি-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা নয়, বরং সেই ঐতিহ্যের গঠনতান্ত্রিক মূলকে পুনঃবিশ্লেষণের একটি সচেতন এবং সমালোচনামূলক প্রয়াস। এই পাঠ এক বহুস্বরিক পাঠ।যেখানে একমাত্রিক যুক্তি, প্রগতির সরলরৈখিকতা কিংবা মানবতাবাদের অভিন্ন ধারণা আর অপরিহার্য সত্য হিসেবে গণ্য হয় না। বরং এখানে উঠে আসে ভিন্ন মানবিকতার দাবি— যে মানবিকতা অঘোষিত, উপনিবেশিত, জাতিগত কিংবা লিঙ্গ-নির্ধারিত বাস্তবতার ভেতর থেকেও নিজের ভাষা খুঁজে নিতে চায়।
একবিংশ শতকের চিন্তার অভ্যুদয়ে আমরা দেখি— সাহিত্য আর কেবল নান্দনিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্র থাকে না; তা হয়ে উঠেছে একপ্রকার প্রতিরোধের ভাষা। শিল্প শুধু সৌন্দর্য নয়, হয়ে উঠেছে এক প্রকার সত্যের সাক্ষ্য। সংস্কৃতি আর কেবল অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য নয়, বরং বর্তমানে অনুপস্থিত ও অবদমিত কাহিনির পুনরুদ্ধার। ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ তাই এক অর্থে ইতিহাসের পুনর্লিখন, এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের কল্পনাকে নতুনভাবে নির্মাণ করার চেষ্টাও।এই চিন্তা আমাদের আহ্বান জানায় পুরাতন আলোয় নয়, বরং ছায়ার মধ্য দিয়ে দেখতে শেখার। যেখানে আলোকিত কেন্দ্র নয়, বরং প্রান্তের অস্পষ্টতা ও দ্বিধাগ্রস্ততা থেকেও উঠে আসে জিজ্ঞাসার দীপ্তি। যেখানে সৃজনশীলতা মানে শুধু রচনার ক্ষমতা নয়, বরং অনুচ্চারিতের প্রতি এক গভীর শ্রবণ। এইভাবেই ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ হয়ে উঠেছে একটি প্রতিরোধী চেতনা—যা প্রশ্ন তো তোলে, তেমনি নতুন এক সহনশীল, বহুমাত্রিক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবিকতাকে আহ্বান জানায়। এই আহ্বান আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ভূগোলকেই শুধু পাল্টে দেয় না, পাল্টে দেয় আমাদের উপলব্ধির ভেতরের মানচিত্রও।
‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ একবিংশ শতকে সম্ভাবনার যে দিগন্ত উন্মোচিত করেছে সেগুলি হলো:
১. যুক্তি, মানবতা ও বিশ্লেষণের পুনর্বিন্যাস।
২. প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কারের বিরুদ্ধে বিকল্প বোধের নির্মাণ।
৩. মৌলিক সৃজনের জায়গায় “প্রতিসাহিত্য”, “প্রতিশিল্প” ধারণার উত্থান।
৪. ‘উত্তর-আধুনিকতা’ এই মতবাদের বিপক্ষে ‘উত্তর-রেঁনেসা’র প্রয়োজনীয়তা।
নিচে উল্লিখিত চারটি মূল পয়েন্ট ‘উত্তর-রেঁনেসা’র আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—
১. যুক্তি, মানবতা ও বিশ্লেষণের পুনর্বিন্যাস
রেঁনেসা ও আধুনিকতা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি সার্বজনীন সত্যের প্রতিনিধি হিসেবে, মানবতাকে করেছিল একরৈখিক উন্নয়নের ক্যানভাস। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ এই অনুমানের ভেতরকার দমননীতি ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতাকে উন্মোচন করেছে। এখানে যুক্তি আর কেবল যুক্তিবাদের চর্চা নয়, বরং এই চিন্তা এটি হয়ে উঠেছে এক বহুবাচনিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্র।যেখানে প্রান্তিক এবং আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা, অবদমিত স্মৃতি ও ব্যক্তিগত সত্যের সমবেত সুরে মানবতা পুনরায় সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তা যেভাবে যুক্তিকে গ্রহণ করেছে, তা কিন্তু আর নিছক সরল ও সার্বজনীন উদ্দেশ্যে নয়। এই চিন্তা স্থানীয় মানুষের জ্ঞান, উপনিবেশবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, শরীরের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তির এক নতুন রূপ তৈরি করেছে।
উদাহরণস্বরূপ, কোনো কবিতা বা সাহিত্যকর্মে উপস্থিত স্মৃতি অনেক সময় কেবল ব্যক্তিগত অনুরণন বা আবেগসঞ্জাত মুহূর্ত নয়— বরং তা হয়ে ওঠে একটি জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও বেদনার নির্বাচিত উপস্থাপন। এই স্মৃতি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে নির্মিত এবং সংকলিত হয়। যাকে বলা হয় ‘স্মৃতির সংগঠন’। এই সংগঠিত স্মৃতি কেবল অতীতের প্রতিবিম্ব নয়, বরং বর্তমানের বয়ান নির্মাণেও সক্রিয় থাকে। যেমন— কবি শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতায় কেবল ভাষার নির্মাণ বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়; বরং এই সৃজনের অন্তরালে রয়েছে একটি ভূগোলের অভিঘাত, এক দীর্ঘ রাজনৈতিক নিপীড়নের ইতিহাস, এবং এক যৌথ স্মৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিরোধী বিন্যাস। এই পাঠে ‘স্মৃতির সংগঠন’ যুক্তির কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।কেবলমাত্র শিল্প-আলোচনার জন্য নয়, বরং ইতিহাস, ভূগোল ও মানবিক বেদনার এক বৃহৎ পাঠচক্র নির্মাণের জন্য।
————-
২. প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কারের বিরুদ্ধে বিকল্প বোধের নির্মাণ
‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তার চর্চা শিল্প-সাহিত্যের সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক সচেতন প্রতিরোধ, যে কাঠামো নির্ধারণ করে কে ‘মহৎ সাহিত্যিক’, কে ‘বিশিষ্ট লেখক’, এবং কোন সাহিত্য ‘পুরস্কারযোগ্য’। এই কাঠামো মূলত এক নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক ছাঁকনির ভেতর দিয়ে পুরস্কার, স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তার তথাকথিত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ এই প্রতিষ্ঠিত ধারা ও মানদণ্ডের বিপরীতে গড়ে তোলে এক প্রতিস্বীকৃতির ভাষ্য। যা প্রথাকে প্রশ্ন করে, প্রতিষ্ঠানকে খণ্ডিত করে এবং বিকল্প বোধের ভিতর দিয়ে এক নতুন মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এই নতুন মূল্যবোধ জনপ্রিয়তার মোহে নয়, বরং বিস্মৃত, উপেক্ষিত এবং প্রান্তিক অভিজ্ঞতার গভীরতায় গঠিত। এখানে সাহিত্য আর প্রতিষ্ঠার জন্য নয়— বরং প্রতিবাদের জন্য, নিঃশব্দের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য, অথবা নির্জনতার দাগ রেখে যাওয়ার জন্য।
‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তা এক গভীরতর প্রশ্ন উত্থাপন করে— সাহিত্যের প্রথা কে নির্ধারণ করে? কেন কিছু প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট লেখক, কবি কিংবা ছড়াশিল্পীকে ‘পুরস্কারপ্রাপ্ত’ ও ‘যোগ্য’ বলে মান্যতা দেয়, অথচ অন্যদের ‘অসফল’, ‘অসম্পূর্ণ’ কিংবা ‘একাডেমিক নয়’ বলে বাতিল করে দেয়?
‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তা সাহসের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই চিন্তা ঘোষণা করে— বিকল্পবোধ মানে কেবল প্রথার বিপরীতে দাঁড়ানো নয়, বরং তা নিজস্ব, আঞ্চলিক এবং সামাজিক কেন্দ্রবিন্দুর বাইরে থাকা কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে টেনে আনে। এই চিন্তা হচ্ছে প্রথার বাইরের চর্চা, চিন্তার অন্তর্গত দর্শন, এবং বহুস্বরিক বাস্তবতার আত্মপ্রত্যয়ী ভাষ্য।
উদাহরণস্বরূপ, “চট্টগ্রামের দশ নারীস্বর: একুশ শতকের অভিঘাতে কবিতায় বিষয়ের দ্যোতনা”— এই বিষয়টি ‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তার আলোকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়সংলগ্ন আলোচনা। এখানে প্রতিফলিত হয়েছে এক বিকল্প বাস্তবতার ভাষ্য।যেখানে নারী-অভিজ্ঞতার প্রান্তিকতা, প্রতিবাদ ও প্রতিস্মৃতির শক্তি একত্রে কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই কবিস্বরগুলি কেবল ব্যক্তিগত অনুভব নয়, বরং একুশ শতকের সামাজিক অভিঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও নান্দনিক আত্মপ্রতিষ্ঠার চিহ্ন হয়ে উঠেছে।
———-
৩. মৌলিক সৃজনের জায়গায় “প্রতিসাহিত্য”, “প্রতিশিল্প” ধারণার উত্থান
‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ এই চেতনা কোনো ঐতিহাসিক উত্তরসূরি নয়। এই চেতনা এক প্রগাঢ় মূল্যবোধের অবস্থান। যে মূল্যবোধ ‘মৌলিকতা’-র প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এখানে মৌলিকতা মানে আর কেবল নতুন কোনো কাহিনি বা রচনাশৈলীর উদ্ভাবন নয়। বরং তা এখন ঐতিহ্য, কেন্দ্র, কর্তৃত্ব এবং আদর্শ পাঠকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার একটি সামাজিক ও দার্শনিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘প্রতিসাহিত্য’ কেবল মূলধারার সাহিত্যের বিপরীত কোনো রচনা নয়। এই ভাবনা এমন এক সাহিত্যচর্চা, যা প্রথাবিরোধী, প্রতিরোধী এবং অনেক সময় নীরব বা অসম্পূর্ণ হয়েও গভীরভাবে সামাজিক। এই সাহিত্য নিরবতার মধ্যেও উচ্চারণ করে, অসম্পূর্ণতার মধ্যেও প্রকাশ করে এক চেতনার অনুরণন—যা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যকে প্রশ্ন তোলে।
তেমনই ‘প্রতিশিল্প’— চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, থিয়েটার পারফরমেন্স—এসব মাধ্যমের ভাষ্যকে প্রশ্ন তোলে। এই ভাবনা বহুমাত্রিক ও বহু-আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ, যা শ্রেণি, জাতিসত্তা, লিঙ্গ বা ভূগোলের প্রান্ত থেকে উঠে আসে।
অতএব, ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ একবিংশকে আলোকিত করেছে যে, ‘মৌলিকতা’ মানে কেবল সৃষ্টিশীল নতুনত্ব নয়। বরং কর্তৃত্বের কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে দেখা, শোনা ও প্রকাশের পথ নির্মাণ। এই চিন্তা এক প্রতিপক্ষীয় চর্চা—যেখানে শিল্প ও সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের ভাষ্য, এমনকি তার নিজস্ব ভাঙন ও নীরবতার মাধ্যমেও।
উদাহরণস্বরূপ, কবি হাফিজ রশিদ খানের কবিতা।
যেখানে কবিতাগুলি প্রতিভাবনার সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিকতার অবস্থান থেকে বিরুদ্ধতার জগৎ সৃষ্টি করেছে।
ইব্রাহিম ইকবালের হাসপাতাল-ভিত্তিক ফটোগ্রাফি প্রজেক্ট— ‘Aamar Hospital’। এই প্রজেক্টে ক্লিনিক ও হাসপাতালে পড়ে থাকা নিস্তরঙ্গ, পরিত্যক্ত, প্রান্তিক মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্প হয়ে উঠেছে ক্ষমতার নির্লিপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক প্রকার দৃশ্য-প্রতিবাদ।
——-
৪. ‘উত্তর-আধুনিকতা’ এই মতবাদের বিপক্ষে ‘উত্তর-রেঁনেসা’র প্রয়োজনীয়তা
যদিও ‘উত্তর-আধুনিকতা’ আধুনিকতার একরৈখিক যুক্তি, সার্বিক সত্য ও একক মানবতাবাদের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, তথাপি তার নিজস্ব জিজ্ঞাসা প্রায়ই আবর্তিত হয়েছে একটি নৈরাজ্যিক মতবাদের চারপাশে। যেখানে স্পষ্ট অবস্থানের বদলে রয়ে গেছে জটিলতার ছদ্মবেশ, আর নৈতিক প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছে আরও গূঢ় সংশয়। চিন্তা, ভাষা ও অভিজ্ঞতার আপেক্ষিকতা তুলে ধরতে গিয়ে ‘উত্তর-আধুনিকতা’ অনেক সময়ই নিজেকে দায়হীন এক বীক্ষার মধ্যে বন্দি করেছে। এই দার্শনিক ফাঁকিগুলির বিপরীতে উঠে আসে ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’—যা কেবল প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এক বিকল্প নির্মাণের সূত্রপাত। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ নতুন এক নৈতিক বোধের সূচনা করেছে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে—যেখানে সামাজিক সত্য, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দায় একে অপরকে প্রশ্ন করে, আবার পরিপূরকও হয়। সাহিত্যে এটি ফিরিয়ে এনেছে সমাজ ও রাজনীতির তীব্র অনুরণন। আর দর্শনে সৃষ্টি করেছে কেন্দ্রবিমুখ অথচ দায়বদ্ধ বিরোধিতার এক জটিল অথচ সংবেদনশীল কাঠামো।
এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বিদ্রোহ করে থেমে থাকে না; বরং তা গড়ে তুলতে চায় নতুন কিছু। একটি নতুন ভাষা, নতুন মানবতা এবং নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ। যেখানে ‘উত্তর-আধুনিকতা’ সব কিছুর অর্থকে অনিশ্চিত ও ভাসমান করে তোলে, সেখানে প্রশ্ন ওঠে—এই ভাসমানতা কি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও সমাজের প্রতি কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না? এই অনিশ্চয়তা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তিকে দুর্বল করে না?
‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ এই প্রশ্নগুলোর একটি গভীর ও সুসংবদ্ধ উত্তর দেয়। এই চিন্তা অনুভব করিয়ে দেয় যে, ভাষার অনেক মানে হতে পারে। তবুও সেই মানেগুলোর দায়িত্ব আছে মানুষের ন্যায্যতা ও অধিকারের প্রতি। এখানে ভাষা কেবল খেলার জিনিস নয়, বরং অন্যায়, দমন আর ভুলে যাওয়া ইতিহাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ভাষা এখানে ভবিষ্যত গড়ার এবং হারিয়ে যাওয়া সত্যকে ফিরিয়ে আনার একটি উপায়।
উদাহরণ ১ :
উত্তর-আধুনিক প্রবণতা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি
এই উপন্যাসে শহরের মধ্যবিত্ত তরুণেরা জঙ্গলে ছুটি কাটাতে যায়। তারা সমাজ থেকে কিছুটা ‘বিচ্ছিন্ন’, সংকটবোধহীন, এবং অস্তিত্ব সংকট নিয়ে ভাবিত—কিন্তু কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান বা সংগ্রাম নেই। এই উপন্যাস এক ধরনের বিনির্মাণমূলক আত্মদর্শন যেখানে তারা তাদের জীবন ও সম্পর্ক নিয়ে সংশয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো সামাজিক দায় বা প্রতিরোধমূলক ভাষা এতে অনুপস্থিত।
এই উপন্যাস উত্তর-আধুনিক চেতনার উদাহরণ। যেখানে সৌন্দর্য, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মবিশ্লেষণ আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই, দায় নেই।
উদাহরণ ২:
চলচ্চিত্রে: সত্যজিৎ রায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ বনাম ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’
প্রতিদ্বন্দ্বী-তে (১৯৭০) সত্যজিৎ রায় মূলত তরুণদের অস্তিত্ব সংকট, চাকরির সমস্যা ও মূল্যবোধ নিয়ে অনুসন্ধান করেন—একটা পরিমিত, দর্শনগত অথচ বিচ্ছিন্ন স্বর।
এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা পটভূমি হয়ে থাকে, কিন্তু তা প্রতিরোধে রূপ নেয় না—এটা অনেকটাই উত্তর-আধুনিক ঘরানার আত্মদর্শন।
অন্যদিকে,
মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)-তে ঋত্বিক ঘটক দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিরোধী ভাষা গড়ে তোলেন।
তাঁর সিনেমা কেন্দ্রবিমুখ, ভাঙা-জোড়া বাস্তবতা দিয়ে গঠিত—তবুও তা রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহিমূলক ও নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ ।
———
উপসংহার:
উত্তর-রেঁনেসা কেবল একটি নয়া-তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরং একপ্রকার ভাবনার সংস্কার যা—
জনসাধরণকে যুক্তি দিয়ে সংযুক্ত করে ,
প্রথাকে ভাঙে,
সৃষ্টিকে প্রতিরোধে রূপান্তরিত করে,
এবং নতুন চিন্তার ভেতর দিয়ে ন্যায় ও সত্যের নতুন সংজ্ঞা গড়ে তোলে।
‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা’ একপ্রকার বিকল্প মানবিকতার পুনর্জাগরণ। যা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, ক্ষমতার বাইরে এবং আঞ্চলিক গভীরতা থেকে।
————–
উত্তর-রেঁনেসা ও সাহিত্যের আত্মশুদ্ধি :
——————————————
যাঁরা সামাজিক মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পুরস্কারনির্ভর শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অর্থলিপ্সু ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করে চলেছেন, তাঁরা নিছক অভিযোগকারী বা হতাশ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নন। বরং তাঁরা হয়ে উঠেছেন এক নতুন চিন্তার ধারক, যাঁদের চিন্তাকে ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তক’— এমন প্রতিস্থাপনে অভিহিত করা হয়। এই পরিভাষাটি তাদের সাংগঠনিক পরিচয়ের নয়, বরং হচ্ছে এক বৌদ্ধিক ও নান্দনিক অবস্থানের রূপান্তর। ‘উত্তর-রেঁনেসা’ কেবল ঘটমান সময়ের অনুরণন বা সাময়িক বিক্ষোভের নাম নয়, এ এমন এক অন্তঃসারময় তাত্ত্বিক উচ্চারণ, যা আত্মচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের এক যৌথ ক্ষেত্র নির্মাণ করে। এই চিন্তনের কেন্দ্রে রয়েছে এক বহুমাত্রিক প্রশ্নচিহ্ন— যা পুরস্কার, স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তার তথাকথিত প্রথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাদের নৈতিক ও নান্দনিক ভিত্তি থেকে। এই প্রতিরোধ— যুক্তির কাঠামো, বিশ্লেষণাত্মক দ্বান্দ্বিকতা ও বিকল্প বোধের আলোকে গড়ে ওঠে। সেখানে সাহিত্য আর নিছক পাঠ্য বস্তু নয়, হয়ে ওঠে মানবিক প্রশ্ন, নৈতিক প্রতিরোধ এবং নতুন সাংস্কৃতিক নির্মাণের ক্ষেত্র।
‘উত্তর-রেঁনেসা’ শব্দবন্ধটি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে একাধিক স্তরে এর তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়। এ কেবল ঐতিহাসিক রেনেসাঁ আন্দোলনের উত্তরসূরি নয়, বরং এক প্রেক্ষিত-পরিবর্তনমূলক মননচর্চা, যা সংস্কার নয়, বরং কাঠামো-বিনির্মাণে বিশ্বাসী। রেনেসাঁ যেমন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও অন্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তি, মানবতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল, তেমনই উত্তর-রেঁনেসা চিন্তা সমকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত মেধাহীন জনপ্রিয়তা, মননহীন সাহিত্যবাজার এবং ক্ষমতানির্ভর পুরস্কার-রাজনীতির বিরুদ্ধে এক প্রাজ্ঞ ও পরিশীলিত প্রতিরোধ নির্মাণ করে। এই চিন্তার ভিত্তিভূমি তৈরি হয় অন্তর্জিজ্ঞাসা, যুক্তিনিষ্ঠ পাঠ এবং মননশীল বিশ্লেষণের উপর। এই চিন্তকেরা একদিকে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির তথাকথিত প্রধান স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিকল্প বয়ান নির্মাণ করেন; অন্যদিকে সমাজের গভীর স্তরে অবস্থিত শ্রেণি, ক্ষমতা ও সংস্কারবৃত্তিকে প্রশ্ন করে গড়ে তোলেন প্রতিসাহিত্য, প্রতিশিল্প, এবং প্রতিসংস্কৃতির নতুন ভাষ্য। এই ভাষা আবেগনির্ভর নয়, বরং বহুমুখী চিন্তার সাযুজ্যে যুক্তিনির্ভর। এই চিন্তা কেবল প্রত্যাখ্যানের ভাষা নয়, বরং প্রতিসৃষ্টির এক অন্তর্লীন প্রচেষ্টা।
উত্তর-রেঁনেসা চিন্তকেরা জানেন, পুরস্কার ও জনপ্রিয়তা যদি লেখালেখির চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তবে সাহিত্য তার মৌলিক চেতনা এবং উদ্দেশ্য হারায়। কারণ, সাহিত্য হলো প্রশ্নের ক্ষেত্র, সন্দেহের ভাষা, এবং আত্মবীক্ষণের আয়না। সেখানে বহিরাগত স্বীকৃতির প্রলোভন একধরনের সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা রচনা করে। যার মাধ্যমে লেখক হয়ে ওঠেন প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার ধারক, স্বাধীন চিন্তার নয়। এই চিন্তা মূলত একধরনের মেটা-প্রতিবাদ, অর্থাৎ প্রতিবাদের প্রতিস্বর। এই প্রতিস্বর সাহিত্যকে পুনর্নির্মাণ করে ভেতর থেকে। এখানেই ‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তা এর বিশিষ্টতা দাবি করে, কারণ এ কেবল প্রতিক্রিয়া নয়,—এ হচ্ছে বীক্ষণধর্মী নির্মাণ, পর্যালোচনা এবং বিকল্প চেতনার এক গভীর অনুসন্ধান। এর মধ্য দিয়ে একটি নতুন সাহিত্যচিন্তা জন্ম নেয়, যা ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠাননির্ভর সাহিত্যধারাকে অতিক্রম করে একধরনের নৈতিক ও নান্দনিক চেতনার পুনর্নির্মাণে নিযুক্ত হয়।
‘পুস্কারবিরোধিতা’ এই বিষয়টি নিছক এক নৈতিক আপত্তি নয়, এ হচ্ছে একটি রূপান্তরমুখী, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক অবস্থান, যা সাহিত্যচর্চার অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে গভীরভাবে প্রশ্ন করে। এই বিরোধিতা কোনো আবেগপ্রসূত প্রতিবাদ নয়, বরং এক ধরণের বিশ্লেষণাত্মক প্রত্যাখ্যান— যা প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং তথাকথিত স্বীকৃতির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে নির্মোহ যুক্তির আলোয় পর্যালোচনা করে।যখন সাহিত্য একটি স্বাধীন অভিব্যক্তি থেকে সরে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের পোষণ ও তোষণের ছায়াচ্ছন্ন এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেই সাহিত্যের মৌলিক সৃজনশীলতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে প্রাতিষ্ঠানিক ভব্যতার বর্মে আচ্ছাদিত; তার আবেগ আর চেতনা অভিভাবকতান্ত্রিক কাঠামোর অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে। তখন সাহিত্য আর প্রশ্ন তোলে না—বরং অনুমোদিত ভাষ্যকে পুনরাবৃত্তি করে।এই সংকটের প্রেক্ষিতে ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তক’ উদ্ভাসিত হন একধরনের বিকল্প-সচেতনতার বাহক হিসেবে। তাঁরা কেবল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যানই করেন না, বরং সেই সংস্কৃতির নেপথ্যে যে ক্ষমতা, অর্থনীতি এবং মতাদর্শের জটিলতা লুকিয়ে থাকে, সেটিকেই উন্মোচন করেন। তারা সাহিত্যের মধ্যে নির্মাণ করেন এক প্রতি-ভাবনার স্পেস— যেখানে প্রতিস্থাপন হয় মূল্যায়নের মাপকাঠি, এবং প্রশ্ন করা হয়: সাহিত্যিক স্বীকৃতি কাদের জন্য, কারা দেয়, কেন দেয়?
‘প্রতি-ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি’ এইখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতি-ভাবনা স্বীকার করে যে, সাহিত্যের স্বীকৃতি যদি রাজনৈতিক আনুগত্য কিংবা বাণিজ্যিক সুবিধার বিনিময়ে প্রদত্ত হয়, তবে সেই স্বীকৃতি আসলে সাহিত্য নয়, বরং এক প্রকার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার ফল। এর ফলে সৃজনশীলতা অন্তঃসার হয়ে যায়, আর সাহিত্য পরিণত হয় একরকম অনুগত পাঠ্যতন্ত্রে। যেখানে মূল্যায়ন নয়, বরং প্রতিষ্ঠাবান্ধব ছাঁচে ফিট হওয়াই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থানের বিপরীতে ‘উত্তর-রেঁনেসা চিন্তক’ সাহিত্যকে ভাবেন এক নান্দনিক মুক্তির সত্তাতে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নয়, বরং আত্মানুসন্ধান, চিন্তার তীক্ষ্ণতা এবং ভাষার ভেতরকার সত্যের পরিস্ফুটনই হয়ে ওঠে সাহিত্যিক মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড। তাঁরা মনে করেন, সাহিত্য কেবল ‘প্রাপ্তি’ নয়—বরং প্রশ্ন, সংশয়, প্রত্যাখ্যান এবং বিকল্প চেতনার একটি জীবন্ত পাঠভাষ্য। তাঁদের যুক্তির কাঠামোতে স্পষ্ট হয়: পুরস্কারপ্রাপ্তি নয়, বরং পুরস্কারের যোগ্যতার ভিতরে যে মূল্যায়ন-সংকট লুকিয়ে থাকে, সেটিকেই আগে খতিয়ে দেখা জরুরি। একটি লেখা কেন মূল্যবান— এই প্রশ্নটি পুরস্কার পাওয়ার আগে পাঠক, সমাজ এবং সময়ের সঙ্গে লেখার গভীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বোঝা প্রয়োজন। না হলে সাহিত্য আর মুক্ত অভিব্যক্তি থাকে না; তা হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির এক অনুগত সংস্করণ।
এ প্রসঙ্গে আমরা গ্রামশিয়ান ধারণা ‘হেজেমনি’ (hegemony) ব্যবহার করতে পারি। সাহিত্যে হেজেমনি তখনই গড়ে ওঠে, যখন কিছু প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে দেয়, কে ‘মহান’, কে ‘প্রসিদ্ধ’, কে ‘চর্চাযোগ্য’। উত্তর-রেঁনেসা চিন্তকরা সেই হেজেমনিক ক্ষমতা কাঠামোকে অস্বীকার করেন। তারা সাহিত্যকে ‘প্রতিস্রোত’-এর পরিসরে নিয়ে যান, যেখানে জনপ্রিয়তা নয়, গূঢ় অন্তর্জিজ্ঞাসা, ধ্যানমগ্ন বিশ্লেষণ এবং অনুভবের প্রকৃত জিজ্ঞাসা থাকে মুখ্য। এই চিন্তাপ্রক্রিয়ায় জার্মান দার্শনিক আদর্নোর ‘negative dialectics’-এর ধারাও আমরা দেখতে পাই, যেখানে ইতিবাচক ঘোষণা নয়, বরং সমালোচনাই হয়ে ওঠে একটি সৃষ্টিশীল পদ্ধতি। উত্তর-রেঁনেসা চিন্তকেরা মূলত এভাবেই চিন্তার বিষয়গুলি প্রতিফলিত করেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ ঘোষণার চেয়ে প্রশ্ন, দ্বান্দ্বিকতা এবং কাঠামোভাঙার দিকে মনোনিবেশ করেন। সাহিত্যে তাঁরা যে প্রতিবাদ নির্মাণ করেন, তা আসলে ‘কাউন্টার-লিটারেচার’। এই প্রতিসাহিত্য কোনো একক আঙ্গিকে নয়, বরং বহুস্তরীয় চেতনায় সংযোজিত।যেখানে ভাষা, রাজনীতি, সমাজ ও নৈতিকতা একসঙ্গে— প্রবাহমান ধারায় অন্তর্ঘাত ঘটান।
এই ধারায় ‘উত্তর-রেঁনেসা’ হয়ে দাঁড়ায় এক ‘ঐতিহাসিক চেতনার অভ্যুত্থান’। যেখানে সাহিত্য আর প্রতিষ্ঠান নয়, পাঠকের সংবেদনশীলতা, লেখকের অন্তর্দৃষ্টি এবং চিন্তার স্বাতন্ত্র্যই হয়ে ওঠে প্রধান অনুষঙ্গ। এই আন্দোলন একটি নতুন বোধ তৈরি করে, যার ভাষা— তীক্ষ্ণ, তির্যক, কিন্তু গভীরভাবে নান্দনিক। এবং ঠিক এখানেই উত্তর আধুনিকতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তর আধুনিকতা যেখানে সত্যকে আপেক্ষিকতা আর খণ্ড-দৃষ্টিভঙ্গিতে ভেঙে দেয়, সেখানে উত্তর-রেঁনেসা একটি অন্তর্নিহিত নৈতিক কাঠামোতে দাঁড়িয়ে সত্য ও সৌন্দর্যকে যুক্তি ও প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ করে। উত্তর-রেঁনেসা চিন্তকেরা সাহিত্যকে ফেরাতে চান এর আত্মিক গাম্ভীর্যে, এর সৃষ্টিশীল বিবেকের তীব্রতায়। তাঁরা মনে করিয়ে দেন— সাহিত্যের সম্মান কোনো পদক বা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সাহিত্যের অন্তর্গত সত্য এর তাত্ত্বিক গভীরতায় অবস্থিত। আর সেই গভীরতার আলোকে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাই প্রধান ভাষ্য হয়ে ওঠে।
—————-
সাহিত্যের মৌলিকত্বের প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা
—————————————————————–
✺ সাহিত্যে ‘মৌলিকত্ব’— এই ধারণাটি বহু পুরোনো, কিন্তু এর ব্যাখ্যা এবং চর্চা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বিবর্তিত হয়েছে। এককালে সাহিত্যের মৌলিকতা বলতে বোঝানো হতো এমন কিছু যা সম্পূর্ণরূপে নতুন সৃষ্টি, যা পূর্বতন কোনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি নয়।
এককালে মৌলিকতা মানে ছিল ‘অন্যদের থেকে আলাদা কিছু’ বলা, ‘কখনো না বলা’ নতুন কোনো অভিজ্ঞতা তুলে ধরা। এক ধরনের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যা অন্যের ভাবনা নয়, বরং নিজেরই একান্ত স্বর। কিন্তু একবিংশ শতকের পাঠ-সংস্কৃতিতে, যেখানে পাঠান্তর, পুনঃপাঠ, আন্তঃপাঠিকতা এবং এমনকি অনুকরণও স্বীকৃত রচনাকৌশলে পরিণত হয়েছে, সেখানে প্রথাগত মৌলিকতার ধারণা এখন বিভ্রমে পরিণত হয়েছে। বরং তা একধরনের কাল্পনিক বা অতীতমোহিত ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের প্রেক্ষাপটে প্রথাগত মৌলিকতার ধারণাটি কার্যত এক নান্দনিক অনুমান, যার বাস্তব ভিত্তি ক্রমেই ক্ষীয়মাণ। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায়, আমাদের প্রয়োজন এক বিকল্প মৌলিকতার ধারণা। যা বাহ্যিক অভিনবত্বে নয়, উপস্থিত থাকবে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, ভাবনার ঘনত্ব ও তার বাস্তব-সংবেদী চিন্তার প্রতিস্বর। এই মৌলিকতা কোনো একক ভাষা, রীতি বা অলংকারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর প্রয়োগ হবে লেখকের দেখা, শোনা, অনুভবের এমন এক নির্মিত রূপে। যা পরিচিত বাস্তবতাকেও অচেনা করে তোলে। সমকালীন সাহিত্যিকের আসল কাজ আজ আর ‘নতুন’ কিছু বলা নয়, বরং পুরনোকে এমনভাবে দেখা ও দেখানো, যাতে তা নিজেকে নতুন করে অনুধাবনের আহ্বান জানায়। আজকের সাহিত্যে কেবল ‘নতুন কিছু’ বলার চেয়ে ‘চেনা বিষয়কে নতুন চোখে দেখানো’র দিকেই মনোযোগ দিতে হয়।
✺ বিশ্বায়নের অভিঘাতে, যেখানে ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি এক অন্তহীন আন্তঃপ্রবাহে মিশে যাচ্ছে, সেখানে সাহিত্যের মৌলিকতা আর বাহ্যিক অভিনবতায় নয়, প্রকাশ পায় টেকসই ভাবনার অন্তঃসার ও নৈতিক উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রতিফলনে। কবিতা হোক, গদ্য, কিংবা চলচ্চিত্রের কাহিনি —সাহিত্যকে হয়ে উঠতে হয় এমন এক সংবেদনার ক্ষেত্র, যেখানে লেখক নিজের অভিজ্ঞতা ও বীক্ষাকে রূপ দেন এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বাচনে। এই বাচন কখনো সংহত, কখনো অনুপুঙ্খ, আবার কখনো ভাষাহীন নিস্তব্ধতায় উচ্চারিত। কিন্তু তা পাঠককের সীমাবদ্ধকে নাড়িয়ে দেয়, প্রশ্ন তোলে, বোধ প্রসারিত করে। এ হল সেই মৌলিকতা, যা ‘নতুন কিছু বলার’ প্রয়োজন অনুভব করে না, বরং চেনা অভিজ্ঞতার মধ্যেও এমন কিছু উচ্চারণ করেন, যা পাঠক বা দর্শকের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল এতদিন। অর্থাৎ , এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা হ’ল— নতুন কিছু ‘না বলার’ মধ্যেও এমন কিছু বলা, যা পাঠক আগে অনুভব করেনি।
✺ সাহিত্যে ‘মৌলিকত্ব’ দীর্ঘকাল ধরেই সৃজনশীলতার পরম মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এর ঐতিহাসিক উৎস নিহিত রয়েছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর চিন্তাপরিসরে।যেখানে ‘স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর’ ও ‘প্রথম উচ্চারণ’-কে সৃজনের শ্রেষ্ঠতম গুণ বলে বিবেচনা করা হতো। শিল্পী বা লেখক যেন এক প্রকার অলৌকিক সৃষ্টিশক্তির অধিকারী— এই ‘ঈশ্বরতুল্য নির্মাতা’র ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে ‘originality’-র রোমান্টিক আদর্শ।
কিন্তু একবিংশ শতকের সাহিত্য-বাস্তবতায় এসে এই ধারণা আর অবিকল টিকে থাকেনি। আজকের সাহিত্যচর্চা একটি বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষিক প্রেক্ষাপটে বিকশিত হচ্ছে। যেখানে পুনঃপাঠ, পাঠান্তর (transcreation), আন্তঃপাঠিকতা (intertextuality), অনুকরণ (pastiche), এবং ‘সিটেশনালিটি’ (citation-based writing)– এসবই গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত রচনাকৌশল। । এই প্রেক্ষিতে ‘লেখা’ আর একক কণ্ঠস্বরের একান্ত উচ্চারণ নয়; বরং তা হয়ে উঠেছে এক টেক্সটচক্রের অন্তর্ভুক্ত— এক জালের মতো বোনা ভাষ্যসমষ্টি, যেখানে অনুরণন, প্রতিধ্বনি ও প্রভাবের সঞ্চার বহুরৈখিক। এই জটিল বয়ানে লেখকের ভূমিকাও আজকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। সাহিত্যিকের কাজ আজ আর কেবল নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয়, বরং বিদ্যমান অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্য দিয়ে এমন এক বীক্ষা তুলে ধরা— যা পূর্বানুভূত হলেও, পূর্ববিবেচিত নয়। মৌলিকতা, এই পরিপ্রেক্ষিতে, এক অলঙ্কারিক অগ্রাধিকার নয়, বরং হয়ে ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যার বিশিষ্টতা।
✺মৌলিকতা মানে কী—অভিনব বিষয় না নতুন বীক্ষা?
প্রথাগতভাবে আমরা মৌলিকতাকে বিচার করি বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব দিয়ে— অর্থাৎ যা আগে কখনো লেখা হয়নি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর বাস্তব নয়, কেননা মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং সাহিত্যের ইতিহাস এত বিস্তৃত ও বহুবর্ণ যে ‘একেবারে নতুন’ কিছু বলা প্রায় অসম্ভব। বরং আজকের সাহিত্যিক চ্যালেঞ্জ হল— চেনা বিষয়কে এক অনন্য ও সংবেদনশীল দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা। যেমন, প্রেম, মৃত্যু, স্বপ্ন, নিঃসঙ্গতা, নিপীড়ন— এসব চিরায়ত বিষয় বারবার এসেছে সাহিত্যে, কিন্তু প্রতিবারই তা নতুনভাবে ধরা দিয়েছে লেখকের বাচনিক কৌশল, ভাবনার গভীরতা এবং সমাজ-বাস্তবতায় সংযুক্তির কারণে। কাজেই আজকের দিনে মৌলিকতা মানে ‘অভিনব অভিজ্ঞতা’ নয়, বরং অভিজ্ঞতার ‘অভিনব রূপান্তর’।
✺ ভাষা, শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির ত্রিমাত্রিকতা
এই নতুন মৌলিকতা কেবল ভাষা বা শৈলীর নিরীক্ষা নয়, বরং এ হচ্ছে এক গভীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে রাজনৈতিক, সামাজিক, নারীবাদী, উপনিবেশ-পরবর্তী, বা এমনকি পরিবেশবাদী। যেকোনো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বাস্তবতাকে পাঠ করা ও তাকে বাচনিক রূপ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, সাদাত হাসান মান্টো’র লেখা ‘টোবাটেক সিং’ একটি পাগলের কাহিনি হলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি দেশভাগের নৈরাজ্য ও মানবিক ভাঙনের গভীর রাজনৈতিক পাঠ তৈরি করে। একইভাবে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অনেকে নিখুঁত গদ্যে আত্মজৈবনিক ও সামাজিক গল্প বললেও তাদের মৌলিকতা নিহিত থাকে অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির সততায় ও বাচনিক শৈলীতে।
✺ বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও লেখকের নৈতিক দায়
বিশ্বায়নের সময়ে লেখক অবস্থান করছেন এক বহুসংস্কৃতি-সংলগ্ন বাস্তবতায়। যেখানে ভাষা, চিন্তা ও রুচির প্রথাগত সীমারেখা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি যেমন ভাবনার গতি ও বিস্তার বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে একটি ভোগসর্বস্ব ব্যবস্থায়। যেখানে সাহিত্যও ক্রমে পণ্যায়নের বিপন্ন সীমান্তে। এই টালমাটাল বাস্তবতায় লেখকের মৌলিকতা আর কেবল শৈলীর অভিনবতায় সীমিত থাকে না; তা নির্ধারিত হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, নৈতিক দায়বোধ ও সত্য উচ্চারণের সাহসে। তিনি সমাজকে কী দৃষ্টিতে দেখেন, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন ভাষায়, কোন বাচনে পাঠকের কাছে তুলে ধরেন—এই বিবেচনায় উন্মোচিত হয় তাঁর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য।মৌলিকতা এখানে হয়ে ওঠে এক অন্তর্জাগতিক দায়, নিজস্ব সত্যকে বলার গভীর নিষ্ঠা। সে সত্য হয়তো খুবই সাধারণ, নৈমিত্তিক জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা; কিন্তু যখন সেই অভিজ্ঞতা ভাষায়, অথবা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় সংবেদনের এমন এক তীব্রতায়, যা পাঠকের, অথবা দর্শকের চেতনাকে উদ্বেল করে, বোধের পরিসরকে প্রসারিত করে, তখনই তা সাহিত্যের এবং শিল্পের নির্ভুল মৌলিকতার দাবিদার হয়ে ওঠে। এইরকম সৃষ্টিশীল ব্যতিক্রম আমরা প্রত্যক্ষ করি জাহেদ মোতালেব, সৈকত দে ও শোয়ায়েব মুহামদের কথাসাহিত্যে— যাঁরা নিখুঁত দৈনন্দিনতার ভেতর নির্মাণ করেছেন এক অন্তর্লীন গভীরতা। যেখানে অভিজ্ঞতার স্বর, সাহিত্যের ভাষাভঙ্গি, ও মানবিক অনুরণন অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে এক অনন্য সাহিত্যভুবন। এই প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে তানিম নূর পরিচালিত জুন ২০২৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘উৎসব’-এও। যেখানে জীবনের অতিসাধারণ, প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা ক্ষণগুলো এমন সংবেদনশীলতা ও নান্দনিক রূপ পেয়েছে। যেখান থেকে তা বড়পর্দা অতিক্রম করে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়েছে দর্শকের মননে। এই চলচ্চিত্র কেবল একটি গল্প নয়; শিল্পটি হয়ে উঠেছে এক সমকালীন বয়ান। যেখানে মৌলিকতা গড়ে উঠেছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতার বাস্তব অভিব্যক্তিতে।
✺ উপসংহার: এক নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন
সাহিত্যে যেভাবে ‘মৌলিকতা’ দীর্ঘদিন যাবত এক ‘অভিনব বিষয়’ উদ্ভাবনের অর্থ নিয়ে সমার্থক ছিল, সেই চেতনা একবিংশ শতকের জটিল, বহুরৈখিক বাস্তবতায় এই সংজ্ঞা আজ আর এরকম একমুখীতায় যথেষ্ট নয়। সমকালীন সাহিত্যচর্চায় এখন মৌলিকতার পুনর্ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রয়োজন। এমন একটি বিশ্লেষণ , যা ধারণ করতে পারে বাচনিক বহুত্ব, আন্তঃসংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিক্রমী রূপান্তর। একবিংশ শতকে লেখকের মৌলিকতা মাপা উচিত এই প্রশ্নে যে, তিনি অভিজ্ঞতাকে কীভাবে রূপান্তর করেন? তাঁর ভাষা কতটা অন্তঃসারবাহী ও সংবেদনশীল? তিনি কীভাবে পাঠকের পরিচিত বাস্তবতাকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণে উদ্ভাসিত করতে পারেন?
এই নতুন ধারণার মৌলিকতা এখন আর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণা এখন নিহিত দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে, বর্ণনার বিন্যাসে, এবং ভাষার অন্তর্লীন বোধে। এখন মৌলিকতা মানে— শব্দ নয়, দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতা; বিষয় নয়, বিন্যাসের নান্দনিক গভীরতা; কৌশল নয়, উপলব্ধির রূপান্তর। শিল্প ও সাহিত্যের প্রকৃত শক্তি এখানেই যে, এই ধারণা পরিচিত বাস্তবতাকে নবদৃষ্টিতে আবিষ্কার করায়।
(এই আলোচনাটি ‘উত্তর-রেঁনেসা’ চিন্তার আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে)
**************************