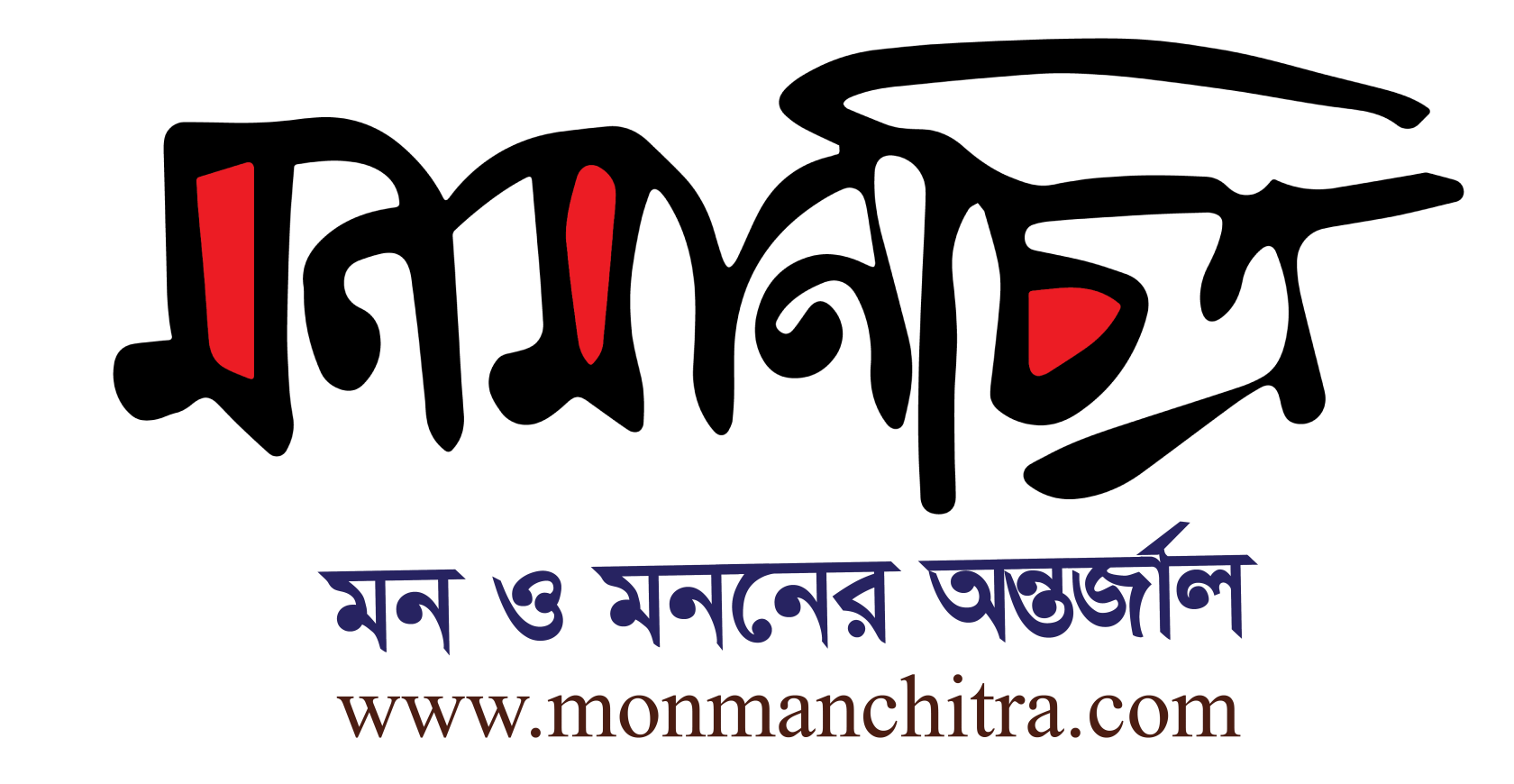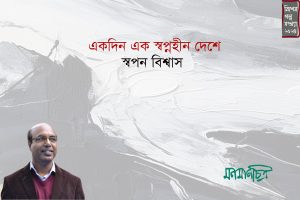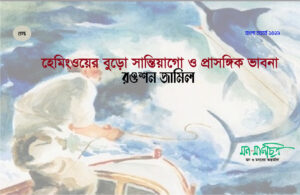লুৎফুল হোসেন
সমকালীন সাহিত্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনুধ্যায়
পাঠশালা যখন ইশকুল হলো স্টিম ইঞ্জিন পালটে তখন ডিজেল ইঞ্জিনে রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে। সেই আমলে গোটা দিন পার হয়ে যাওয়া যাত্রাপথ এখন চার ঘণ্টায় পাড়ি দেয় আন্তনগর ট্রেন। একসময় দেশের ভিতর একটা চিঠি পৌঁছাতে সাত দিন আর দেশের বাইরে পৌঁছাতে লাগতো এক-দেড় মাস, এখন লহমায় পৌঁছে যায় যে কোনো দূরত্বে। তবে এখনকার চিঠি সেই আগের দিনের চিঠিও নয়, আর চিঠির মাধ্যম এখন পোস্ট অফিস নয়; এখন পত্রালাপের মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, টুইটার, স্ন্যাপচ্যাট, টেলিগ্রাম। আগের দিনের দীর্ঘ চিঠিরা এখন বিবিধ মাধ্যমে আদান-প্রদান হওয়া বিবিধ কিসিমের ক্ষুদে বার্তা। আগের দিনে চিঠিগুলো মানুষ সংগ্রহে রাখতো, বিখ্যাতদের চিঠিপত্র বই আকারে প্রকাশও পেতো। এখন চিঠির আয়ু বড়ো ক্ষয়িষ্ণু, স্ন্যাপচ্যাটের মতো কিছু কিছু মাধ্যমে তো তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। আর তাই পুরোনো যোগাযোগের বোঝা বইতে না হওয়ায় বরং এ যুগের তারুণ্যের কাছে এর আলাদা রকম জনপ্রিয়তা।
একসময় সন্ধ্যা নামলে আলো জ্বালাতে, তখনকার প্রচলিত ভাষায় – সন্ধ্যাবাতি দিতে হলে হারিকেনের তেল সলতে ঠিক করে, চিমনির কাচ মুছে আলো জ্বালাতে সময় লাগতো অন্তত আট-দশ মিনিট। বিদ্যুৎ এসে গেলে জীবন গতিময় হলো, সুইচ টিপলেই লহমায় জ্বলে ওঠে আলো। হালে তো সুইচ টেপার কষ্টটাও করতে হয় না, বাতির সীমানায় এলে সেন্সরই আমার হয়ে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আলোর জন্যে দশ মিনিট অপেক্ষায় যখন আমরা অভ্যস্ত ও অভিযোগহীন ছিলাম, তা আমাদের ধৈর্যশীলও করে রেখেছিল। সেই আমরাই আজ সুইচ টেপা মাত্রই বাতিটা না জ্বললে ধৈর্যহারা হই। আমাদের পরের প্রজন্ম, যাদের হারিকেন বা হ্যাজাকের আলো দেখার অভিজ্ঞতাটুকুও নেই, তারা! তাদের তো কোনোকালে ধৈর্য ধরার সেই অভিজ্ঞতাটুকু নেয়াই হয়নি। তাই জীবন যাপনের ধারণা এবং ব্যবস্থাগুলোই পালটে গেছে আজ। আগে একটা বাড়িতে সব ঘরে, মানে সব রুমের আলাদা হারিকেন থাকতো না। পড়ার ঘড়ের হারিকেনটা খাওয়ার সময় চলে আসতো খাওয়ার ঘরে। এখন প্রতি রুমে থাকে একাধিক বাতি, একটা না জ্বললে আরেকটা জ্বলবেই।
একসময় স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতার নৈমিত্তিক একটা বিষয় ছিল, ‘বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ’। স্কুলে পড়েছে কিন্তু এই শিরোনামের পক্ষে-বিপক্ষে বলার বা নিদেন পক্ষে শোনার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের প্রজন্মে এমন মানুষ পাওয়া যাবে খুব কম। গতি আমাদের জীবনটাকে আমনতরো পালটে দিয়েছে যে, একসময় অপেক্ষার দীর্ঘ অভ্যস্ততায় থাকা আমরাও মেসেজটা সঙ্গে সঙ্গে না গেলে, বাতিটা সুইচ টেপা মাত্রই না জ্বললে মানতে পারছি না। পরের প্রজন্মের কাছে তাই ধৈর্যের সেই নজির আশা করাটা অবান্তর এক আলাপ। এর ছাপ তাই স্বভাবতই জীবন-যাপন ছাপিয়ে প্রভাব রাখছে আমাদের মনস্তত্ত্বে, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সাহিত্য, বিনোদোন সর্বত্র।
বিজ্ঞানের আশীর্বাদ গতিকে ঘিরে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রভাব দৈনন্দিন জীবনে পড়েছে অনস্বীকার্য মাত্রায়। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে আমাদের পাঠাভ্যাসেও। সভ্যতার বিবর্তন কাগজে ছাপানো বইয়ের জায়গায় একসময়ে এনে দিলো ই-বুক। আমরা ভাবতে শুরু করলাম কাগজের বইয়ের অস্তিত্ব একদিন নির্ঘাত বিলীন হয়ে যাবে ই-বুকের কাছে। দেখতে না দেখতে ই-বুকের পাশে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো অডিও বুক। দৌড়ে অডিও বুক সহসাই পেছনে ফেলে দিলো ই-বুককে। সম্ভবত অডিও বুকই আধিপত্যে থাকবে অনাগত দিনে। কাগজের বই লোপাট হবে না, তবে অনেক বিখ্যাত বইয়ের দোকান ইতিমধ্যে লোপাট হয়েছে বিশ্বজুড়ে। অনেক পত্র-পত্রিকা প্রিন্ট ভার্শন গুটিয়ে ফেলেছে, কোনো কোনোটা বন্ধই হয়ে গেছে।
মানুষের এইসব মনস্তাত্ত্বিক বীক্ষণ আর দৈনন্দনিকতাকে নিয়েই তো সাহিত্য। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ গতিকে ঘিরে প্রভাবিত আবেগ-সৃষ্ট সাহিত্যেও তাই এসবের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। হ্যাঁ, মানুষের ক্ষুধা, যৌনতা, জন্ম, মৃত্যু খুব না পাল্টালেও প্রেম, ভালোবাসা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পাল্টেছে বিবিধ মাত্রায়। আবেগ অনুভূতি পাল্টেছে, উবে না গেলেও। দুঃখ, বেদনা, বিরহ, বিষাদ, উৎসব, আনন্দ– এসবও উবে যায়নি, তবে ধরন পাল্টেছে। সব রকমের পরিবর্তন সাহিত্যের প্রকাশ, ভঙ্গি, বিষয়, ধরন-ধারন, আঙ্গিক, দৈর্ঘ্য– এসবের ওপর প্রভাব রেখেছে। মানব জীবন ও সভ্যতার অন্য সব অনুসঙ্গের মতো সাহিত্যও তার বিবর্তনের ধারা নির্ধারণে সর্ব কালেই সক্রিয়। ইলিয়াড, ওডিসি, শাহনামা, মনাস, মহাভারতের দৈর্ঘ্য সাহিত্যে সংকুচিত হয়েছে যুগ পরম্পরায়। মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা দীর্ঘ পাঠের অভ্যাস থেকে মানুষকে সরিয়ে এনেছে। এখন যুগ এসেছে ফ্ল্যাশ ফিকশনের, মাইক্রো ফিকশনের। অণুগল্প, ক্ষুদে কবিতা এসবই এখন ক্রমশ অধিকতর পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠছে।
সোশাল মিডিয়ার উদ্ভবে– ব্লগিং থেকে ফেসবুক, টুইটার হয়ে সুবিশাল পাঠক আগেকার দিনের সরলরৈখিক লেখক-পাঠক সংযোগ থেকে একই সময়ে একইসঙ্গে বহু লেখক ও বহু পাঠকের বহুমাত্রিক মিথস্ক্রিয়ার অভাবনীয় ও সীমাহীন বিস্তৃতির এক সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এতে একটা লেখা কয়েকশো বা হাজার কপি বই এবং প্রায় সমানুপাতিক পাঠকের সীমিত গণ্ডি থেকে হাজার হাজার পাঠকের সমুদ্রে এসে পড়ছে। বই প্রকাশের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যাবার প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে একজন চাইলেই তার মনের ভাব প্রকাশে, যে কোনো লেখা সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করতে পারছে, যখন-তখন, যে কোনো আঙ্গিকে। ফলতঃ ধরা যাক একটা কবিতা বা গল্প আগে যখন প্রকাশ পেতো প্রিন্ট মিডিয়ায়, তখন পাঠক সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল, ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা ডিঙিয়ে দূরবর্তী পাঠকের কাছে পৌঁছানোটাও দুঃসাধ্য ছিল। এখন পৃথিবীর যে প্রান্ত বসেই কেউ লিখুক না কেন, সোশাল মিডিয়ার কল্যাণে গোটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে অন্য যে কেউই তার পাঠক হতে পারছে। চাওয়া মাত্রই যে কেউ লিখে ফেলতেও পারছে। এতে পাঠকের পরিধি যেমন লাগাম ছাড়িয়ে বেড়েছে, তেমনি লিখিয়ের সংখ্যাও বেড়েছে লাগামহীন ভাবে। ফলত কোয়ান্টিটি যতটা স্বাধীন ও উদ্দাম হয়েছে, কোয়ালিটি ততটাই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এর সূত্র ধরে অনেক বইও প্রকাশিত হচ্ছে, যা আগে প্রকাশক টাকা লগ্নি করে বই আকারে ছাপতো না। যে কোনো লেখাই বই আকারে বেরুতো না। তাই যথাযথ মান না থাকলে একটা লেখা বই আকারে প্রকাশ না পাওয়ায় একজন পাঠক ক্রেতা হিসেবে ঠকে না যাওয়ার পাশাপাশি মানসম্মত লেখা বাদ দিয়ে অন্য লেখা পড়ে কোনো পাঠকের সময় নষ্ট হওয়ার কোনো ঝুঁকিও সেরকম ছিল না। বিপরীতে বই আকারে বা পত্র-পত্রিকায় ছাপা না হয়ে অধরা থেকে যাওয়া নিশ্চিত মেধাবী অনেক লিখিয়ের লেখাও আজ অনায়াসে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, প্রতিভা অপ্রস্ফুটিত থেকে যাওয়ার দিন তাই আজ আর নেই।
অবশ্য লেখার মান এবং ভালো লেখক ও পাঠককে বহু বহু লেখার মধ্য থেকে ভালো লেখাটি বেছে নেয়ার জটিল ও প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ পরিস্থিতি হেতু সকল সুবিধা-অসুবিধার বাইরে সোশাল মিডিয়া এবং বিস্তৃত ও অবাধ যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে একজন পাঠক আজ বৈশ্বিক সাহিত্যের সকল তথ্য খুব সহজে হাতের নাগালে পাচ্ছে। আগে এত সহজে বিশ্বের যে কোনো দেশের, যে কোনো ভাষার একজন লেখকের কথা জানা সবার জন্য এতটা সহজ ছিল না, বইপত্র পাওয়া তো দূর। সেই জায়গায় আজ যে কেউ উৎসাহী হলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একজন লেখকের সন্ধান যেমন পেতে পারে সহজে, চাইলে তার বই বা কোথাও প্রকাশিত কোনো লেখাও হাতের নাগালে পেয়ে যেতে পারছে অনায়াসে। ফলে পাঠক ও লেখক উভয়ের বৈশ্বিকীকরণ ঘটে যেতে পারার সহজ সুযোগ আজ আমাদের সবার হাতের মুঠোয়।
অনলাইন বিক্রয় পদ্ধতি কিংবা এমাজনের মতো প্রকাশনা ও বিপনন প্ল্যাটফর্ম বইয়ের বিক্রয় বাড়াতে ভূমিকা রাখছে, ভৌগলিক গণ্ডি টপকে যাওয়াটাকে চাইলেই সম্ভব করে তুলেছে। পাশাপাশি একটা কবিতা শুধু শব্দের নির্মাণ না, হয়ে উঠেছে নান্দনিক প্রকাশের চাহিদাপূর্ণও। লেখকদের মিথস্ক্রিয়া এবং লেখক-পাঠকদের মিথস্ক্রিয়াও ঘটছে অনায়াসে ও অবারিত মাত্রায়। এর ফলশ্রুতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে যাচাই করার বা সফল প্রমাণ করার একটা ভ্রান্ত প্রতিযোগিতা একজন লিখিয়েকে ভুল পথে যেমন পরিচালিত করছে, তেমনি প্রকৃত পাঠক ছাড়াই জনসংযোগ ও বিপণন কৌশলগত কারণে কখনো কখনো প্রতিক্রিয়ার আধিক্য লেখককে এবং সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করছে। আবার এই বৈরীতার সমান্তরালে সৃষ্টিশীলতা নতুন মাত্রা পাচ্ছে একটা লেখার অডিও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার সুবাদে।
শীঘ্রই একদিন এই অডিও বা অডিও ভিজ্যুয়াল প্রকাশ মাধ্যমটিই সম্ভবত হয়ে উঠতে যাচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। যদিও একটা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম এই উপস্থাপনা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে হয়তো তার জন্য সম্যক পাঠকের (শ্রোতা বা দর্শকও বলা যায় প্রসঙ্গ বিবেচনায়) কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হওয়ার দৌড়ে অনায্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, কিংবা পৌঁছাবেই না। তাথাপি জীবনযাপনের নৈমিত্তিক ব্যস্ততা মানুষকে এমন একটা দিনের দিকেই ধাবিত করছে প্রতিনিয়ত। কেননা, দূর ভবিষ্যতে হয়তো সাহিত্যপাঠ হবে মূলত শ্রবণ পদ্ধতির ওপর ভর করেই। ইউটিউবে গান শোনার মতো নাগত কোনো দিনে মানুষ হয়তো সকালে অফিসে যেতে কিংবা সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার পথে হাতের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে রেডিও ওয়েভলেংথে আজকে তার পছন্দের গানটির মতো খুঁজতে থাকবে পছন্দের কবিতা, গল্প, উপন্যাসের অংশ কিংবা হয়তো খুঁজে বের করবে প্রিয় লেখকের নতুন কোনো লেখা, আর তা শুনতে শুনতে মেটাবে তার পাঠের তেষ্টা।
প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি একজন লেখককেই হতে হবে সেই কারগরি কৌশলজ্ঞান সম্পন্ন? না, প্রকাশকের ভূমিকায় তখন হয়তো পূর্ণ দমে ক্রিয়াশীল থাকবে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও পাবলিশার শিরোনামে একটা বিশাল গোষ্ঠী। প্রযুক্তির আবির্ভাবে প্রথম প্রথম অপব্যবহার থাকতেই পারে। এই টিকটক আর রিলের উৎপাতের ভিতর থেকেই কিন্তু জেগে উঠছে গল্প-কবিতার অডিওভিজ্যুয়ালের নানা রকম প্রকাশ। আমাদের অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত ধারার সেই দিনটি হয়তো আমাদের মাঝে পথ চলতে শুরু করেই দিয়েছে।
লুৎফুল হোসেন
২৩ জুলাই ২০২৫
*****************
![]()