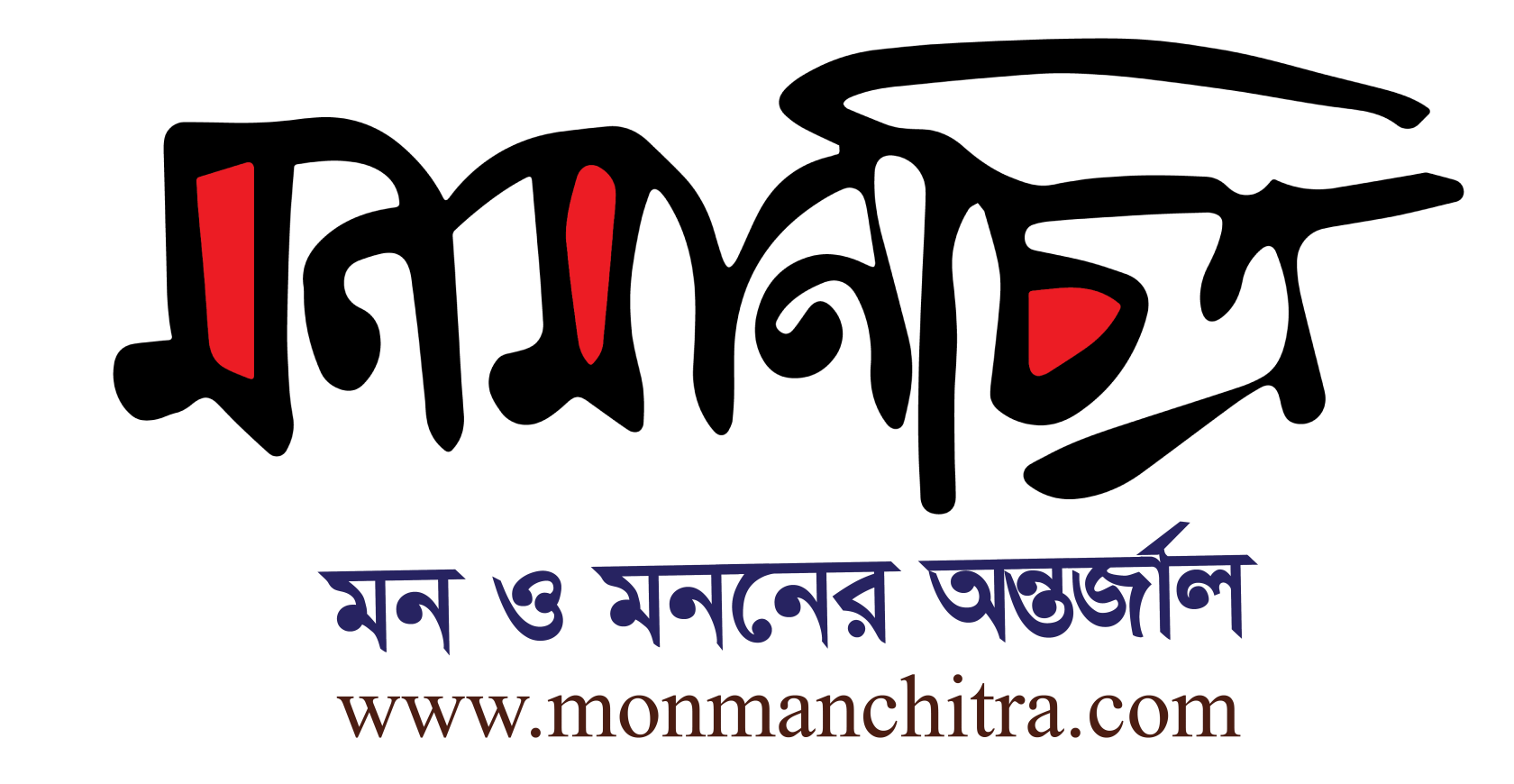মহীবুল আজিজ
হন্তারকের খোঁজে
আমি খুনি মাইনুদ্দিনের খোঁজ করতে থাকি। চ্যানেল ফোরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ডকুমেন্টারিটা দেখবার পর থেকেই আমার মনে হতে থাকে, মাইনুদ্দিনকে কোথাও দেখেছি। বিশেষ করে, চৌদ্দই ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকা- ঘুরপাক খায় করোটির মধ্যে। শহীদ মুনীর চৌধুরীর ছেলে মিশুক মুনীরের চাচাত ভাই আমার বন্ধু। ওর কাছ থেকে জেনেছিলাম, সকালটা ছিল রৌদ্রময়। ফুলার রোডের ওদের আঙিনাতে শিশুকিশোরেরা খেলছিল যদিও চারদিকে ভাসছিল আতঙ্ক। হঠাৎ একটা জিপগাড়ি এসে হাজির হলো সেই আঙিনায়। ওরা দেখলো, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশীদুল হাসান, ফয়জুল মহী, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সবাইকে ধরে নিয়ে গেলো লোকগুলো। যারা ধরে নিয়ে যায় তারাই হত্যাকারী। ওদের একজনকে মিশুক কোনভাবেই ভুলতে পারে না। ফর্সামত দাঁড়িঅলা গোলগালমুখো লোকটার চেহারাটাই কী আমি দেখতে পেলাম চ্যানেল ফোরে কাল রাতে! তাহলে কোথায় দেখেছি তাকে। নাকি দেখেছিল মিশুক মুনীর। তার সেই দেখাটা আমার বন্ধু তার চাচাত ভাই সুমনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা আমার মনের মধ্যে জলভ্রমির সৃষ্টি করেছে। ক্লোজ শটে লোকটাকে যে-ক’বারই দেখায় আমার মনে হতে থাকে যে সে আমার চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই কেম্ব্রিজ শহরে, দেশ থেকে এতটা দূরত্বে এসে একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীর সূত্রিতা আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে সেটিকে ঝেড়ে ফেলা কোনভাবেই সম্ভব হয় না আমার পক্ষে।
আমার মনে হতে থাকে সুদূরের এই জনারণ্যেই কোথাও তাকে দেখেছি। গত ক্রিসমাসের সেইল-এর ভিড়ে মার্ক্স এ্যান্ড স্পেন্সার কি দেবেনহ্যাম্স্ কিংবা বুট্স্ কি রবার্ট স্যাইলের ভিড়ের কথা স্মরণ করতে থাকি। আলিঝালি একটি দু’টি মুখ ঘুরে-ঘুরে আসেও। কিন্তু সেই মুখকে মাইনুদ্দিনের মুখ বলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কেন মনে হবে, টিভির পর্দায় সহসা ভেসে ওঠা বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী বলে কথিত লোকটা আমার চেনা। অথচ যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করলে সেই লোককে দেখতে পাওয়াটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরেও আমার মনে হতে থাকে, হোক এই কেম্ব্রিজ শহর এতটা দূরের সীমানা তবু এখানেই আমি দেখেছি লোকটাকে। সেই লোকটাকেই যে একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের অন্যতম পান্ডা। হয়তো সিটি সেন্টারের মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে কোন দোকানির কাছ থেকে ব্রোকলি কি ক্যাপসিক্যাম কিনছিল। হতে পারে সে ছিল আমারই নিঃশ্বাসের দূরত্বে। কিন্তু দেখে তো আমার বোঝা অসম্ভব, একজন ভয়ংকর খুনি আমারই পাশে দাঁড়ানো ক্রেতার ভূমিকায়। আর খুনির অবয়বটা আগে থেকেও যদি মনে গাঁথা হয়ে থাকে তাতেও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, সে-ই খুনি। যদি বাস্তবে সেটাই সত্য হয় তবে নিজের হাতে খুন করা লোকেদের তো থাকবার কথা কঠিন অন্ধকারের কুঠুরিতে। সভ্যতা সমাজ রাষ্ট্রের তো তাদের একই মর্যাদায় নিরপরাধ মানুষদের পাশাপাশি থাকতে দেওয়া অনুচিত। তারা সেটি করবে না আর আমি তাকে খুনি বলে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকবো সেটা তো কাজের কথা নয়। আমার মনে হতে থাকে এক বিকেলে লায়ন ইয়ার্ডের চত্বরে আমি যখন বুনুয়েল রেট্রোসপেক্টিভ দেখবো বলে টিকিট হাতে দাঁড়িয়েছি তখন সে ‘হালাল বুর্চাস্ শপ’ থেকে মাংস কিনছিল গরুর কিংবা মুরগির।
আমি আসলে খুনি মাইনুদ্দিনেরই খোঁজ করি। শেষ পর্যন্ত আমার বদ্ধমূল ধারণাটাকে আমি যাচাই করতে শুরু করি। কেন এক অদেখা লোক সারাক্ষণ আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, আমাকে বিরক্তিকর অস্বস্তির মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। দেশ থেকে আসা বন্ধু সুমনের চিঠি আমাকে নিশ্চিত করে, খুনি মাইনুদ্দিনই এবং সে পলাতক। কিন্তু পলাতক মাইনুদ্দিন পৃথিবীর এক অতি সভ্য দেশের এক শ্রেষ্ঠ শহর কেম্ব্রিজে ইমামতি করে একটি মসজিদে। সেখানে সে মুক্ত মানুষ, কেউ তার হাতে খুঁজে পায় না রক্তের দাগ। স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। আমার আর হিসেব মিলতে চায় না। এ কেমন সভ্যতা। একটা ভয়ংকর লোক একটা দেশ ও জাতির স্বর্ণসন্তানদের হত্যা করলো। পরাজয় নিশ্চিত জেনে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিরপরাধীন একটি জাতির স্বাধীনতার আসন্নতার মুখে দেশটিকে পঙ্গু করে দেওয়ার মারাত্মক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সে-জাতির মনন-মানবদের হত্যা করলো বেছে-বেছে। অথচ ইংল্যান্ড আশ্রয় দিয়েছে তাকে। কেবল আশ্রয় নয়, বলতে গেলে কোলেপিঠে পরিপোষণ করবার দায়িত্বও নিয়ে নিয়েছে কাঁধে। যে-লোকের শাস্তি ছিল অবধারিত মৃত্যুদ- বছরের পর বছর সে মুক্ত বায়ুতে কেবল নিঃশ্বাসই নিয়ে গেল না, তার বংশবিস্তারের পরম্পরায় বীজ থেকে অংকুর এবং অংকুর থেকে বৃক্ষ আর বৃক্ষ থেকে বৃক্ষরাজি হয়ে এক বিপুল ঘৃণার পৃথিবী সে সৃষ্টি করে ফেলেছে যে-পৃথিবীর নাগরিকেদের সকলের জীবনের উপাদান ঘৃণা ও প্রতিহিংসা। মাইনুদ্দিন সেই পৃথিবীর অধীশ্বর। আমি নিশ্চিত, একদিন কেম্ব্রিজ শহরের কোথাও না কোথাও তাকে খুঁজে পাবো আমি। মসজিদে সে ইমামতি করলেও নিশ্চয়ই তাকে খাওয়াপরা করতে হয়, বাজারসদাই করতে হয়, দাঁড়াতে হয় দোকানের কিউতে। এবং সুমনের চিঠি পৌঁছাবার পর থেকে আমার পূর্বধারণাটা আরও মজবুত হয়। নিশ্চয়ই এই কেম্ব্রিজেরই কোথাও তাকে আমি দেখে থাকবো। নইলে চ্যানেল ফোর-এ যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে টিভি-পর্দায় ভেসে ওঠা তার মুখটা কেন আমার পরিচিত মনে হবে। আমি ঠান্ডা মাথায় উত্তেজনা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি। পৃথিবীর সভ্য দেশেরাই খুনিদেরও আশ্রয়দাতা। দ্বিতীয় বিশ^সমরে পরাজিত হত্যাকারীরা আশ্রয় নেয় সভ্য বলে কথিত দেশগুলোতেই। তাদের কাঁধে পরোয়ানা অথচ তারা ঘুরে বেড়ায় আর্জেন্টিনায় অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রান্সে গ্রেট বৃটেনে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হ্যাঁ, ছদ্মবেশে থাকা তাদের অনেকেই ধরা পড়ে। শোনা যায়, তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বদৌলতে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে মুখের আদলও পাল্টে ফেলতে পেরেছে। বাইরের তাদের নবার্জিত মুখম-লের ভেতরে নিহিত প্রকৃত হত্যাকারীর মুখ।
সেদিনটায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেনেট হাউজের সামনেকার চাতালটাতে। একদিকে গ্রনভিল-কীজ কলেজের ভবন, উল্টোদিকে মিডল্যান্ড ব্যাংক। কোণের দিকটাতে উলওয়ার্থ এবং সেইন্সবারি কাছাকাছি। মার্কেট স্কয়্যারের গোটা এলাকাটা চোখে পড়বে স্পষ্ট। পরিচিত মহিলাটা ডোনাট ভাজছিল একমনে। ওর লাগোয়া ক্যারাভানের জানলা দিয়ে দেখা যাবে বুড়ো মাইকেলকেÑ বিভিন্ন ঘরানার হটডগের পসরা সাজিয়ে বসেছে। বিখ্যাত ভিয়েতনামি রোলের ছোটখাট লোকটাও রয়েছে। সেনেট হাউজের গা ঘেঁষে বসে একটি রুমানিয় জিপসি মেয়ে -বেহালা বাজায় ধীর লয়ে। ওর পোষা কুকুরটা মেয়েটির হাঁটুর কাছে মুখ গুঁজে ঘুমায়। এগিয়ে যেতেই যাকে মোটেও পছন্দ নয় সেই মার্গারেটের মুখোমুখি। কাঁধে চামড়ার খোপে রাখা বেহালা। কেম্ব্রিজের আর্টস্ থিয়েটারে বাজায় সুযোগ পেলে। ওর সঙ্গে একবার ঝগড়া হয়েছিল। বিষয় ছিল হলোকস্ট। ওর ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ষাট লক্ষ মৃত্যুর সংখ্যাটা অতিরঞ্জন – সেটা নাকি মিত্রপক্ষের প্রচারণা। আমি জানি ওর জার্মান রক্তের মধ্যে বয়ে চলেছে নাজি পূর্বসুরীদের উপাদান। ওকে দেখে মনে হলো সে আসলে আমাদের সেইসব স্বদেশবাসীর সমগোত্রীয় যারা মনে করে খুনি মাইনুদ্দিন পবিত্র পুরুষ। মার্গারেট আমাকে সম্ভাষণ জানায় পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে। চার্চে দুপুর বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ভাবছিলাম ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকবো চিকেন বার্গার খাওয়ার জন্যে। কানে আসে ‘ওয়ান পাউন্ড’ ‘ওয়ান পাউন্ড’ বলে হাঁকতে থাকা মাঝবয়েসী ফুলঅলার কণ্ঠ। লাল হলুদ কমলা নানান রঙের টিউলিপের স্টিক ওর সামনে। একটা স্টিকে তিনটে করে টিউলিপ। হয়তো আজ ভোরেই সেগুলো এসেছে নেদারল্যান্ড থেকে। সহসা সবুজ রঙের পাবলিক বাসটা এসে দাঁড়ায় সামনে। নামতে থাকে লোকেরা। নিরুৎসাহী দৃষ্টি দিয়ে দেখি ওঠানামার যাত্রীদের। আচমকা আমার চোখ গেঁথে যায় বাস থেকে নামা এক যাত্রীর দিকে। একী, এই তো সেই লোকটা। এই তো সেই লোক যাকে ক’দিন আগে দেখেছিলাম চ্যানেল ফোরে। সেই লোক যে কিনা হত্যা করেছিল আমাদের স্বর্ণসন্তানদের। আমার চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে খুনি মাইনুদ্দিন। সোৎসাহে দৃষ্টি দিয়ে খনন করতে থাকি লোকটাকে।
মাঝবয়েসী কাঁচাপাকা চুলদাড়িঅলা মাইনুদ্দিন তখন ঢুকে পড়েছে উলওয়ার্থে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঢুকে পড়ি আমিও। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাকে অনুসরণ করি তা নয়, আমি চাই লোকটাকে যতটা সময় সম্ভব দৃষ্টির সীমানায় ধরে রাখা। দেখি সে কী করে, কোথায় যায়। ব্যস্ত লোকজন কেনাকাটা করে এদিকে ওদিকে চলে যায়। কেউ হয়তো বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকে বিশেষ ছাড় দেওয়া সামগ্রীর সামনে। চকলেট কেনে বাক্সভর্তি কি একটি কিনলে একটি ফ্রি’র জিনিস তুলে নেয় ট্রলিতে। একটা ট্রলি নিয়ে কেনাকাটা করে মাইনুদ্দিন। আলগোছে তাকে পরখ করে যাই। গোলগাল মুখ এবং মুখভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা দাঁড়িতে পেটানো শরীরের লোকটাকে দেখে মনে হয় যৌবনে সে বেশ দশাসই ধরনেরই ছিল। চকিতে আমার মনে পড়ে যায় শিল্পী আবুল বারক আলভীকে। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঢাকা চারুকলা ইন্সটিটিউটে। জেনেছিলাম তাঁকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল রাজাকার-আলবদর এবং হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা। যে ঘরটাতে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয় ঠিক সেই ঘরে পাশের কামরাটাতে নির্যাতন চালানো হয় অমর সুরকার শহিদ আলতাফ মাহমুদকে। কড়িকাঠের দড়িতে ঝুলছেন আলতাফ মাহমুদ। তাঁর দুই পা দড়িবাঁধা এবং তাঁর মুখ মেঝে ছুঁইছুঁই। শিল্পী আলভীকে নির্যাতনের জন্যে কামরায় ঢোকানোর মুহূর্তে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তিনি দেখতে পান কামরাবন্দি আলতাফ মাহমুদকে। আমার কানে ভাসে ছোটখাট শরীরের ফর্সামুখ আলভীর কথাগুলো, আলতাফ মাহমুদকে ওরা মেরেই ফেললো। কিন্তু একটা শব্দও পারলো না মুখ দিয়ে বের করতে। এই হলো আসল মুক্তিযোদ্ধা। ঠিক যেমন ফরাসি লেখক জ্যঁ পল সার্ত্র্-এর ‘সমাধিবিহীন মৃত্যু’ নাটকের দৃশ্যায়ন। হিটলারের দোসর ফরাসি রাজাকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পেত্যাঁ-র বাহিনী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নির্যাতন চালায় ফ্রান্সের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। কিল-ঘুঁষি জাতীয় সাধারণ অত্যাচার থেকে শুরু করে আঙুলে সুঁই ঢুকিয়ে দেওয়া এরকম সব নির্মমতা চলতেই থাকে কিন্তু একটি শব্দও বের করানো যায় না। একটু পরেই উলওয়ার্থ ডিপার্টমেন্টস্ স্টোর থেকে বেরিয়ে পড়ে মাইনুদ্দিন। বেরিয়েই মার্কেট স্কয়্যারের খোলা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে হাতে থাকা দু’তিনটে ব্যাগ সামলে নিয়ে, হয়তোবা হাঁটবার কথাই ভাবছিল। জানি না সে কোন্ দিকে যাবে, বাসে না পদব্রজে, সে সময় নেয় খানিকটা। আমার তখন সুমনের কথা মনে পড়ে। শহরের একটা মসজিদের সে ইমাম। ওর ব্যাগধরা হাত দু’টো লক্ষ করি। কব্জি এবং চেটো’র পরিমাপ থেকে তার শক্তি আন্দাজ করা যায়। এই দু’টো হাতের প্রাবল্য দিয়েই সে একাত্তরের ডিসেম্বরে নিরাপত্তার আশ্রয় বলে কথিত বেসামরিক নাগরিকের ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল ‘রাইফেল রোটি আওরাত’-এর লেখক আনোয়ার পাশাকে। তুলে নিয়েছিল জাতির বেদনানীল সঙ্গীতের সুর¯্রষ্টা আলতাফ মাহমুদকে। শিশুর মত সরল গোবিন্দচন্দ্র দেবকে। আরও আরও কত নিরীহ মানুষকে। কেবল তুলে আনাই নয় বেয়নেট আর গুলিতে বিদ্ধ করে হত্যা করে তাদের। কিন্তু এখন মধ্যবর্ষের প্রখর দুপুরে মাইনুদ্দিনের হাতে কী আর রক্তের দাগ লেগে থাকে! ব্যাঙ্কো-হত্যার অনেকটা কাল পরেও লেডি ম্যাকবেথ তাঁর হাতে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছিলেন। আরবের দামি সুগন্ধিতেও সেই দাগ সেই গন্ধ মুছে যায় না। আমার দেশের মানুষদের মধ্যেও অনেকের নিকটে মাইনুদ্দিনের হাত পরম পবিত্র কিন্তু আমি ঠিকই রক্ত দেখি মাইনুদ্দিনের দুই হাতে। লেগে রয়েছে এবং সেই লালচে আভায় দুপুরের রোদে অস্বাভাবিকভাবে তার দুই হাত আমার চোখের সামনে দুলতে থাকে আতঙ্কের মতন। সে যখন উলওয়ার্থের ট্রলিটা দোকানের গা ঘেঁষে রেখে ব্যাগগুলো গোছাতে থাকে তখন তার সেই শক্তিশালী দু’টি হাতের কব্জি থেকে চেটো চুঁইয়ে পড়তে থাকে রক্ত – টপ্ টপ্ করে – আলতাফ মাহমুদ রাশীদুল হাসান মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী গোলাম মোর্তজা গিয়াসুদ্দিন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এরকম কত কত নাম জানা-অজানা সব লোকেদের। সব রক্ত একসঙ্গে মিশে এক অনিঃশেষ রক্তপ্রবাহ হয়ে বইতে শুরু করে এবং আশ্চর্য, গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখি সেই রক্তের গঙ্গোত্রী ঢাকা নামের এক জনপদ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আরও দূর কেম্ব্রিজশায়ারের কেম্ব্রিজ নামক আরেক জনপদেও পৌঁছে গেছে সেই রক্তের ধারা। মাইনুদ্দিনের হাতে ধরা উলওয়ার্থের গাঢ় লাল রঙের ব্যাগের মধ্যে কী রয়েছে কে জানে আমি দেখি তার হাতের রক্তপ্রবাহে সেই ব্যাগগুলি একেকটি রক্তের দলায় পরিণত হয়েছে।
চিৎকার আচমকা আটকে পড়ে আমার গলার কাছে এসে। মাইনুদ্দিন কী সেটি বুঝতে পারে! হয়তো আমার বাদামি প্রকরণের বাস্তবতায় সে কেবল মুহূর্তকালের জন্যেই আমাকে লক্ষ করতে চায় কিন্তু আমি ধরা দেই না। তাকে না দেখার ভাণ করে আমি উল্টো দিকের রাউন্ড চার্চের গোল গম্বুজটা পরখ করতে থাকি। তখনই আমার কাছ ঘেঁষে চলে যেতে যেতে আমাকে সম্ভাষণ জানায় কামিলাÑ কামিলা লুন্ড। সুইডেনের মেয়ে কামিলা আমার হাউজমেট। হাউজে তুমুল জনপ্রিয় কামিলা প্রথমত তার অসাধারণ সৌন্দর্যের কারণে এবং দ্বিতীয়ত তার মিশুক ধরনের স্বভাবের কারণে। খুব ভোরে হাঁটা শেষে সে যখন খোলা মাঠের কোণের দিকটাতে দাঁড়িয়ে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত হয় তখন ঠিকই আমাদের ঘরের নানান জানলা থেকে চিন ফ্রান্স নরওয়ে জাপান স্পেন ভারতবর্ষ এইসব নানান দেশের গৃহবাসীরা মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে কামিলাকে। এমন যে ধার্মিক অন্ধ্রের শ্রীধর ইধাপালাপ্পা, সেও ভোরের সূর্যকে জোড়হাতে প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে মুদ্ধতার দৃষ্টি মেলে দেয় আঁটসাট গেঞ্জিপরা কামিলার দিকে। সেই কামিলা আমাকে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে বলা যায় আমাকে উদ্ধার করে চলে যায় মাইনুদ্দিনের মনোযোগ থেকে। সে তখন হাঁটা শুরু করেছে। কোন্ দিকে যাবে সে! এখান থেকে গার্টন রোডের দিকে গেলে গার্টন কলেজ পেরিয়ে ওকিংটন। যাওয়া যায় ম্যাডিংলে হয়ে ক্যামবুর্ন। ডান দিকে গেলে লিটল উইলবারহ্যাম। আরও রয়েছে লিন্টন ডাক্সফোর্ড সোয়াস্টন বারি সেন্ট এডমন্ড। এগুলোর কোন্ পথে সে হাঁটবে। মাইনুদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের রাস্তা ধরে এগোয়। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে থাকি আমিও। একজন মারাত্মক খুনি লোক নিরীহ নাগরিকের ধরনে পথ হেঁটে যায়। আমি ছাড়া কেউ জানে না তার হত্যা আর রক্তের বৃত্তান্ত। সে কী তাহলে কেম্ব্রিজের বিখ্যাত আবুবকর মসজিদের দিকেই যাবে। এটাই কেম্ব্রিজের মূল মসজিদ। হয়তো সেই মসজিদেরই সে ইমাম।
সদর রাস্তার লাগোয়া ফিৎজউইলিয়ম মিউজিয়ম ডানে রেখে সে ঢুকে পড়ে ফিৎজউইলিয়ম স্ট্রিটে। মিউজিয়মের বিশাল প্রাসাদের ছায়া পড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। এখানেই আমি দেখেছি ক্লদ মোনে সেজান পিকাসো ব্রুগেল শুরাট বেকন রেমব্রান্ট জন কন্সটেবল দালি এরকম সব বিখ্যাত শিল্পীর মূল শিল্পকর্ম। ব্যাগগুলো সমতার ভিত্তিতে দুই হাতে ধরে রাখবার কারণে মাইনুদ্দিনের দেহ থাকে ঋজু ও লক্ষ্যাভিমুখ যদিও ডান দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটাই তার বিশেষত্ব। পরনে থাকা ফতুয়া এবং পাঞ্জাবির মিশ্রণে গড়া হলুদাভ পোশাকে তার ফর্সা চেহারাটা দুপুরের রোদে আরও উজ্জ্বল দেখায়। সে যখন বাইশ নম্বর পেরিয়ে যায় আমি তখন ধীরে পেরোই নয় নম্বর, অর্থাৎ আমি থাকি রাস্তার উল্টো দিকে। বাইশ নম্বর ফিৎজউইলিয়ম ঠিকানাটা এমনিতেই পৃথিবীবিখ্যাত। চার্লস ডারউইন তাঁর বিগল-অভিযাত্রার শেষে ১৮৩৬-৩৭ সালে এসে বসবাস করেন বাইশ ফিৎজউইলয়মেই। আর মিউজিয়মটাও ঠিক ঘাড়ের ওপরেই বলা যায়। সেখানে ডারউইনেরই সংগ্রহ করা বেশকিছু নিদর্শন আমি দেখেছিলাম। কী আশ্চর্য সমাপতন। পঁচিশ নম্বরে থাকেন পিএইচডি করতে আসা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ফরিদ আহসান। বাড়িটা পেরিয়ে যেতে যেতে সেই কথা ভাবি একটুক্ষণ। মাইনুদ্দিন ততক্ষণে টিরেস-বাড়িগুলো পেরিয়ে পিটারহাউজমুখী রাস্তাটায় পা রেখেছে। বিখ্যাত এলিজি-রচয়িতা টমাস গ্রে’র পিটার হাউজ। আমার পূর্বধারণা এরিমধ্যে বদ্ধমূল হয় মাইনুদ্দিন আবু বকর মসজিদের দিকেই যাবে। কেম্ব্রিজে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের মুসলমান বাংলাদেশি এবং কেম্ব্রিজে উচ্চশিক্ষা করতে আসা লোকেরা নামাজ পড়তে আসে মসজিদটাতে। শুক্রবারে ভিড় বাড়ে। কালো ও ধূসর পাথরবসানো মসজিদটাকে দূর থেকে বেশ ঐতিহাসিক-ঐতিহাসিক দেখায়।
মাইনুদ্দিন মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ালে আগে থেকে অপেক্ষমান আরেক লোক এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। হতে পারে লোকটা মোয়াজ্জিন। কিন্তু দেখে বাঙালি মনে হয় না। লম্বা সফেদ আলখেল্লা আর লম্বাটে টুপি দেখে তাকে সুদান বা নাইজেরিয়ার লোক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যোহরের নামাজের সময় আসন্ন। অল্পক্ষণের মধ্যে এদিক ওদিক থেকে আরও দশবারোজন লোক এসে আবুবকর মসজিদে ঢোকে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। যেখানটায় আমি দাঁড়াই সেটা একটা ছোট্ট দোকান। মালিকটা সম্ভবত গুজরাটি। পেপার ম্যাগাজিন চকোলেট আর নিত্যব্যবহার্য নানান সামগ্রী এপাশ থেকে আয়না দিয়ে মোটামুটি স্পষ্ট নজরে আসে। মসজিদটা একটেরে। আশেপাশে ঘরবাড়ি কম। বরং মসজিদ ছাড়িয়ে গেলেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর- স্ট্রবেরির। জুন মাসের তপ্ততায় স্ট্রবেরি ক্ষেত লালে লাল হয়ে উঠেছে। স্ট্রবেরি গাছগুলোর চিরল লম্বাটে সবুজ পাতার পটভূমিকায় লাল স্ট্রবেরিগুলো সবুজ-লালের দারুণ এক পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে। জানি না আবুবকর মসজিদের ইমাম মাইনুদ্দিনের চোখে সেই পটভূমিকার সূত্রে উনিশশো একাত্তরকে মনে পড়েছিল কিনা। আমার মনে পড়ে। কেবল মনেই পড়ে না। আমি মাইনুদ্দিনের হাতে লেগে থাকা সেই রক্তের দাগ হয়ে লালে লাল স্ট্রবেরি ক্ষেত ছুঁয়ে চলে যাই রায়েরবাজারের দিকে। স্ট্রবেরি ক্ষেতের মধ্যে পক্কলাল রসালো স্ট্রবেরিগুলো এক সুবিশাল লালের মানচিত্র হয়ে দাঁড়ায় আর আমি দেখতে পাই লালে লাল রায়েরবাজার। সেখানে মানুষেরই শরীর একটা আরেকটার সঙ্গে দলা পাকিয়ে এক বিশাল মানবমন্ডলী হয়ে ছড়ানো। হয়তো আলতাফ মাহমুদের হাত ছুঁয়ে রয়েছে আনোয়ার পাশার হাঁটু আনোয়ার পাশার ঘাড়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে গিয়াসুদ্দিনের একটি পা গিয়াসুদ্দিনের পেটের দিকটায় লেগে রয়েছে গোবিন্দচন্দ্র দেবের কয়েকটি আঙুল।
মসজিদের ভেতরে ততক্ষণে নামাজ শুরু হয়ে গেছে ইমাম মাইনুদ্দিনের ইমামতিতে। বাইরে অপেক্ষা করি। নামাজ শেষে দেখতে হবে মাইনুদ্দিন কোথায় যায়। দেখতে হবে তার বাসাটা কোথায়। ক্ষীণ ইচ্ছে থাকলেও মসজিদের ভেতরে যাওয়ার তাড়না বোধ করি না। জেনেশুনে একজন খুনির পেছনে দাঁড়িয়ে কী করে নামাজ পড়া যায়। আর এখন যদি মসজিদে ঢুকে চিৎকার করে বলি, আপনারা একজন খুনির পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। একজন মারাত্মক খুনি আপনাদের ইমাম, যার হাতে লেগে রয়েছে বহু-বহু মানুষের রক্ত, তাহলে কী লোকেরা বিশ্বাস করবে আমাকে। উল্টো হয়তো আক্রান্ত হবো আমি স্বয়ং। আমি তাই অপেক্ষা করি। দূরে লাল স্ট্রবেরি ক্ষেতের মধ্যে দুলতে থাকে রায়েরবাজার বধ্যভূমি।
**************************