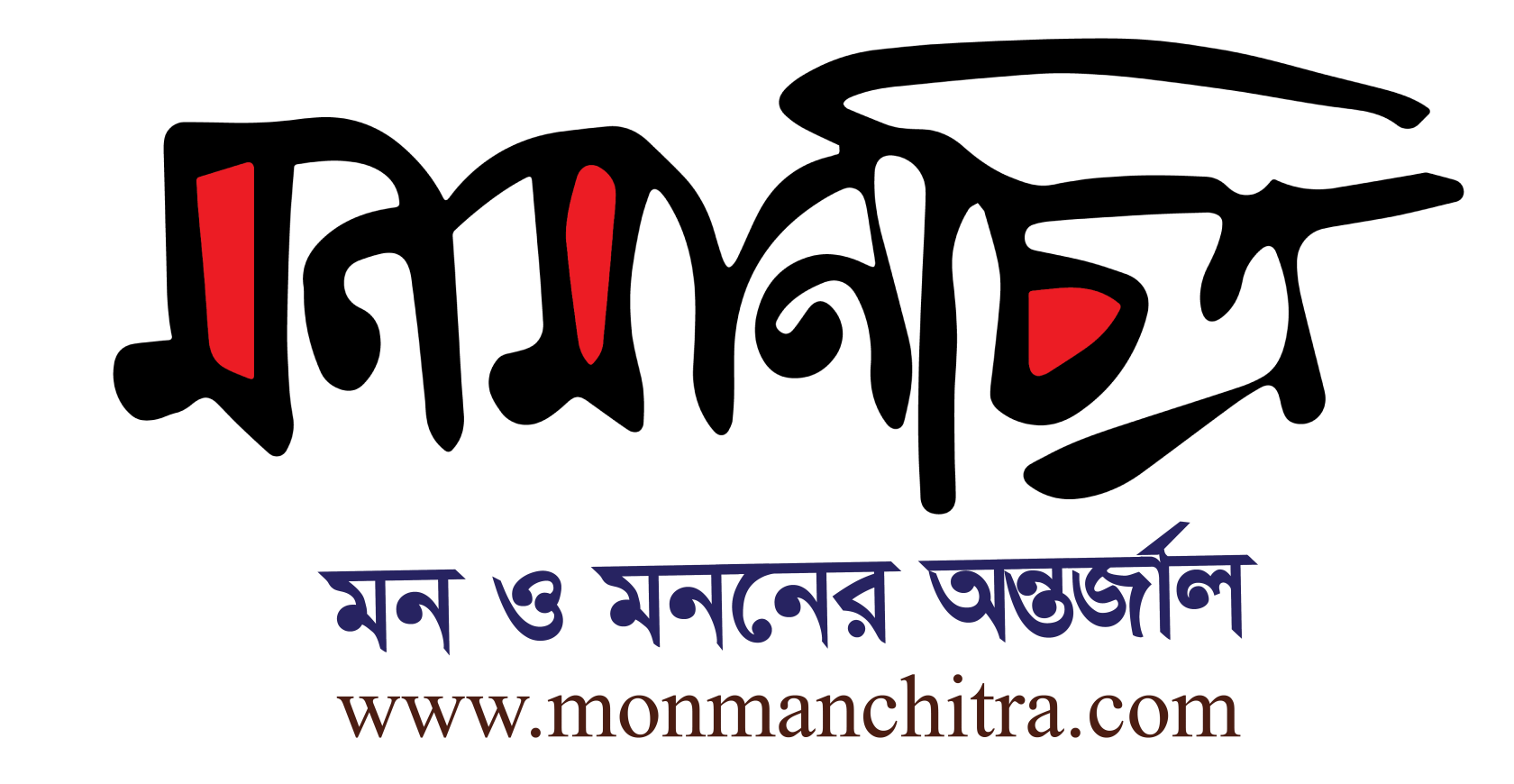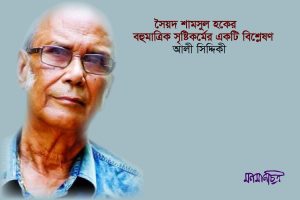মনি হায়দারের উপন্যাস ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’
রুশ্নি আরা
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে অনন্য উপন্যাস মনি হায়দারের ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’। ফাগুনের অগ্নিকণা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী রায় চৌধুরী বা মিনু। কল্যাণী রায় চেীধুরী বা মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনে প্রথম নারী, যিনি ভাষা আন্দোলনে মিছিল করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জে। কল্যাাণী রায় চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যা, চাকরি করতেন স্টেট ব্যাংক অফ ই-িয়ায়। পরবর্তীতে নারায়নগঞ্জের মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হোন তিনি। স্বামী আব্দুল মান্নাফ পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ হতে কলকাতায় যান সিভিল সাপ্লাই অফিসের চাকরির সুবাদে সাথে লেখাপড়া করতে। সেখানেই দুজনের দেখা, পরিচয় ও প্রেম । বিয়ের পর কল্যাণী রায় চেীধুরী নাম পরিবর্তন করে হয়ে যান মমতাজ বেগম । চাকরি নেন নারায়নগনেজর মর্গান স্কুলে। আব্দুল মান্নাফ সরকারী খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা। পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান থাকাকালীন মিনু স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে বিশাল মিছিল করে। মিছিলে প্রায় তিনশজন নারী (ছাত্রী, শিক্ষক, গৃহিণী) অংশগ্রহণ করেন এবং মিছিলের নেতৃত্ব দেন মমতাজ বেগম। এ মিছিল আন্দোলনের সভা পর্যন্ত নিয়ে যান এবং সভায় বক্তৃতা দেন বাংলা ভাষার পক্ষে।পাকিস্তার সরকার তহবিল তছররূপের মিথ্যা কারণে গ্রেফতার করে মমতাজ বেগমকে। কারাভোগ শেষে তিনি ফেরেন শূন্য হাতে। যদিও বাংলা ভাষা মর্যাদা পায় পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা হবার। একরোখা, সাহসী চরিত্রের কারণে নড়ে উঠেছিলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের ভিত। ইস্পাত কঠিন মনোবলের কারণে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিলো সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আলম ও পশ্চিম পাকিস্তানের রক্তখেকো চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ। যাদের সুখের বাগানে বিষকাঁটা হয়ে দেখা দেন মমতাজ বেগম।
উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্রের বিষয়ে ঔপন্যাসিকের উপলব্ধি ও অনুভব নিঃসন্দেহে উচ্চতর। সমকালীন সমাজ ও জীবন প্রেক্ষিতের মুখোমুখী একটি পরিবার কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় কথাশিল্পী মনি হায়দার পারঙ্গমতার সাথে তুলে ধরেছেন ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ উপন্যাসে। মানবসভ্যতায় নারীদের মনোজগৎ গঠনে ঔপন্যাসিকের এই উপন্যাস দারুণ প্রভাব ফেলবে। নারী হিসেবে মহান ও সাহসী হতে শেখাবে ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ উপন্যাসের চরিত্র প্রধান চরিত্র মমতাজ বেগম মিনু।
সমকালীন সকল নেতাকে নিয়ে আসা হয়েছে এ উপন্যাসের পটভূমিকায় নানান প্রয়োজনে। উপন্যাসিক সংযতভাবে চরিত্র অংকন করেছেন। উপন্যাসে রাজনীতিবিদ ও নেতাদের মধ্যে আছেন- খান সাহেব ওসমান আলী, আজগর আলী, জালালউদ্দিন, এ কে এম শামসুজ্জোহা, মোস্তফা সারওয়ার, মুস্তফা মনোয়ার, নুরুল ইসলাম মল্লিক, শফি হোসেন খান, লুৎফর রহমান, জানে আলম, এম এইচ জামিল, বাদশা মিয়া, নাজির হোসেন, সুলতান মোহাম্মদ, মশিয়ার রহমান, নিখিল সাহা, জালাল আহমেদ দুলু, সুবিমল গুহ, আবু বকর, আবদুল মোতালিব, রুহুল আমিন, আফেন্দি হাদিস মোল্লা, মোসলেহ উদ্দীন, অভিনেত্রী রওশন জামিল, নৃত্যশিল্পী গওহর জামিল ও বুলবুল চৌধুরী। আলোচনায় আছেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।
কল্যাণী রায় চেীধুরী মেধাবী, সচেতন, স্বাধীনচেতা মানুষ। চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসিক মনি হায়দার বর্ণনা দেন
ভীষণ মানুষমুখী একজন মানুষ। দিনরাত সাধারণ মানুষের কল্যাণ কিভাবে করা যায়, ভাবে। স্কুলের মেয়েদের কতো ধরণের সমস্যার সমাধান যে করে, শুনলে অবাক হবেন।… গানের গলাটাও ভালো …মিষ্টি গলা। শিক্ষকতা না করে গান গাইলেও অনেক বড় শিল্পী হতো।
উপন্যাসের পটভূমি ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়। আগেরদিন ঢাকায় ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয় রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ আরো অনেকে। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পরে সারাদেশে। নারায়ণগঞ্জও পিছিয়ে থাকে না বরং এগিয়ে আছে ঐতিহাসিক নানান কারণে। ১৯৫২ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ মহকুমা শহরের রহমতুল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের সামনে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিবাদ সভা হয়। এই সভায় মহিলা বা মেয়েরা মোহময় সাহসী রজনীগন্ধা ফোটার দৃশ্যের মতো মিছিল করে আসে। স্লোগান দেয়, “রাষ্ট্রভাষা-রাষ্ট্রভাষা – বাংলা চাই, বাংলা চাই। নূরুল আমীনের কল্লা, কেটে ফেলবো আমরা। রাষ্ট্রভাষা-রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই।” মমতাজ বেগমের ভাষা আন্দোলনে এবং পুরো পাকিস্তানে ‘প্রথম নারী মিছিল’ যা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমগ্র পাকিস্তানে সেদিন প্রথম নারী মিছিল হয়। মমতাজ বেগম ছিলেন একজন অকুতোভয় সাহসী ও সংগ্রামী নারী।
আবুল হাশিম চমকে উঠেছেন মিছিল দেখেই কিন্তু স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক এতোটা অগ্রসর হয়ে আসবেন, তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। মমতাজ বেগম মিনু এগিয়ে যেতেই বয়োবৃদ্ধ আবুল হাশিম দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু এগিয়ে আসেন মমতাজ বেগম। আবুল হাশিমের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়ালে অজস্র মানুষের মধ্যে তিনি জড়িয়ে ধরেন, বিজয়ী হও মা; সামনে তোমার বিপদ, ভয়ানক বিপদ। পাকিস্তানের সরকার তোমাকে ছাড়বে না। এই সমাবেশের মধ্যে সরকারের চর লুকিয়ে আছে। সামনে তোমার বিপদ।
মুখে সাহসের হাসি মমতাজ বেগমের, আমি ভয় পাই না চাচা।
ভয় পেলে কি তুমি এমন কাজ করতে? এমন মিছিল করার সাহস পেতে? আমার মনে হয় সমগ্র পূবর্ পাকিস্তানে, না- আবুল হাশিম তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, সমগ্র পাকিস্তানে আজ প্রথম নারী মিছিল হলো। তুমি সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছ- তোমাকে অনেক অপমান সইতে হবে মেয়ে! পাকিস্তানের সরকার সরকার নয়, আজহাদা মুখ। যা পায় কোনো কেনো যুক্তি ছাড়াই গিলে খায়।
সামনে ভয়ংকর দিন আসবে বা আসতে পারে তা জেনেও মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে তিনি দেশকে সংস্কৃতির আগুনে গড়ে তুলতে চান। তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, ছিলেন সংষ্কৃতির লালনকারী নারী। বাংলাভাষার অধিকার রক্ষায় “মিছিল করেছেন, ভাষার জন্য প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!” পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যে সময় বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল, বঞ্চিত করতে চেয়েছিল সকল সযোগ সুবিধা থেকে, একর পর এক রাজনৈতিক ধ্বস ও বিশ্বাসহীনতার অবাক আক্রমণ চলছিলো সারা বাংলায় সে সময় নারী মিছিল অবিশ্বাস্যই বটে!
জাতি হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে করতে হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার প্রথম ও প্রধান অস্ত্র ভাষা। বাঙালিদের অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস থাকার পরও প্রায় পনেরোশ মাইল দূরের করাচীর শাসকেরা আমাদের ভাষা, আমাদের আশা কেড়ে নিতে চাইছে। কেবল কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, আমাদের ভাইদের হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না। আমরা এই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করি নাই। আমরা চেয়েছিলাম, সবাই পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান মিলে একসঙ্গে থাকতে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে, একটি ভাষায় কথা বলতে। কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী শুরুতেই মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দু জবানে কথা বলতে ও লিখতে বাধ্য করতে চায়, যা এই পূর্ববাংলার বাংলা ভাষার জনগণ হয়ে আমরা মানতে পারি না। কারণ, শত-শত বছর ধরে আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কথা বলছেন বাংলা ভাষায়। আমরা সেই মহান ভাষার বৈধ উত্তরাধিকারী। দুই পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ববাংলার মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদি দুই পাকিস্তানে একটি ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়, যুক্তির কারণে সেই ভাষা হওয়া উচিত বাংলা। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী, যারা আমাদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের ছদ্মবেশে চেপে বসেছে। যদি আমরা ওদের এই কুচক্র মেনে নিই পরের দিন ওরা আমাদের হাত-পা কেড়ে নেবে, আমাদের জিহ্বা কেড়ে নেবে। আমরা কি চুপচাপ বসে থাকবো? নিশ্চ্য়ই না, আমরা প্রতিবাদে প্রতিরোধে ওদের ঘায়েল করবো, যার শুরু হলো নারায়ণগঞ্জ থেকে। (পৃ. ৪৮)
‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ উপন্যাসের পটভূমি যেমন বড় একটি বিষয় চরিত্রও তেমনি। জীবনের ও সময়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমনভাবে উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন যে চরিত্রের আকর্ষণ ও তাৎপর্য কোনোভাবেই খর্ব হয়নি। গল্পের পটভূমি চরিত্রের পরিপন্থী বা চরিত্র পটভূমির পরিপন্থী না হয়ে উপন্যাসের শিল্পগুণ ও মর্যাদা বাড়িয়েছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষায় বাঙালি যে একমত একজোট হতে পেরেছিলো, তার বর্ণনা এবং এর জন্য সারাদেশে যে কতশত বাঙালি ত্যাগ স্বীকার করেছে, লড়াই করেছে, প্রতিবাদ করেছে তারই একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক এ ঘটনা দৃশ্যপট চলমান ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে জীবনরস ও ইতিহাসরস দুটোই সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছে। ঘটনা, পটভূমি ও মূল চরিত্র এক অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।
ঘটনার চড়াই-উত্রাইয়ের পথ ধরে মূল চরিত্র মমতাজ বেগম মিনুর চলাফেরা, কথাবার্তা, জীবনধারার বেশ কিছু প্রকাশ পাওয়া যায়। তারই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় সে সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি, পরিবেশে। যে প্রতিবেশে একটি ২৭/২৮ বছর বয়সী মেয়ে সামগ্রিক সমাজ, পরিবেশকে প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করে করে জীবনের সামনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ধর্ম যেন দুজন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের এক হবার পথের কাঁটা বা বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে তাই মমতাজ বেগম মিনু মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী প্রেমিককে সরাসরি বলে, “ধর্ম, যে কোনো ধর্মই হোক আমার কাছে আচার মাত্র, মনের মধ্যে যে ধর্ম বাস করে সেটাই প্রকৃত ধর্ম। আমি সেই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমার সাথে থাকবো ”। দুজনের দুই পরিবার এ মানবিক প্রেমকে আটকে রাখতে পারেনি, না ধর্মের দোহাই দিয়ে, না সদ্য ভাগ হয়ে যাওয়া দুই কাঁটাতারে বিভক্ত দুই বাংলার সীমারেখা দিয়ে।
নারী হিসেবে মিনু ছিলেন স্বাধীন ও নারীবাদীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। বাবাকে মানলেও পুরুষতান্ত্রীক সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, “রায়বাহাদুর মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী আমার পিতা হলেও তিনি পুরুষ। আমি পিতার কাছে হারতে রাজি কিন্তু পুরুষের কাছে নয়।” (পৃ.৫৭) আব্দুল মান্নাফ ঠিকই চিনেছিলেন মমতাজ বেগমকে, “এই মেয়ে তো মেয়ে নয়, জ¦লন্ত অগ্নিকু-।”
উপন্যাসের বর্ণনায় উঠে আসে অন্যান্য সাহসী, ত্যাগী, মানবিক, সংগ্রামী নারীর আলোচনা। যেমন- রোকেয়া সাখোয়াত, সরোজিনী নাইড়ু, লীলা নাগ, অরুণা আসফ আলী, নন্দিতা কৃপালিণী, উষা মেহতা, ইলা মিত্রের ঘটনা। যাদের ত্যাগ, সাহস, লড়াই দেশ গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইলা মিত্রের উপর পাকিস্তানী বর্বররা যে অমানুষিক নির্যাতন চালায় সেই বর্ণনায় পাঠকের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেয়ার অপরাধে পাকিস্তানের পুলিশ থানায় নিয়ে মারিরীক ও মানসিক নর্যিাতন চালায় তাঁর উপর। এসবই সত্য কাহিনি, কোনোটাই বানানো গল্প নয়। পাকিস্তান সরকারের নির্মম নির্যাতনের ঘটনা দগদগে ঘা হয়ে ছড়ানো সারা বাংলায়। মানবিক বিপর্যয়ের প্লট ও চরিত্রের বিন্যাস দেখানো হয়েছে এ উপন্যাসে।
ইতিহাসগত পটভূমিতে রচিত ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ একটি বিশেষ সময়, ঘটনা, স্থান ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যিক মনি হায়দার রচনা করেছেন। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কি নজরে দেখতো তা ফুটে উঠেছে জ¦লন্তভাবে। বাঙালির আবেগ, ভাষাপ্রেম পাকিস্তানিরা কি দৃষ্টিতে দেখতো তা-ও ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসের পাতায় পাতায়।
‘বাঙালি, বাংলা ভাষা- এসব বাড়তে দেওয়া যাবে না। এসব বাড়তে দিলে ভবিষ্যতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে। আর ওই ভূখন্ডে বাঙালি জাতীয়তাবাদ একবার গড়ে উঠলে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। আমরা ভারতের খপ্পরে পরে যাবো।’ (পৃ. ১০৩)
বাঙালিকে নানা উপায়ে পাকিস্তানিরা দাবিয়ে রাখতে চাইতো।ঔপন্যাসিক মনি হায়দার বাঙালি মনোভাব ও পাকিস্তানিদের মনোভাবের বিশদ বর্ণনা উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র মমতাজ বেগম সারা বাংলার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। যিনি দেশের মানুষের জন্য, বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য সমগ্র বাংলার হয়ে একাই লড়াই করছেন পাকিস্তানী শাষক, শোষক ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে। শুধু পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে নয় ইংরেজদের বিরুদ্ধেও মমতাজ বেগম ছিলেন সো”চার। নিজের শিক্ষক মাকেও বোঝাতেন ইংরেজদের জোর-জুলুম-নৃশংসতার পরিস্থিতি-।
উষা মেহতা গোপনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। ধরা পরে জেলে আছেন। এইসব মহান সাহসী মানুষের মধ্যে তুমি-আমি কোথায় মা? যারা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে এই দেশের মাটি ও মানুষ দখল করে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাচ্ছে, ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝোলায়, জালিয়ানওয়ালাবাগে দিনদুপুরে গুলি করে হাজার হাজার ভূমিপুত্র হত্যা করে, তাদের সঙ্গে মেশা যায়, থাকা উচিত আমাদের? ওদের কোনো কাজ সমর্থন করা উচিত? (পৃ. ৩২-৩৩)
দেশভাগের মাত্র ছয় বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছিলো পাকিস্তানিদের মনোভাব। সুজলা, সুফলা পূর্ববাংলায় বানিজ্যিক লাভের আশায় পাকিস্তানিরা নিজেদের ঘাটি গড়ে। নিজেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আর বাঙালিদের নানান অপমানজনক সম্ভাষণে গালিগালাজ করে। যার চরম প্রকাশ ঘটে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে।
কোথায় হাভাতে বাঙালি? এরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সহ্যই করতে পারে না। আবুল আফসার খান বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কেন মাত্র ছয় বছরের মধ্যে দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘৃণার ফলক তৈরি হয়েছে। নিজে যা বুঝেছেন, সেটা কোথাও প্রকাশের সুযোগ নেই। সত্যি, বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, অবকাঠামোর বিস্তারে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। সকল অধিকার থাকার পরও যারা পিছিয়ে থাকে বা রাখা হয়, তারা ঘৃণা করবেই। কিন্তু পাকিস্তান এমন একটা রাষ্ট্র, যার কাঠামো বাস্তবের ওপর নয়, ¯্রফে ধর্মীয় কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। (পৃ. ১৩২)
দু’টি বিশেষ অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্য, মানব চরিত্র, দ্বন্দ্ব-জটিলতা ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। মনি হায়দার বাস্তব সমস্যার আলোকে প্লট, পাত্রপাত্রীর ঐতিহাসিক দৃশ্যপট তুলে ধরেছেন। ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ প্রেমের উপন্যাস না হলেও প্রেম এ উপন্যাসের বিশেষ একটি অংশ জুড়ে পাঠককে রোমান্টিক আবেগে ভাসিয়ে রাখবে। কলকাতায় কল্যাণী রায় চৌধুরী ও আবদুল মান্নাফের দুর্মর-আবেগ-অনুভবমাখা প্রেম তারই সাক্ষ্য দেয়। কখনো আইন কলেজে, কখনো নদী-তীরে সন্ধ্যার আলো আঁধারির ফাঁকে, কখনো চলন্ত গাড়ির ভ্রমণকালীণ সময়ে দুজনার প্রেম পূর্ণতার লাল গোলাপ ফোটায়।
ময়াময়ী নারী, প্রেমময় স্ত্রী, স্নেহময়ী মা কিভাবে দেশের জন্য, মুখের ভাষার জন্য ইস্পাত কঠিন নারীতে পরিণত হয় তারই রূপান্তর ‘ফাগুনের অগ্নিকণ’ উপন্যাসে। সরকারের কোনো প্রলোভনে যিনি পিছু হঠেননি। মেয়ের ভবিষ্যত ও সংসারের মায়ায় আন্দোলনের পথ থেকে সরে যাননি। মমতাজ বেগম সাধারণ একজন নারী, একজন হেডমাষ্টার, একজন স্ত্রী, একজন প্রেমিকা, একজন মা থেকে ক্রমেই শক্ত মনোবলের কারণে, ভাষাপ্রেমের কারণে, দেশপ্রেমের কারণে সবার কাছে ‘ভাষার মা’ হয়ে উঠেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের কারণে এরেষ্ট হয়ে জেলে আসার পথে মর্গান স্কুলের পাঁচজন ছাত্রী সে”ছায় একই গাড়িতে চলে আসে মমতাজ বেগমের সাথে। ভালোবাসার আদরের ছোট্ট সন্তান মা ছাড়া অনাদরে-অবহেলায় পথে-পথে বেড়ে উঠবে এ মহাসত্য জেনেও মমতাজ বেগম আন্দোলন থেকে পিছু হটেননি। একজন মমতাজ বেগম দেশের লাখো-কোটি মানুষের মুখের ভাষার জন্য লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন। একজন মহিলার কাছে জিম্মি হয়ে পরে দুই পাকিস্থান।
উপন্যাসিক মনি হায়দার ইতিহাস-ভিত্তিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’ লিখতে গিয়ে সমাজ-ব্যবস্থা, মানব-মনের নানান বৈচিত্র্যময় আবেগ, অনুভূতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জীবন-সমস্যার গূঢ় জটিলতার প্রকাশ দেখিয়েছেন। নির্বাচিত ঘটনা, সময়, চরিত্র, শিল্পিত গ্রন্থন ও বয়ন এমনভাবে উপন্যাসের প্লটকে সুসামঞ্জস্য ভারসাম্য দিয়েছে যার কারণে সফল হতে পেরেছেন। উপন্যাসের আখ্যান নির্ধারিত ও কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে। অহেতুক চমক সৃষ্টির প্রয়োজন পরেনি। যা সত্য, যা ঘটে গেছে, যা অনিবার্য প্রাণময় বর্ণনা, বিবৃতির মাধ্যমে আবর্তিত হয়েছে। জানা ঘটনাও লেখকের শৈল্পীক লেখনীগুণে রসময়, রহস্যময় ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে পাঠকের কাছে ধরা পরেছে। উপন্যাসের আঙ্গিক তথা শৈলী- ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা ও ভঙ্গী, প্রকরণ, দৃষ্টিকোণ উপন্যাসকে সরল বলিষ্ঠতা প্রদান করেছে। কিছু চরিত্রের কারণে কিছু স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার আছে জায়গা বিশেষে যা ঘটনা, সময়, পরিবেশ-পরি¯ি’তির প্রয়োজনে আরো শৈল্পিকভাবে উপন্যাসকে উ”চাসনে বসিয়েছে। যার প্রয়োগ না করলে তথাকথিত বিষয়টিকে, চরিত্রটিকে, মানসিক অবস্থান ও বিশ্বাসকে ঠিকঠাক উপস্থাপন করা যেত না। এ ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক সফল। কারণ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে উপন্যাসিকের কখনো সংলাপ নির্মাণ করতে হয় আবার সংলাপ প্রকাশের প্রয়োজনে কখনো চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।
ফাগুনের অগ্নিকণা উপন্যাস কেবল উপন্যাস নয়, নয় কেবল ইতিহাসের কাহিনি, এটি একটি ভাষা আন্দোলনের দলিলও বটে। কারণ উপন্যাসিক মনি হায়দার নানান জায়গা থেকে, বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ, চরিত্র, সংলাপ, কাহিনি, পটভূমি ও প্রতিবেশ, শৈলী, সময় নির্বাচন করেছেন ও ঘটনা সংযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। সবকিছুর সাথে উপন্যাসিক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট অবয়ব দিতে সক্ষম, সফল হয়েছেন। উপন্যাসটিকে নান্দনিক ও সৃজনী কল্পনার প্রাণরসে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। এবং মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা ভাষা আন্দোলনের এক মহাবৃক্ষ কল্যাণী রায় চৌধুরী বা মমতাজ বেগমকেও বাংলা ভাষার পাঠকদের দরবারে পৌঁছে দেবার মহার্ঘ দায় পালন করেছেন।
মনি হায়দার লেখালেখি যার প্রাণ। যিনি ঔপন্যাসিক, গল্পকার, শিশুসাহিত্যিক। রুচিশীল ও বৈচিত্রময় লেখায় যিনি পারদর্শী সাহিত্যিক। শিশুদের জন্য সৃজনশীল, মননশীল লেখা যেমন তিনি রচনা করেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ ঐতিহাসিক বিষয়কে পটভূমি করে তিনি রচনা করে চলেছেন গল্প উপন্যাস-সমূহ। পরিছন্ন ও ঝরঝরে শব্দ, বাক্যে তিনি লেখেন ঘটনা ও পটভূমির উপযোগ। সংক্ষিপ্ত ও আবেগরহিত বর্ণনা, ঘটনা ও চরিত্রের সাথে আবেগী সংযোগ ঘটিয়ে তিনি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখেন লেখায়। মনি হায়দার লেখেন তন্ময় দৃষ্টিতে। লেখায় বর্ণনার অপ্রয়োজনীয় বিস্তৃতি থাকে না তাই পাঠক একঘেয়েমীতে ভোগে না। ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার জটিল বিনুণীতে চাপা পড়ে যায় না। সরল ভাষায় জটিলতাহীন বর্ণনা পড়তে পাঠকের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় বইয়ের পৃষ্ঠা ও পুরো উপন্যাসের পাতা। সৃজনী কল্পনা, ভাষা ও বর্ণনার মাধ্যমে জীবনের জটিল ও পূর্ণতর রূপকে প্রকাশ করে। সমাজ-জীবনের বহুমাত্রিক টানাপোড়েনের উন্মোচন ঘটিয়ে উপন্যাসকে সার্থক করে তোলেন এবং চরিত্র, বিষয় ও সময়ের ঈঙ্গিতময় বিস্তার ঘটান।
মনি হায়দারের এ পর্যন্ত প্রায় ১১২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে গল্পগ্রন্থ: আঠারো বছর পর একদিন, একটি খুনের প্র্সতুতি বৈঠকের পর, ইলিশের মাংস, আমার বীনু খালা, এক ঝাঁক মানুষের মুখ, থৈ থৈ নোনাজল, আঠারো বছর পর একদিন, একটি খুনের প্রতি বৈঠক,ঘাসকন্যা, জিহ্বার মিছিল, রক্তাক্ত গ্লাসের গল্পগুলো, ঘাসকন্যা, ফ্যান্টাসী, গল্প পঞ্চাশ।
উপন্যাসত: ফাগুনের অগ্নিকণা, কিংবদন্তির ভাগীরথী, চলুন- মানুষের কারখানায়, অধ্যাপক কেনো মানুষ হইতে চায় না, সুবর্ণ সর্বনাশ, নায়ক ও নায়িকারা, মেয়েটি সমুদ্রে ডুবে যেতে চেয়েছিল, এক টুকরো কাগজ, মোকাম সদরঘাট।
গল্প উপন্যাস সম্পাদনা মিলিয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে গত চল্লিশ বছরের সাধনায়।
পুরষ্কার ও সম্মাননা
পুরষ্কার ও সম্মাননার মধ্যে মনি হায়দার পেয়েছেন,
নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরষ্কার ২০০৮
অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরষ্কার ২০০৯ সহ আরো অনেক।
***********************