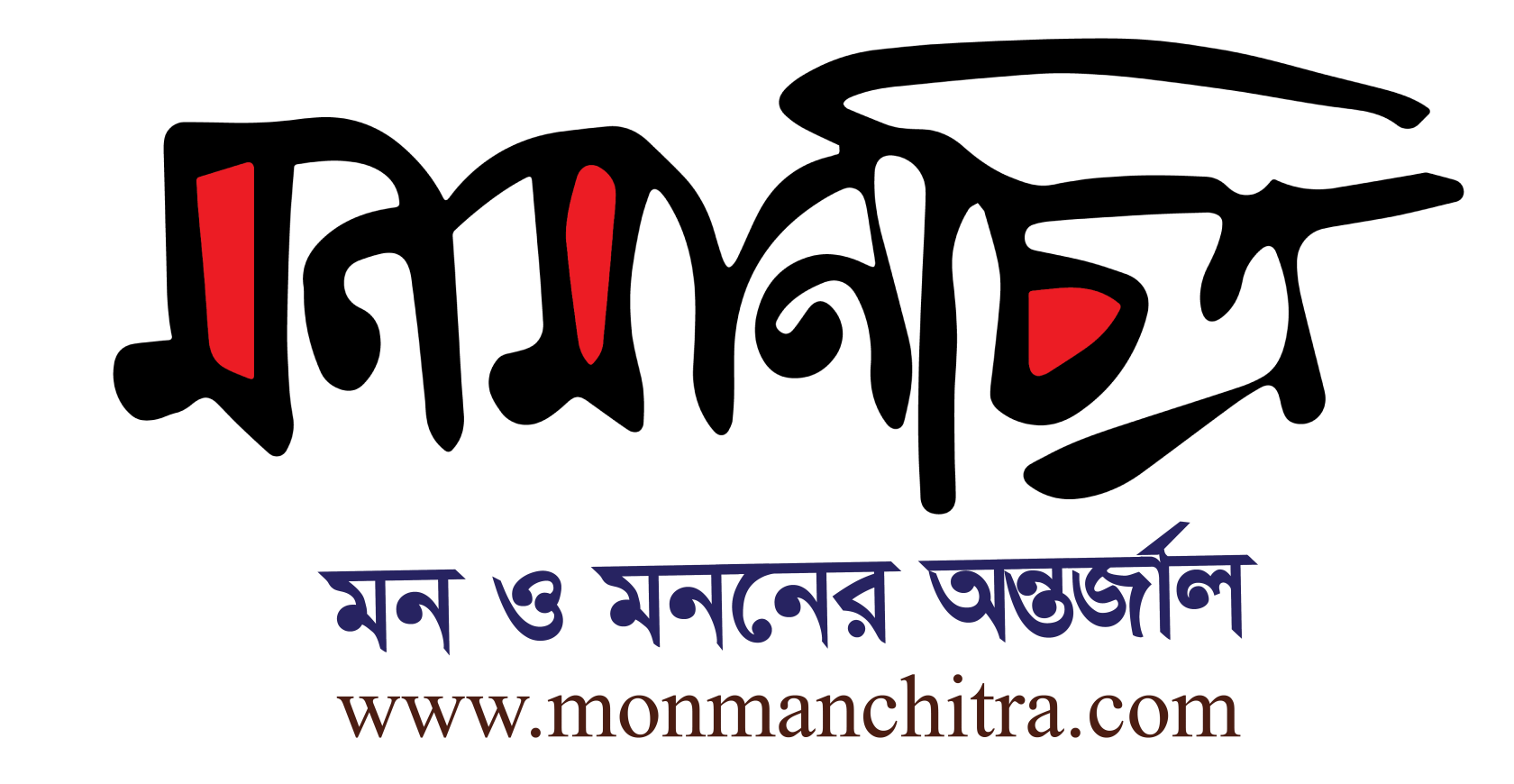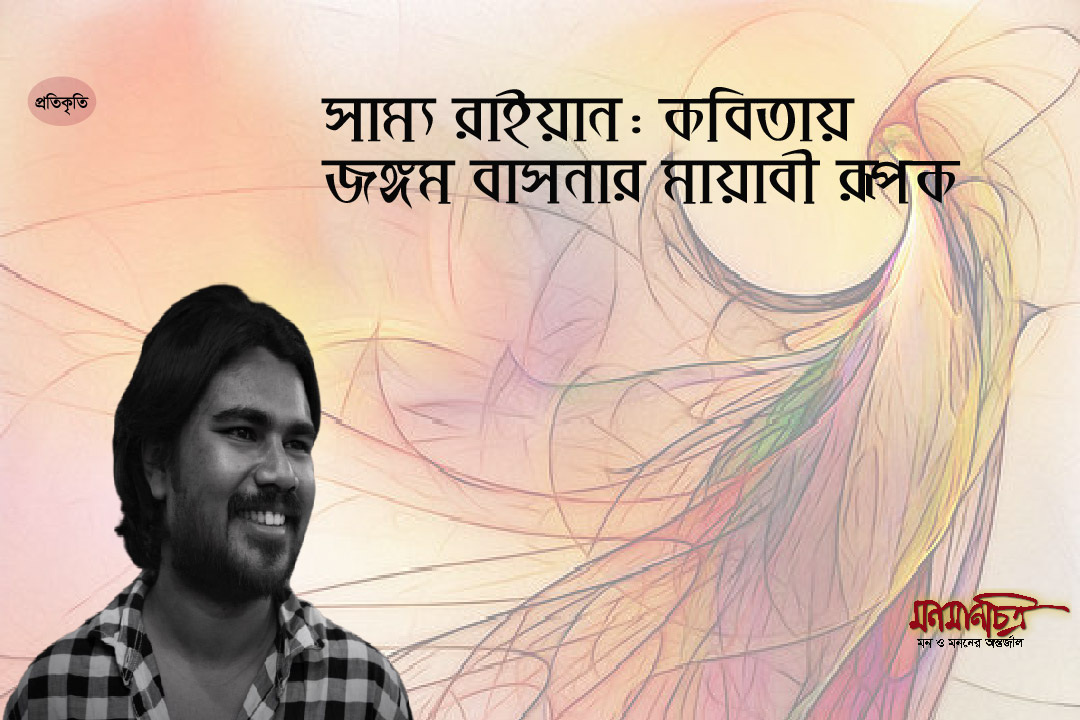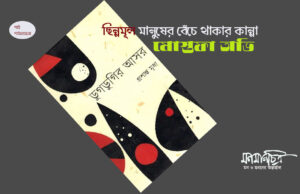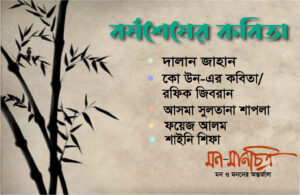সাম্য রাইয়ান: কবিতায় জঙ্গম বাসনার মায়াবী রূপক
কবি সাম্য রাইয়ান। নিজস্ব ভাষার চুনসুরকি ছড়িয়ে পথের অন্বেষণে শব্দময়তায় নিমগ্ন এক কবি মানস সাম্য রাইয়ান। বিন্দু থেকে বিসর্গ হয়ে অনিকেত এক পরিব্রাজক সাম্য রাইয়ান যার অবধারিত গন্তব্য হয়ে ওঠে মানুষ ও মানবমন। মনমানচিত্রের প্রতিকৃতি’র আয়োজনে সাম্য রাইয়ানের কাব্য ভাবনা ও শব্দশিল্পের কারুকাজকে প্রথম উপস্থাপন করা হচ্ছে।
সূচীপত্র
পরিচিতি
মনমানচিত্র-এর সাথে কথোপকথন
একগুচ্ছ কবিতা
সাক্ষাৎকার: লাবণী মণ্ডল
প্রবন্ধ:
অমিতাভ অরণ্য/ শামীমফারুক
বিপুল বিশ্বাশ/ হোসাইন মাইকেল
ধীমান ব্রহ্মচারী/ শামীম সৈকত
তানজিন তামান্না/ ড. সুশান্ত চৌধুরী
সৈয়দ আহসান কবীর/ মাহাদী আনাম
ড. অমিতাভ রায়/ প্রবাল চক্রবর্তী
ড. মধুমঙ্গল ভট্টাচার্য/ ফেরদৌস লিপি
পরিচিতি:
সাম্য রাইয়ানের জন্ম নব্বই দশকে; ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ, বাঙলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায়৷ স্কুলজীবনে কবিতা লেখার হাতেখড়ি৷ প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘মঞ্চ’ পত্রিকায়৷ ২০০৬ থেকে লিটল ম্যাগাজিন ‘বিন্দু’ (www.bindumag.com) সম্পাদনা করছেন৷ কবিতা, মুক্তগদ্য ও প্রবন্ধ লেখেন৷ প্রকাশিত পুস্তিকা:বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা (কবিতা)সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট (গদ্য)মার্কস যদি জানতেন (কবিতা)হলুদ পাহাড় (কবিতা) প্রকাশিত বই:চোখের ভেতরে হামিং বার্ড (কবিতা)লোকাল ট্রেনের জার্নাল (মুক্তগদ্য)লিখিত রাত্রি (কবিতা)হালকা রোদের দুপুর (কবিতা) সম্পাদিত বই:উৎপলকুমার বসুজন্মশতবর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট: sammo.bangmoy.com
মনমানচিত্রের সাথে কথোপকথন
১। লিখিত রাত্রি ।। কবিতাগুলোর বুনন খুব সংহত, কিন্তু কবি’র অন্তর্লোক বড় ছত্রখান। কবি হিসাবে কী বলবেন?
উত্তর: ‘লিখিত রাত্রি’ অনেক মগ্নতার বই, অশেষ ভালোবাসারও। যা রচিত হয়েছিলো ২০১৫-র জুন ও জুলাই মাসে৷ এখন ভাবতে অবাক লাগে কী আশ্চর্য মগ্নতায় আমি রচনা করেছিলাম মাত্র এক/দেড় মাসে এই পঞ্চান্নটি কবিতা! অথচ ওই সময় আমি মানসিকভাবে খুবই ডিসটার্বড ছিলাম৷ চারদিক থেকে এত এত আঘাত— বারবার ভেঙে আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলাম৷ রচনার ছয় বছর বাদে ঘাসফুলের কল্যাণে পাণ্ডুলিপিখানা আলোর মুখ দেখেছিলো৷ এর মধ্যে কত সম্পাদনা, কত মাতামাতি এই সিরিজ নিয়ে!

পঞ্চান্ন পর্বের এই সিরিজজুড়ে আছে রাত্রির গল্প— অনেক রাত— রাতের পর রাত যা লিখিত হয়েছে— এক রাত্রিতে এসে তা মিলিত হয়েছে৷ সেখানে বিস্তৃত হয়েছে রাত্রির নিজস্ব আসবাব— কুকুর, পতিতা, নাইটগার্ড, পাখি, কবি, প্রেম, বিবাহ, ট্রাক ড্রাইভার…!
২। লোকাল ট্রেনের জার্নাল।। একেবারে গৃহস্ত ঘরের প্রেমিক ছেলেটি বুঝি আকুতিগুলো বলে যাচ্ছে একের পর এক। আপনার কী মনে হয়?
উত্তর: ‘কবিতার দুর্বোধ্যতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, “কবিতা সম্বন্ধে ‘বোঝা’ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝিনে; কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু ‘বোঝায়’ না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা ‘বোঝা’ যাবে না, ‘বোঝানো’ যাবে না।” আমি বুদ্ধদেবের এ বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত৷ কবিতা আমরা অনুভব করতে পারি৷ এমত ভাবনা থেকেই ২০১০ সালের দিকে শুরু করেছিলাম এক নতুন খেলা— কবিতা বনাম কবিতা কবিতা খেলা! এ হলো সিরিজ গদ্য৷ প্রথম গদ্যটি লিখেছিলাম, ‘সময়ের অসহায় দাস’, যা পরে বাতিল করেছি৷ এরপর লিখেছি, ‘হাঁটতে হাঁটতে পথ গ্যাছে ক্লান্ত হয়ে’৷ এরপর ক্রমান্বয়ে আরো প্রায় দশ-বারোটি গদ্য লিখেছি৷ এই গদ্যগুলোতে আমি বাঙলা ভাষার বিশেষত নতুন সময়ের নতুন কবিদের কবিতা পাঠপরবর্তী অনুভব ব্যক্ত করেছি৷ এগুলো মূল্যায়নধর্মী গদ্য নয়৷ কখনো কবিতা পড়তে পড়তে আমার মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তা বিবৃত করেছি৷ আবার কখনো কোন কবিতা পড়ে ব্যক্তিগত কোন স্মৃতি মনে পড়েছে, তা-ই উল্লেখ করেছি৷ হুবহু, অকপটে!
৩। চোখের ভেতরে হামিংবার্ড।। বইটিতে কেমন একটা শ্লোকের মত ব্যাপার আছে, আর আছে কেমন একটা স্বস্তির ভাবে। এমনটা কীভাবে হলো- আগের বইয়ের ছেঁড়াছেঁড়া ভাবটি কোথায় গেল?
উত্তর: কবিকে আমার কেবলই মনে হয়- জীবনব্যাপী সম্পর্কশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করে চলা ব্যক্তি৷ সে নানান সম্পর্ক- প্রাণের সাথের প্রাণের, প্রাণের সাথে প্রাণহীনের, ক্ষুদ্রপ্রাণের সাথে মহাপ্রাণের- সকল সম্পর্ক। এই প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন-রক্ষা-চ্ছেদ-বিকাশ বিষয়েই মনে হয় জীবনের সকল গবেষণা৷ সেই সম্পর্কশাস্ত্রেরই এক রূপ ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’৷ এর উৎসর্গে লেখা আছে- ‘সোনামুখী সুঁই থেকে তুমি/ চুইয়ে পড়ো সুতো হয়ে/ নিচেই বিদ্ধ আমি/ সেলাই হই, তোমার সুতোয়।’
‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ বইয়ে আমি একই ফর্মের কবিতাগুলো রেখেছি৷ যেমনটা আমি প্রতিটি পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে করি৷
৪। বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা।। কাব্যগ্রন্থের নামটি দেখে মনেহয়, এটি একজন মাওবাদী গেরিলা কবি’র কবিতা হয়ে উঠতে পারতো৷ কিন্তু তা হয়নি, যদিও পোড়খাওয়া রাজনৈতিক স্বপ্নের একটি আঁচড় আছে এখানে। বইটি সম্পর্কে কিছু বলুন।
উত্তর: এ পুস্তিকাটি আমার লেখালিখির শুরুর দিকের কয়েকটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত৷ তখন ছাত্র আন্দোলন করতাম৷ আর বাঙলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমি শুরু থেকেই হতাশাবাদী ঘরানার৷ ফলে কবিতায় এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন বোধ করি৷ আর আমি এক সময়ে একরৈখিক কবিতাই লিখেছি তা নয়৷ একই সময়ে আমি বহুরৈখিক কবিতা লিখেছি৷ কিন্তু পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে আমি সময় নিয়েছি অনেক৷ এর প্রধান কারন হলো, আমি চেয়েছি কনসেপচুয়াল পাণ্ডুলিপি হোক প্রতিটি৷ ফলে একই সময়ে ‘বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা’ ও ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ বইয়ের কিছু কবিতা লিখলেও পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে কবিতাগুলোকে আমি আলাদা করে ফেলেছি৷
৫। মার্কস যদি জানতেন।। এই বইয়ের কবিতাগুলো আরও বেশি তির্যক ও সরাসরি হবে বলে ধারণা করেছিলাম, কিন্তু বাস্তবত সরাসরি না হয়ে কবিতাগুলো যথেষ্ট পরিমাণেই রূপকাশ্রয়ী- আপনার বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞান কী এমন যে, কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি, বা শ্রেণীসংগ্রামের জঙ্গমতা আসলে এর শৈল্পিক ভারসাম্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে?
উত্তর: আপনার প্রশ্নের শেষাংশে আমার উত্তর আছে৷ আমি এমনটাই মনে করি, কবিতা আড়াল দাবি করে৷ আর এ প্রসঙ্গে আরেকটু বলি, আমার ধারনা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা বড় ফ্যাক্ট৷ বাঙলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরাসরি কথা বলার কোন সুযোগ নেই৷ একসময় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইস্যুতে কার্টুন অনেক জনপ্রিয় ছিলো৷ কিন্তু আজ সেসব কার্টুন বিলুপ্ত! এর কারন বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা৷ কিন্তু এই ফর্মটি পরিবর্তিত হয়ে ‘মিমস’ রূপে প্রকাশিত হচ্ছে৷ দুঃখের কথা হাসির ছলে বলছে৷ মানুষের বেদনা ঘনীভূত হতে হতে এমন রূপ ধারণ করেছে যে, তা নিয়ে নিজেই মশকরা করছে৷ কারন তার প্রতিবাদ করার শক্তিও আর নেই৷
তবুও এসময়ের কবিতায় এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়৷ সময়ে সময়ে কবিতার ফর্ম বদলে যায়৷ প্রতিবাদের কথা, রাজনৈতিক চিত্র— সেসব থাকে নতুন সময়ের ফর্মে৷ ষাট, সত্তর কিংবা নব্বই দশকে যে ফর্মে রাজনৈতিক কবিতা রচিত হয়েছে, আজ নতুন শতকে এসে সেই ফর্মে কবিতা লেখা হবে না, এটাই স্বাভাবিক৷ তারই প্রতিফল হয়তো পাচ্ছেন ‘মার্কস যদি জানতেন’-এ৷
৬। হলুদ পাহাড়।। বইটিতে আবছা কোথায় যেন খানিক পরাবস্তবতার পোঁচ আছে। হলুদ পাহাড় নিয়ে আপনার অনুভব কী?
উত্তর: ‘হলুদ পাহাড়’ এর কবিতাগুলো আমি এক মাসে লিখে ফেলেছিলাম৷ যেন হঠাৎ করেই এই সবগুলো কবিতা আমার কলমের ডগায় উপচে পড়ছিলো৷ অন্তর্গত অনুভূতিমালা আর দৃশ্যের বিবরণ লিখেছি; আমি যা দেখি— যেভাবে আমার চোখে ধরা পড়ে, তা-ই… হয়তো আমার ‘দেখা’ ‘স্বাভাবিক’ নয়… পরাবাস্তব হতে পারে…
৬। আপনার প্রত্যেকটি বই ভাবে ও ভঙ্গিমায় আলাদা আলাদা। আপনি কী থিমেটিক্যালি বইগুলো করেছেন?
উত্তর: একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি হবার পর আমি সময় নিই; মাসের পর মাস কিছু লিখি না৷ পূর্বের ফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করি৷ নতুন কিছু লিখতে চাই৷ নতুন চিন্তা— নতুন ফর্মে৷
আমার এমন হয়; দেখা যায়, মাসের পর মাস আমি কবিতা লিখিনি, লিখতে পারিনি; শুধুই ভেবেছি— চিন্তিত হয়েছি৷ কখনো বছর পেরিয়ে গেছে— কবিতা আসেনি! আগে মনে করতাম আর বুঝি লিখতে পারবো না, আমার বোধয় লেখা শেষ৷ কিন্তু না৷ তার পরই হঠাৎ করে কবিতা লিখতে শুরু করি; মনে হয় সাইক্লোনের মতো সবকিছু ভেঙেচুড়ে আসছে৷ দুর্বার গতি— যাকে রোধ করা অসম্ভব৷ এমন অবস্থা থাকে এক থেকে দেড় মাস৷ সেই সময় প্রচুর কবিতা লিখে ফেলি৷ এভাবেই লেখা হয়েছে ‘হলুদ পাহাড়’, ‘লিখিত রাত্রি’, ‘হালকা রোদের দুপুর’…
৭। একদম সাম্প্রতিক কালে অনেকের কবিতায় কেমন ধাঁধার মত একটা ব্যাপার থাকে। মনে হয়, পাঠকের যেন একটি ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ধরুন আপনার এই কবিতাটি-
হেমন্তে
উঠোনের সমস্ত ব্যর্থতা খুবলে আনা হৃৎপিণ্ডের
মতো প্রকাশ করা দরকার আজ। উনুনের গভীরতম
ক্যানভাস থেকে বের করে আনা দরকার সমস্ত অমুদ্রিত
জলের ইতিহাস। ডুবন্ত চাঁদের যাত্রী কীভাবে,
সেইসব তীব্র বিরল ছবি অলক্ষ্যে রোদের বাগানে
ফুটাতে দিয়ে কোনদিন, সূর্যবেলায় খুব নির্ভার হবো।
আপনার কী মনে হয়, এই কবিতাটি পাঠকের প্রাণের কাছে আরও অনায়াস হয়ে উঠতে পারতো?
উত্তর: আমি আসলেই চাই অনায়াস করে তুলতে৷ এমন একটি প্রচেষ্টা আমার মধ্যে কাজ করে৷ হয়তো পারি না, পেরে উঠি না ঠিকমতো৷ কিন্তু সহজ করে বলতে চাই৷ স্বাভাবিকভাবেই লিখি, বাড়তি কসরত আমি করি না কবিতায়৷ কিন্তু তা যে রূপ ধারণ করে তা কতোটা ‘স্বাভাবিক’ মনে হয় পাঠকের কাছে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই৷
৮। সব কবিরই জানায় অজানায় একটি দর্শন থাকে- আপনার দর্শন কী?
উত্তর: আমার দর্শন, সে তো কবিতায়ই প্রকাশিত৷ সেই দরশনের কথাই লিখি কবিতায়৷ আমার কবিতাই আমার দর্শন৷
৯। আপনি বাংলা কবিতার পরম্পরায় নিজেকে কীভাবে যুক্ত করেন? আবার বাংলা কবিতার পরম্পরা থেকে নিজেকে কোথায় বিযুক্ত করে প্রাতিস্বিক হয়ে ওঠেন?
উত্তর: আমার কথা, আমার বক্তব্য, যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার যা চিন্তা তা আমি লিখি; লিখে বলি; এছাড়া আমার আর কোনো মাধ্যম নেই; বিকল্প নেই৷ আমি তা-ই লিখতে চেষ্টা করি কবিতায়— যে কথা আমার, যা কেউ বলছে না৷ বলার ভঙ্গিতে নতুন কিছু করবার প্রয়াস আমার মধ্যে থাকেই৷ এতে কতটুকু সফল আর কতটুকু ব্যর্থ তা পাঠকই বলতে পারবেন৷

একগুচ্ছ কবিতা
বিবাহবার্ষিকী
বিবাহবার্ষিকীতে নিষ্পত্র ছিলাম। অঘোষিত
ভঙ্গিতে নেমে এলো প্রেম, যেভাবে সন্ধ্যে নামে
ব্রহ্মপুত্র তীরে। সম্মোহনী সংগীতে জাগে
কুয়াশার সমূহ কম্পন। নিয়তিবৃক্ষ ছিঁড়ে যায়
চাঁদ নেমে আসে জলের মোহনা আর ফসলের ক্ষেতে
নিউট্রাল বিউগলে জাগে দিনের সকল রাত
জগতে সকলই রাজনীতি আর আর্থিক আলোচনা
তবুও তখন দুমদাম লাল আমার নিটোল বুকে।
নিউটন
নিরাকার-জলের সাইরেন
এলো আমফান-সাফোর
কলোনীতে। বৃষ্টিবৈভবে
জেগে উঠি
শব্দ হয়
নিউটন, আপেলতলায় থাকো
বাড়িতে যেও না
বাড়িতে হৃদয় নেই
মানুষভর্তি বেদনা
জলের অপেরা
ডানা আঁকো-সশব্দে ঝাপটাও
ডাকছে ব্যাকুল নদী
শিহরিত
হেঁটে হেঁটে আমি পৌঁছলাম
নদীর কাছে। অনেক মানুষ-
যারা হৃদয় ফেলে এসেছে
ধরলার জলে; সকলে
একত্রিত আজ। হারানো
হৃদয়ের গান শুনছে মেয়েটি-
ছেলেটিও।
হাঁটু মুড়ে ওর পাশে বসি
আমি তো যাবো না কারো সাথে
তোমার উপশিরা
যেদিকে এঁকেছে পথ
শুধু সেই দিকে যাবো।
অন্য কোনো জলে
যাবো না।
বসন্তের সনেট
অহেতুক বসন্তের রোদ-অসময়ে ঝড়
বিরক্ত শিশুর কান্না… এরকম টুকরো-টাকরা
শীত-মিশ্রিত সময়ের প্রবচন!
তোমার চুলের ভাঁজে
এক তোড়া সনেট গুঁজে দাও
মরা নদী ভাষা ফিরে পাবে।
নামকরণের সার্থকতা
নামকরণের সার্থকতা নেই। একা
যেতে যেতে ভাবি, বুড়িগঙ্গায় প্রবাহিত
জীবনের সকল প্রণাম। শান্ত হয়ে
ভেসে যেতে থাকে বেকসুর কান্না।
দেখেছি কয়েকদিন, শহরতলীতে নেই বাণিজ্যবিশেষ
গীতবিতান সুদূর পরাহত, তুমিও নিরুদ্দেশ!
নৈশসঙ্গী
আলোগুলো লাল আর নীল
-টলমল করে
চারটে লোকের ভারে কেঁপে ওঠে
ইঞ্জিনের ঘোড়া।
টগবগিয়ে
কেঁপে কেঁপে ওঠে সমূহ পথের দিশা…
নেমে যাই
এই রাস্তা চলে গেছে
অধিকতর নিঃসঙ্গতার দিকে।
পুরনো শহরে বয়সী শামুক, হেঁটে যায়
অক্ষয়দাস লেন পেরিয়ে-
পকেটে মুদ্রা নাচে।
গলির মুখে নাচে পুলিশের গাড়ি।
বেদনাহত কোকের বোতল ছুঁয়ে
নৈশ বন্ধুর সাথে ট্রাফিক পেরিয়ে হাঁটি
অদেখা প্রতিবেশিনীর নিঃশ্বাস কাঁধে
টের পাই, আমরা তখন মেঘের ছায়ায়
অন্ধকার, বৃষ্টিহীন গ্র্যাণ্ড এরিয়ায়!
ভ্রমণ বিষয়ক
প্রথমে জঙ্গলে যেতে চেয়েছিলাম
ক্রমান্বয়ে পাহাড় আর সমুদ্রে।
জঙ্গলে গেলে না তুমি, পোকামাকড়ের ভয়!
তাহলে সমুদ্রেই চলো; পাহাড়ে
গণ্ডগোল খুব, বিষাক্ত সেনাদল আর
নিরাসক্ত প্রাণীদের ক্যাম্প।
ফাল্গুনের রোদে
সকালে মিষ্টি রোদের দিন-
কুম্ভ-সূর্য জাগে আদিবাভঙ্গিতে
বাড়ি ফিরে- নিস্তরঙ্গ তারা
ইশারাভাষায় ডাকে মাতৃভাষাবনে।
আচ্ছাদন পেরিয়ে যেদে চাই
দ্রুত!
চোখ বুজে শুনি- ডাকছে আকাশ
ছোট হচ্ছে আলো।
ফাল্গুনের বিকেলবেলায়
গতকালের বাতাশ- আজ খুব এলোমেলো।
মানতে চাই না তবু, কৈবল্য আঁকড়ে
ধরে হাত! স্বপ্নে চিৎকার করে উঠি
দেখেছি অবাক-পরিখা। এইমাত্র ডাকে
সাড়া দিলো যে- বলি, ব্যাগ গুছিয়ে দাও
দেরি হয়ে যাচ্ছে!
আত্মজীবনী
অর্ধেক জীবন গেল
তোমার দিকে চেয়ে।
বাকী অর্ধেক
তোমার কথা ভেবে।
বানানবিভ্রাট
এতো যে জোনাকি-আলো, পথ দেখায় না, আশা জাগায় না; ব্যথা ভোগায় না কিছুই!
আমি শুধু জন্মকে মৃত্যুর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে ভালোবাসি। প্রতিবার জন্মের
ত্রুটি নিয়ে এতো যে প্রবণ-মাঝি!.. তোমার জন্য লাগে আমার কব্জি-জোরের থেকে
বেশি, পুরোনো ক্রোধের সুরে গর্জন। কেন প্রায়শ গোলাপের নামে প্রতারণা
মুদ্রণ করো! শীতার্ত ভয়ে কেঁপে ওঠা, দুলদুল এই পাতাগুলো অসহায়, কপর্দক
ছুঁতে পারছে না। সোডিয়াম বাতি থেকে মিনতিমিনার অব্দি, ভাসে অনঙ্গ বাতাশ
শুধু বাদামের পাতা থেকে যথার্থ মনীষা জাগাতে। আমার ঈশ্বর তুমি, ভেতরে
সবুজাভ পাট; অথচ আশ্চর্য, তোমারই হৃদয়ে ঘটে বানানবিভ্রাট!
*********************************
সাক্ষাৎক্ষার: লাবণী মণ্ডল
‘এদেশে বেশির ভাগ লিটলম্যাগ মানে বনসাই প্রকল্প’
সাম্য রাইয়ান- কবি, প্রাবন্ধিক, লিটল ম্যাগাজিন কর্মী, অ্যাকটিভিস্ট। সম্প্রতি তিনি কবিতা, কবিতার বিভিন্ন ধরন, লিটল ম্যাগাজিনসহ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানাদিক, নিজের কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে উঠে আসে কবিতা ভাবনা, জীবন ভাবনা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে স্বকীয় চিন্তার প্রতিফলন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন লাবণী মণ্ডল।
প্রশ্ন: আপনার কবিতার সূচনা ও যাত্রাপথ সম্পর্কে জানতে চাই।
উত্তর: শব্দখেলার আনন্দ থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। তখন প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অন্তমিল তৈরি করতে, সুর তৈরি করতে আনন্দ হতো। সেই থেকে শুরু, এরপর তো চলছে। ছোটবেলা থেকে গল্পের বই পড়া নেশা হয়ে গিয়েছিলো। পিতৃপ্রজন্মের কল্যাণে আমি জন্মের পরই বাড়িতে বইয়ের সমারোহ পেয়েছিলাম। সেই থেকে বইয়ের সাম্রাজ্যে ঢুকে গেলাম!
প্রশ্ন: আপনার কাছে কবিতা মানে কী?
সাম্য রাইয়ান: কবিতা আমার কাছে জীবনদর্শন। সূর্যের এক হাত নিচে মেলে দেয়া শরীরের দগদগে ঘা।
প্রশ্ন: কবিতার বিভিন্ন ধরন বা ফর্ম আছে। আবার এ সময়ে আমরা দেখছি শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য অনেক ধারার মতো কবিতাও ফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে। কবিতার এ দীর্ঘ যাত্রাপথে আধুনিক-উত্তরাধুনিক কবিতার বিভাজন বা ছন্দের ধারা সবই ভেঙে পড়ছে। আবার নতুন ফর্ম গড়েও উঠছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী?
উত্তর: কবিতার ফর্ম নিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। ফর্ম মুক্ত হওয়া আসলে একটা ধাঁধা। কারণ তা কেবলই এক ফর্ম থেকে বেরিয়ে আরেক ফর্মের দিকে যাত্রা!
প্রশ্ন: সার্থক কবিতা হয়ে ওঠার জন্য একটি কবিতায় কী কী থাকা জরুরি মনে হয়?
সাম্য রাইয়ান: সার্থক কবিতা হয়ে ওঠার জন্য অনুকরণ বাদ দিতে হবে। আবার বলি, অনুকরণ বাদ দিতে হবে। অনুকরণ মানুষ করবে না, অনুকরণ বানরের ধর্ম, মানুষ বানর নয়। প্রথমত, চিন্তার গভীরতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তার প্রকাশভঙ্গি নতুন হতে হবে। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, চিন্তাটা সৎ হতে হবে।
প্রশ্ন: সমকালীন ও বিশ্ব সাহিত্যে কাদের লেখা আপনাকে প্রভাবিত করেছে?
উত্তর: আমার মনে হয়, আমি এ যাবৎ যা কিছু পাঠ করেছি, তার সবই আমাকে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করেছে।
প্রশ্ন: আপনার কবি সত্তা-প্রাবন্ধিক সত্তা-সম্পাদক সত্তা, এ তিনটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
উত্তর: আমি মূলত কবিতা লিখি। মাঝেমধ্যে প্রবন্ধ লিখি। পরিমাণে তা খুবই কম। আর সম্পাদনার কথা বললে এভাবে বলতেই পছন্দ করবো—আমি প্রধানত লেখক, লেখার প্রয়োজনে সম্পাদক। নিজের ভেতরে সম্পাদক সত্তা আমার লেখার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখে। নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সুবিধে হয়। আমি নিজেই নিজের প্রথম ও প্রধান বিচারক।
প্রশ্ন: উৎপলকুমার বসু বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকের কবি। তাঁকে নিয়ে আপনার সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশিত হয়েছে গত বইমেলায়। তিনি কেন আজও প্রাসঙ্গিক?
উত্তর: উৎপলকুমার বসু এমনই এক কবি, যিনি বেঁচে থাকতেই হয়ে উঠেছিলেন বাংলা কবিতা জগতের অনিবার্য নাম। তার কবিতা পাঠকের কাছে এক বিস্ময় আর রহস্যের আধার হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনি তো সকলের মতো লেখেন না, তার আছে এক ‘ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা’। যার সম্মুখে দাঁড়ালে মনে হয়, এর সকল শব্দই বুঝি অমোঘ—বিকল্পহীন!
পুজো করতে নয়, আতশকাচের তলায় বুঝে নেওয়ার কাঙ্ক্ষা থেকেই ২০১৫ সালে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করি বিন্দুর উৎপলকুমার বসু সংখ্যা প্রকাশের। এর মধ্যে আমাদের হতবিহ্বল করে উৎপল প্রয়াত হলেন ওই বছরের অক্টোবরে। পরের বছর সেপ্টেম্বরে মাত্র ছয়জন লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশ করলাম বিন্দুর ক্রোড়পত্র—‘স্পর্শ করে অন্য নানা ফুল’। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা প্রকাশের ভাবনা মাথায় রয়েই গেল। অবশেষে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় চারশত পৃষ্ঠার সেই বই আলোর মুখ দেখেছে, ভারত ও বাঙলাদেশের অর্ধশতাধিক লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে।
প্রশ্ন: কবিতার অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি অর্থাৎ আঙ্গিক, উপমা, ছন্দ, শব্দের বুনন, ভাষার ব্যবহার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মিথ ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?
উত্তর : কবিতার আঙ্গিক, তার শরীরে ছন্দ—এই সকলই চলে আসে কবিতার প্রয়োজনে। ফর্মটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি এমন কোনো ফর্মে লিখতে চাই না যা চর্বিতচর্বন। নতুন চিন্তা, যা আমি প্রকাশ করি, প্রচার করি; তা নতুন ফর্মেই প্রকাশ করতে পছন্দ করি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য জঁ লুক গোদার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সুবিমল মিশ্র লিখেছিলেন, ‘বলার ভঙ্গিটাই যখন বিষয় হয়ে ওঠে।’ কখনো কখনো এমনটাও হয়; আঙ্গিক নিজেই বিষয় হয়ে উঠতে পারে।
আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই থাকে; যদি তিনি ‘ক্রিয়েটিভ লেখক’ হন। আমার কবিতার ক্ষেত্রে একসময় নিরীক্ষাচেষ্টাগুলো জ্বলজ্বলে হয়ে থাকতো, কারণ সেই নিরীক্ষাগুলো ছিলো বাহ্যিক, দৃশ্যমান। কিন্তু আমার বর্তমান কবিতায় বাহ্যিক, দৃশ্যমান নিরীক্ষা কমে তা কবিতার অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমার সকল বইয়েই নতুন কিছু কাজ আমি করতে চেষ্টা করেছি; নতুন শব্দবন্ধ, বাক্যগঠন, চিন্তায় নতুনত্ব…। কিন্তু তা পাঠকের পাঠপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না। আমি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকলন করি না, কনসেপচুয়ালী পাণ্ডুলিপি গোছাই। প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা বলি, ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ বইয়ে এমন ধরনের গদ্য আমি লিখেছি, যা আমার জানামতে নতুন। ২০১১ থেকে এই ধরনের গদ্য আমি লিখতে শুরু করেছি। রাঁধুনী কতটা এক্সপেরিমেন্ট করে তরকারি রেঁধেছেন এটা ভোজন রসিকের আগ্রহের বিষয় নয়; তার একমাত্র আগ্রহ স্বাদে। এক্সপেরিমেন্ট বা কৌশল রাঁধুনীর ব্যক্তিগত বিষয়।
আর নিরীক্ষা যেন পাঠ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত না করে। ধরুন, একজন ইঞ্জিনিয়ার ভাবল বাসের সিট কভারে এত বছর এত এক্সপেরিমেন্ট করলাম, সবাই তার সুফল ভোগ করল—আরামে ভ্রমণ করলো; কিন্তু এর জন্য কত এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছে তা নিয়ে যেহেতু কেউ কথা বলছে না, এবার একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। এই ভেবে তিনি বাসের সিট কভারে কাটা গেঁথে দিলেন। বাসের যাত্রীরা এবার হারে হারে টের পেল ইঞ্জিনিয়ার এক্সপেরিন্ট করেছেন! তো এই ধরনের লোক দেখানো এক্সপেরিমেন্ট আমি করি না। পেন ওয়ারেন তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “এক্সপেরিমেন্টাল লেখা আবার কী? জেমস জয়েস কোনো এক্সপেরিমেন্টাল লেখা লেখেননি, তিনি ‘ইউলিসিস’ লিখেছেন। টি এস এলিয়ট ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ড’ লিখেছেন। যখন আপনারা একটা জিনিস ঠিক ধরতে পারেন না, তখনই তাকে এক্সপেরিমেন্ট বলে ফেলেন; এটা চাপাবাজির একটা অভিজাত শব্দ।”
প্রশ্ন: সচেতনভাবে, অবচেতনে বা পরিকল্পনা করে, বিভিন্ন উপায়ে কবিতা লেখার কথা প্রচলিত রয়েছে; এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন ও নিজে কীভাবে লেখেন?
উত্তর: কবিতাগুলো আসলে কী এক ঘোরের মধ্যে লেখা হয়ে যায়, লেখাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘোরটা থাকেই! তাহলে কি একটা ঘোর কেটে গেল মানে একটা কবিতা শেষ হলো? আমার কাছে বিষয়গুলো এমনই মনে হয়। পিকাসোর একটা উক্তি আছে, ‘I don’t search, I find.’ পিকাসোর কথাটা মনে পড়লো। সম্ভবত অনুসন্ধানী মন অবচেতনে সর্বদাই অ্যাকটিভ থাকে, আর টুকে রাখে।
প্রশ্ন: কাব্যজীবনে আপনার ভেতরে চলমান সংগ্রাম ও সাংসারিক প্রভাব কতটা উপভোগ্য বা যন্ত্রণার?
উত্তর: এই সময়ে কবির সন্ন্যাস সংসার ত্যাগ করে নয়, সংসারে থেকেই। যিনি কবি, তিনি সমাজ-সংসারের চলমান কার্যক্রমের মধ্যেই কবি। পারিবারিক যন্ত্রণা নয়; বরং একভাবে বলা যায়—পরিবারের প্রভাবেই আমি অল্প বয়সে আউট বই পড়তে শুরু করি। কিছু তো ঝামেলা থাকেই। কিন্তু সেটা অন্যদের তুলনায় আমার অনেক কম। বরং যা কিছু যন্ত্রণার তার কারণ রাষ্ট্র ও সমাজ।
প্রশ্ন: এ সময়ে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের ধারা অনেকটাই নগরকেন্দ্রিক। অথবা বলা যায় ঢাকাকেন্দ্রিক। এখানে ঢাকা কেন্দ্র, আরা পুরো দেশ প্রান্ত। কবি-সাহিত্যিকদের যেন অনেকটা কেন্দ্রে এসে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে হয়। আপনি কুড়িগ্রামেই থাকেন। সেখানেই সাহিত্যচর্চার মধ্যে আছেন। বলা যায়, গতানুগতিক ধারায় আপনি প্রান্তের কবি। এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন? এটি কি আমাদের সাহিত্যমানের অবনমনকেই তুলে ধরে?
উত্তর: প্রথম দশকের গোড়ার দিকে ঢাকায় ছিলাম কয়েক বছর। তারপর চলে আসি কুড়িগ্রাম। তারপর থেকে আছি এখানেই। কয়েকবছর ঢাকায় থেকে আমার মনে হয়েছে, ঢাকায় থাকলে আমার অন্য সবই হয়—শুধু লেখাটা ছাড়া। দেখুন, শুধু ঢাকাই তো বাঙলাদেশ নয়, চৌষট্টি হাজার গ্রামই বাঙলাদেশ। কিন্তু শুধু সাহিত্য নয়, সকল সেক্টরেই আমাদের কেন্দ্র হয়ে গেছে ঢাকা। এর ফলে সকল সেক্টরই ক্ষতিগ্রস্ত। বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার।
আর সমস্যা বলে যা হয়েছে তা হলো, অনেকরকম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে কুড়িগ্রামে থাকার জন্য। দূরত্বটা ফ্যাক্ট হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু আমি এগুলো নিয়ে বিচলিত নই। কেননা, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ…
প্রশ্ন: লিটল ম্যাগাজিন সাধারণত প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে এক ধরনের প্রতিবাদ। বর্তমানে আমাদের দেশে লিটল ম্যাগাজিনের চর্চাকে কীভাবে দেখেন?
উত্তর: প্রথম দশকের (২০১০–২০২০) মধ্যবর্তী সময় থেকে বাঙলাদেশে কাগজে ছাপা লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা ভয়াবহ রকম কমে এসেছে। যেগুলো দৃশ্যমান, তার অধিকাংশই আসলে সাধারণ সাহিত্য পত্রিকা। এগুলো তেজহীন বৃদ্ধ ঘোড়া। ২০১৮ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় লিটলম্যাগ চত্বরে যখন বিন্দুর স্টল ভেঙে দিল বাংলা একাডেমি, তখন সেখানে উপস্থিত বাকি ১৬০টি লিটল ম্যাগাজিন, যাদের স্টল ছিল তারা কেউ প্রতিবাদও করেনি। তাদের কারো মনেই হয়নি লিটলম্যাগের স্টল ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদ করা দরকার! এই ঘটনা আমাদের জন্য নতুন উপলব্ধি তৈরি করেছে। বাঙলাদেশের লিটল ম্যাগাজিনগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করেছে। একসময় এ দেশে লিটলম্যাগের প্রধানতম কাজ ছিল দৈনিক পত্রিকার বিরোধিতা করা। অথচ লেখক কোথায় লিখবেন, না লিখবেন, এইটা সেকেন্ডারি ইস্যু। ফার্স্ট ইস্যু হচ্ছে লেখক কী লিখবেন, কীভাবে লিখবেন, কেন লিখবেন। কিন্তু এখানে হলো উল্টো। কোন কাগজে লিখবেন, এটাই হয়ে গেল প্রধানতম আলোচ্য। ফলে শিল্পকলায় আর শিল্প নাই, রইলো শুধুই কলা। তারই ফলাফল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। অবিকশিত এই মুভমেন্ট হাজামজাডোবা পুকুরে ডুবে রইল।
আরও দেখা গেল, সারাদেশের লিটলম্যাগগুলো—যারা সত্যিকার অর্থে চর্চাটা করেছিল, এখনো করছে; ঢাকাই লিটলম্যাগঅলারা এবং ঢাকার সাথে যুক্ত লিটলম্যাগঅলারা সেগুলোকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত করল দশকের পর দশক। এই চক্রান্তের অনেক নমুনা প্রকাশিত রয়েছে। আসলে এই সেক্টরও ভরে গেছে কালচারাল ক্রিমিনাল দিয়ে। এখানেও আওয়ামী লীগ আর বিএনপির দালালি চলছে সমানতালে। ফলে সাহিত্য নির্বাসিত, লিটলম্যাগ মুভমেন্ট বিপর্যস্ত। অবস্থা নির্মম, দুঃখজনক।
প্রশ্ন: আপনি ২০০৬ সাল থেকে লিটল ম্যাগাজিন ‘বিন্দু’ সম্পাদনা করছেন। বর্তমানে অনলাইন ও প্রিন্ট সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে বিন্দু। অনেক লিটলম্যাগ এর মধ্যে শুরু হয়েছে কিন্তু থেমে গেছে, আবার বিন্দু চলছে, এ বিষয়ে কিছু বলুন।
উত্তর: আমি বিন্দুর সম্পাদক হলেও বিন্দু আমার একার কাগজ নয়, আমাদের কাগজ; এর সাথে অনেকেই যুক্ত। সকলে মিলে আমরা এটি প্রকাশ করি। প্রথমে বিন্দু যে উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছিলাম তা হলো—আমাদের লিখবার কোনো জায়গা ছিল না। একটা জায়গা দরকার। এত বছর পরে এসেও মনে হয়, আজও কি আছে তেমন জায়গা, যেখানে আমরা হাত খুলে লিখতে পারি? বিন্দুর প্রয়োজনীয়তা আজও রয়েছে এজন্যই যে, আমরা আমাদের লেখাগুলো কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য যে কোনো শক্তির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই এখানে প্রকাশ করতে পারি। এখানে বলে রাখি, দিন দিন লেখক ও পাঠক উভয় দিক থেকেই পরিসর বাড়ছে। আর ওয়েবসাইট (bindumag.com) আরও আগেই দরকার ছিলো, নানা সীমাবদ্ধতায় তা করা হয়ে উঠেনি। ২০১৯ সালের ২৬ মার্চ থেকে অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ শুরু হয়েছে। এতে আরও অধিক লেখা প্রকাশের এবং পাঠকের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ হয়েছে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে সাহিত্য নিয়ে রাজনীতি বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই। বিশেষত লিটলম্যাগ নিয়ে।
সাম্য রাইয়ান: বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি আমাদের সবুজ ক্ষেত নষ্ট করে ফেলল। এদেশে বেশির ভাগ লিটলম্যাগ মানে বনসাই প্রকল্প। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী লোকজন এখানে সম্পাদনা করে, বুদ্ধিজীবী সাজে, কবিতা লেখে। সেই কবিতা নিয়ে যখন আপনি মন্তব্য করবেন তখনই বুঝতে পারবেন এদের সিন্ডিকেট কত গভীর। এদের হাতে আপনি মারও খেতে পারেন। আর অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, পয়সাঅলা কিংবা সুন্দরী নারীদের তাদের পয়সা কিংবা শরীরের বিনিময়ে কবি-লেখক বানানোরও অনেকগুলো সিন্ডিকেট এই দেশে আছে।
এই দেশে সাহিত্য নিয়ে রাজনীতি খুব নোংরা ও সংকীর্ণভাবে হয়। কবি বা লেখক হতে চাইলে এখানে কোনও না কোনও গোষ্ঠীর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয়! আপনি কত ভাল কবিতা লেখেন এখানে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আপনি কোন গোষ্ঠীর সাথে আছেন এটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি অধিকাংশ লিটলম্যাগও এখন আর লেখা দেখে না, লেখকের দালালি করার যোগ্যতা দেখে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে, বস্তাপঁচা কবিতা হোক সমস্যা নাই, কিন্তু গোলামিতে ঊনিশ-বিশ হলেই আপনি বাতিল। আর আছে গলাবাজি। হম্বিতম্বি। এই শব্দদূষণও সাহিত্যের ক্ষতি করছে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান দুরবস্থার পেছনের কারণগুলো কী?
উত্তর: বাঙলাদেশে আসলে প্রচলিত সংগঠনের যে ফর্ম, সেইটাই ফেইল করেছে। ফলশ্রুতিতে দেখবেন, প্রচলিত সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক সংগঠন, যাদের অবস্থা নব্বই দশকেও রমরমা ছিল, আজ তারা স্রেফ জান নিয়ে টিকে আছে। সংগঠনের ফর্মের পরিবর্তন দরকার। যে সম্ভাবনা আমরা দেখেছি গণজাগরণ মঞ্চের প্রথমদিকের সাংগঠনিক ফর্মে কিংবা আরও পরিণত ফর্ম দেখেছি নিরাপদ সড়কের দাবিতে কিশোর বিদ্রোহে। এই ফর্মেরই বিকাশ দরকার। আরেকটা বিষয় হলো—বর্তমান সংস্কৃতির সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চলন-বিচলনের বিস্তর ফারাক। আমাদের দেশে একটা কালচারাল রেনেসাঁ দরকার। কিন্তু সংস্কৃতির ভাঙা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়; এর জন্য সংস্কৃতির নয়া সেতু গড়তে হবে। নেই অন্য কোনো সহজ বিকল্প।
প্রশ্ন: লেখালিখির সাথে আপনি একজন অ্যাকটিভিস্টও বটে, এই দুটো পাশাপাশি চলতে অসুবিধে হয় না?
উত্তর: বর্তমান সময়ে ক্যাপিটালিজমের বহুমুখী আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে একজন মেরুদণ্ডসম্পন্ন লেখককে শুধু নিজের লেখাটি লিখলেই চলে না। সেই লেখা প্রকাশে অ্যাকটিভিস্টের ভূমিকায়ও নামতে হয়। সময় বদলেছে। বদলাচ্ছে। আরও বদলাবে। আক্রমণের রূপ বদলাচ্ছে। আপনাকে শুধু ভাত-কাপড়ে মারবে না এখন। আরও নানান কৌশলে মারবে। আপনি হাঁটা-চলা করবেন, লম্ফঝম্ফ করবেন, কিন্তু বেঁচে থাকবেন না। প্রতিষ্ঠান-পাওয়ার এর পক্ষের লোকজন নানা রূপে আপনাকে ভেতর থেকে মেরে ফেলবে। আপনাকে অস্থির-অশান্ত করে তুলবে, জীবন অসহ্য করে তুলবে। এমনকি তারা লিটলম্যাগের বেশে হাজির হয়েও এটা করবে। এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকা মানে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। যা করতে হবে তা হলো—নিজের লেখাটা লিখে যেতে হবে, তা প্রকাশ করার জন্য লিটলম্যাগ জারি রাখতে হবে। লেখাটাই আসল কথা। এটাই সব ষড়যন্ত্রের মোক্ষম জবাব। লেখকের ব্রহ্মাস্ত্র। এটাই লেখকের প্রধানতম অ্যাকটিভিজম। লেখকজীবনের প্রধান কথা।
প্রশ্ন: জীবন নিয়ে আপনার ভাবনা…
উত্তর: কবিকে আমার কেবলই মনে হয়—জীবনব্যাপী সম্পর্কশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করে চলা ব্যক্তি। সে নানান সম্পর্ক—প্রাণের সাথে প্রাণের, প্রাণের সাথে প্রাণহীনের, ক্ষুদ্রপ্রাণের সাথে মহাপ্রাণের—সকল সম্পর্ক। এই প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন-রক্ষা-চ্ছেদ-বিকাশ বিষয়েই মনে হয় জীবনের সকল গবেষণা। সেই সম্পর্কশাস্ত্রেরই আরেক নাম প্রেম। যা বেঁচে থাকার আনন্দ-বেদনা এবং অনুপ্রেরণা। তাই তো চোখের ভেতরে একটা হামিংবার্ড নিয়ে বসে আছি…
১৫ ডিসেম্বর ২০২২
=================
পাঠকের মস্তিষ্কে উস্কে দেয় সাম্য রাইয়ানের কবিতাঅমিতাভ অরণ্য “অনন্ত ঘুমের ভেতরে আমি ঢুকে গেলাম, অসামান্য প্রেমের চোরাস্রোতে;বিলুপ্ত জীবাশ্মের বুকের পরে বসে,ধুসর অন্ধকারে দেখা হলো তোমার সাথে…” ‘মৃত্যুপূর্ব গান’ ভারী হয়ে আসে নিপুণ শব্দখেলায় সাজানো উপক্রমণিকায়। তারপর ইতস্তত ভেসে বেড়ায় কিছু বিক্ষিপ্ত দৃশ্য। যে দৃশ্য উঠে আসে চেতনার অতীত থেকে, যে দৃশ্য ডিল্যুসিভ দ্যোতনায় দুলিয়ে দেয় মনকে। কি বলতে চাইছেন কবি? কি বুঝছেন পাঠক? খানিক দ্বন্দ্বে ভুগি— তারপর হাঁটি স্বতন্ত্র পাঠে। তখন কবিতা হয়ে ওঠে নিজস্ব। বলছিলাম কবি সাম্য রাইয়ানের ‘মার্কস যদি জানতেন’ কাব্যগ্রন্থটির কথা। চোদ্দটি কবিতায় গোছানো বাঙ্ময় থেকে প্রকাশিত ষোল পৃষ্ঠার বইটির আনাচ-কানাচে কি যেন এক অবগুণ্ঠিত সুর গুনগুন করছে; অনভ্যস্ত কানে কিছুটা গুঞ্জরিত হয়— বাকিটা অব্যক্ত। তবু মোহময় আকর্ষণে ছুটতে থাকি আরো সামনে- কালো অক্ষর ভেদ করে। “কোনো চিহ্ন রাখবেন না ম্যাডামএটা দাস ক্যাপিটালের যুগঘরে ঘরে মার্ক্স ঢুকে যাবে…” ‘ম্যাডামের দেশে’ শীর্ষক কবিতায় সতর্কবাণী জারি করেন কবি। মার্কস আসার আগেই যেন প্রতিশ্রুতির ডালিতে পূর্ণ হয়ে যায় জনতার জীবন। অথবা ম্যাডামের দেশে হয়তো প্রতিনিয়ত এমনটাই হচ্ছে। পড়তে পড়তে ম্যাডামকে কি বড্ড চেনা চেনা লাগে? “এই যে চায়ের দোকান। খুব পরিচিত দেখা হলে কথা হয়। চলে গেলে ওইচেয়ারে টেবিলে অন্য কুটুম বসে।” ‘সোসাইটির চাকার নিচে’— যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, তা যেন সংসারে আদিমতম প্রবৃত্তি। মানুষ চলে যায়, মানুষ আসে। ভিন্ন মানুষ হয়ে বারবার আসে। এ তো মহাকালের অমোঘ নিয়ম। তার কোনো ব্যাত্যয় নেই। শুকনো পাতারা ঝরে পড়ার কালে মাঝপথে হাওয়া লেগে আবারো উড়ে গ্যাছে অন্য পথে, ভিন্ন গতিতে;মৃত্যুর মতো বদলে গেছে তারা প্রভিন্ন আঙ্গিকে… পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৃশ্যপট; কবির কনটেক্সট আর পাঠকের কনটেক্সট কি সর্বদা এক হয়? কবি যে ছবি আঁকেন, পাঠকের অন্তর হয়তো খুঁজে নেয় তার চেয়ে ভিন্ন কিছু। সাম্য রাইয়ানের পঙক্তিগুলোও এমন বিভ্রান্তিময়- কখনো সংশয়-পাখি উড়ে যায় আকাশ-সীমান্তে, কখনো ভেসে আসে সিরাজ শিকদারের ক্ষীণ স্পষ্ট আওয়াজ, কখনো বা আত্মপরিচয়ের খোজে নামেন কবি। তিনি কি মানুষ? নাকি না-মানুষ? বিভ্রান্তির দোলাচলে কবি ঘোষণা দেন— “কে বললো আমি মানুষ! আমি তো মানুষ নই। কেবল মানুষের মতো দেখতে।” অসংখ্য আপাত বিসদৃশ দৃশ্যপট জোড়া দেওয়া; হয়তো তার অন্তর্নিহিত অন্য কোনো অর্থ আছে, হয়তো নেই… কখনো তা দুর্বোধ্য, কখনো বা অগম্যও। ঠোকর খেয়ে ফিরে আসতে হয় দরজা থেকে। আধুনিক কাব্যজগতে মনে হয় কবির দায়িত্ব ‘লেখা’ পর্যন্তই; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কবিতা-বান্ধব, পাঠক-বান্ধব নয়। কবিতা পড়তে গেলে মস্তিষ্কের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রতিটা কবিতা পড়তে গেলে যদি আলাদা থিসিস করে নিতে হয় তার উপর, তাহলে পাঠক কাব্যবিমুখ হবেই। সাম্য রাইয়ানের কবিতা সে দায় থেকে মুক্ত না হলেও, তার কবিতায় মুক্ত আকাশ নেহাত কম নয়। তাই হাঁপিয়ে গেলে সেখানে ডানা মেলে দেওয়া যায়। তার কবিতা তাই পাঠক নিজের মনে দৃশ্যায়িত করে নেয়। সাম্য রাইয়ানের কবিতা পাঠকের মস্তিষ্কে উসকে দেয় কোনো এক একান্ত অনুভূতি। মার্কস যদি জানতেনএক ফর্মার কবিতার বইবইটি গণঅর্থায়নে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্ময় থেকে প্রকাশিতবিনিময় তিরিশ টাকা চোখের ভেতরে হামিংবার্ড: চিত্রকল্পের গুনগুন শব্দশামীমফারুক কবি সাম্য রাইয়ানের ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ বইটাতে একটা দৃষ্টির গুনগুন শব্দ পেলাম। সোনামুখী একটা সুইয়ের কাজ দিয়ে বইটা শুরু। প্রথম কয়েকটা কবিতা পড়লেই টের পাওয়া যাবে প্রকৃতি, স্মৃতি, আর অনুভুতি কীভাবে জড়াজড়ি করে থাকে। কোথাও ইমেজ, কোথাও ঘোর, ভাঙ্গা গল্পের টুকরা আর ভরপুর আবেগ। “ফড়িং নয় ধরতে চেয়েছে ফড়িং এর প্রেম” —এ থেকে তার কবিতায় বস্তু ও ভাবের ধারনা টের পেলাম। ‘বিচ্ছেদ’ কবিতায় দেখলাম “পাশে অন্ধ শামুক সোরগোল তুলে নেশাগ্রস্ত সংসারে ডুকে যাচ্ছে হামিং বার্ড কবিতা টায় একটা শক্তিশালী ইমেজ পেলাম – “হাতের তালুতে বয়ে যাবে ঢোরা সাপ, রক্তের ধারা৷” আবার বলছে “মনের ভেতর আছে প্রাকৃত শরীর যাকে কখনো জানা হয় নাই।” এভাবে ওঁর কবিতা ঘুমন্ত মার্বেলের মত গড়িয়ে যাচ্ছে বইটায়। ‘জীবনপুরাণ’ কবিতাটা বেশ ভালো লাগলো। শক্তিশালী কবিতা৷ জানলাম কবে থেকে কবি হৃদয়কে সম্মান করেন। ‘কুড়িগ্রাম’ কবিতাটায় ওভাবে নতুনভাবে কুড়িগ্রামকে সংজ্ঞা দেয়াটা ভালো লেগেছে– “বেহিসেবী ঘুমন্ত মেয়ে তীব্র কুড়িগ্রাম৷” “গাছটা অসুস্থ, ওকে ডাক্তার দেখাবো” এরকম আরও অনেক সহজ করে বলা লাইন আছে। তবে মাঝে মাঝে একটা বেশি কাব্যময় করার চাপ আছে কোথাও কোথাও, যা ভাল লাগেনি। ভালো লেগেছে “আন্তঃনগর প্রেম”, সবশেষের কবিতাটা “বানান বিভ্রাট” –কেন জোনাকি আশা জাগায় না, ব্যথা ভোগায় না। এরকম জোনাকিতে কি সাম্য করোনা খুঁজে পাবে এখন? (শামীমফারুক, গৃহবন্দী করোনা দুঃসময়, ঢাকা, ৭ মে ২০২০) বই সম্পর্কে তথ্যঃনামঃ চোখের ভেতরে হামিং বার্ডধরণঃ কবিতাপৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ৬৪ | প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০২০প্রচ্ছদশিল্পীঃ শামীম আরেফিনপ্রকাশকঃ ঘাসফুল রোমান্টিসিজম, কোনো এক উচ্চতর বিন্দুতে পৌঁছে সাম্য রাইয়ানকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছেবিপুল বিশ্বাশ “মিছা কথা কইও না, আমার শীত করে”(চূড়া)আরে কয় কী! এই কথাডা কই পাইলো এই কবি! এ যেন গাবের আঠার মতো টানিয়া রাখিতেছে। নিজস্ব দেহের ভিতর নিজস্ব মনকে একাকার করিয়া কবি নিজেকে যে নিজের ভিতর হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা পরিষ্কার। এ তো অল্প বয়সী ফুড়ফুড়ে পুরোমাত্রার এক রোমান্টিক কবি। তিনি নিজেই তো স্বগতোক্তি করিয়াছেন— “জুলাইয়ের কোনো এক সকালেআমি জন্ম নিলাম শব্দ থেকেআর সামনে উন্মোচিত হলপৃথিবীর প্রবেশদ্বার”।(তোমাকে) জন্ম, জন্মদিন, জন্মান্তর এগুলোতে সবারই আলাদা আলাদা গল্প থাকে— হাসির, কান্নার, কষ্টের। প্রতিটা দিনই তো আমাদের এক একটি ব্যক্তিগত ইতিহাস। আমাদের পায়ের বৃত্তচাপের সাথে জমা হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বৃত্তচাপ। তখন কিছুই ভালো লাগে না। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই। কবিরও— “কিছুই ভাল্লাগছে না আজকাল, অগণিতমিথ্যে সংবাদপত্র, বাহারি চোখ-মুখআলোর জৌলুশ, সিরামিক সোসাইটি”(বোধিদ্রুম) ভালো না লাগা শুরু হইলে মানুষ দুই জায়গায় যায়— তার প্রিয় মানুষের কাছে অথবা ঈশ্বরের কাছে। আর যখন সে তাহার প্রিয় মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পায়, তাহার মতো আনন্দের কিছু নাই। কিন্তু এই চাওয়া তো সবসময় নিজের মনের মতো করে মেলে না। নিজের সব কিছু উজাড় করিয়া বলিবার জন্যে যাহার কাছে ছুটিয়া আসা তাহার কাছে যে সেই জিনিস আর নাই। কবি তাই বলেন—“আমার ঈশ্বর তুমি, ভেতরে সবুজাভ পাট; অথচ আশ্চর্য, তোমারই হৃদয়ে ঘটে বানানবিভ্রাট!”(বানানবিভ্রাট) কবি বুঝিতে পারেন এই সবের সূত্রমুখ অন্য কোথাও আছে, অন্য কোনো মানুষের ভিতর। যদিও সব মানুষ এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন। সবার মুখ অচেনা, যেন দ্যাখাই হয়নি কোনদিন। যে মুখ তিনি চিনিতেন, সেখানে অন্য মুখ লাগানো, এভাবে— “মানুষই হরণ করেছে মানুষের সুখ৷আহা জীবন কী বিচ্ছিন্নতাপরায়ণ!তীব্র স্বরে ডেকে যায় নিঃসঙ্গ শালিক৷”(জীবনপুরাণ) এরপর আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হয় মানুষ। আরো বেশি দূরবর্তী হয়। একই গ্রহে থাকিয়াও সে যেন গ্রহান্তরের মানুষ। এই তো চারিপাশের শিশুরা হাসিতেছিল অথচ তাহারাই আবার কাঁদিতেছে— “কোথায় সে গ্রহ, এতো হাসির শব্দ আসে!আমার শিশুরা কাঁদছে; এদের ঘুম ভেঙে গেছে৷”(ক্রোধ) কবি বা আমরা এই সব ভুলিয়া যাইতে চাই। আর যাহা কিছু ভুলিয়া যাই তাহাও তো এক ধরণের স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে থাকে ছোট্টবেলা, ডাকঘর, আর প্রিয়তম মানুষ। কবি ভুলে যেতে চান— “ভুলে যেতে চাই হারিয়ে যাওয়া ডাকবাক্সের স্মৃতি; আর সেই নীল-জামামাতাল তরুণীর কথা৷”(গভীর স্বপ্নের ভেতর) অল্পবয়সী ফুড়ফুড়ে এই রোমান্টিক কবির রোমান্টিসিজম, কোনো এক উচ্চতর বিন্দুতে পৌঁছে কবিকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছে, যাহাতে তিনি সব পরিস্কার দেখিতে পান। তিনি যেন একটু বেশিই দ্যাখেন। এ এক অন্যরকম দ্যাখা। ‘ডানা ও ব্যাধ’ কবিতায় তিনি তাহার দৃষ্টির প্রসারতা এইভাবে ছড়াইয়া ও আবদ্ধ রাখিয়াছেন— “ছায়ার ডানায় বেঁধে ব্যাধের উচ্ছ্বাসক্ষুব্ধ ধ্বনির সাথে হেসে উঠছে─হেলে পড়ছে স্বরবৃত্তের মেঘ। ঘুম ওজাগরণের মধ্যখানে তোমার এলোচুলছাড়া কোনো বিভেদরেখা নাই। আলোরমুহূর্তে শুধু জীবন্ত হচ্ছে চুল; এতোগুলোগোসলের পর কী সুদূর রেখা বেয়েভেসে উঠছে হারিয়ে ফেলা জামার বোতাম।”(ডানা ও ব্যাধ) নিজস্ব ঘরানার চৌকাঠে এই কবির এক পা দেয়াই আছে, অন্য পা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি জানিয়া গেছেন ঘরের বাহিরে তাহার চারণভূমি, সেখানে আরো অনেকেই তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। তিনিও পারেন সেখানে অন্য সব কবিদের সাথে একসাথে আড্ডায় মাতিয়া উঠিতে। আর সেই আড্ডায় কোনো কবি তাহার নিজের পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলে, কবি সাম্য রাইয়ানও তাহার নিজের পকেট হইতে আগুন বাহির করিয়া স্মিতহাস্যে সেই সিগারেট ধরাইয়া দিতে পারিবেন, নিঃসন্দেহে। চোখের ভেতরে হামিংবার্ড নিয়ে আমি যা ভাবছিহোসাইন মাইকেল প্রত্যহ ১২ টা বেজে গেলে যখন আমার সকাল হয়, অভ্যাসমত প্রার্থনা সেরে শয্যা ত্যাগ করি। প্রার্থনা বলতে আমি চিৎ-শোয়া অবস্থায় তাজবিদ মেনে, ঠিকঠাক মাখরাজ আদায় করে জোরেসোরে কোনো একটি বিশেষ কবিতার পাঠকেই বুঝি। বিশেষ কবিতা হলো— যে কবিতার শরীরে লাল-নীল বিবিধ রঙিন দাগ লেগে যায়, আমার আঙুল-স্পর্শে শিহরিত হয় যে কবিতা কিম্বা যে কবিতার প্রত্যেক অক্ষর হস্তান্তর করতে থাকে আমাকে, আর আমি অধিচিন্তায় প্রবাহিত হতে থাকি, মূলত আমাকে বিরাজ করতে হয় ওইসব অক্ষরে অক্ষরে। এরকম একটি কবিতার নাম হলো— ‘উড়ন্ত কফিন’। অতি আবেগী বাচ্চাদের মতো বলতে ইচ্ছে করছে— ‘উড়ন্ত কফিন’ আমারই লিখবার কথা ছিল, দেরি হওয়ায় সাম্য রাইয়ান নামের এক হিতৈষী কবি সেটি লিখে ফেলেছেন, অথবা ‘উড়ন্ত কফিন’ আমি প্রার্থনায় পাঠ করবো বলেই লেখা। ‘চোখের ভেতরে হামিং বার্ড’ না হয়ে বইটির নাম ‘উড়ন্ত কফিন’ হতে পারতো, হলো না কেন?! হলো না বোধয় ‘জীবনপুরাণ’ নামক কবিতাটির জন্য। যেটি মধ্যরাতে ইশারায় ডাকে, শূন্যতা আর আত্মহননের কথা শোনায়, আমাকে নিমেষেই বানিয়ে ফেলে একটা দূরন্ত লাটিম — আমি জেনেও না জানি ‘ধর্মের সীমানা আছে, মানুষ অসীম’। বইটির নাম ‘জীবণপুরাণ’ও হতে পারতো। হতে পারতো ‘বানানবিভ্রাট’ অথবা ‘বোধিদ্রুম’। এই একেকটি কবিতায় যেন বিশ্ব ধরা পড়ে৷ মূলত আমি একটা ধা—য় ভুগছি, ধা—টির নাম ‘দ্বিধা’। বইয়ের ৪৮টি কবিতা পাঠ করার পর ভাবছি মাথার ভেতরে ‘ট্রাফিক জ্যাম’ লেগে আছে কিনা! ৪৮টি কবিতাই কেমন আটকে আছে মাথার ভেতর, মস্তিষ্কের অসীম সীমানা পেরুতেই পারছে না, প্রত্যেকটিই যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে নিজস্ব স্থিরতায়! আমার ভেতরকার সত্ত্বা একবার এর কাছে যাচ্ছে— একবার ওর কাছে যাচ্ছে। বিবেচনা করছি, সব ক’টি কবিতাই কবিকে তীক্ষ্ণমান দাবি করার যোগ্যতা রাখে। চলুন ধরে নিই, সবগুলো কবিতাই একেকটি হামিংবার্ড। অতঃপর কবিতাগুলো পাঠ করি চলুন, আর দেখি তো চোখের ভেতরে সেসব খেলা করে কিনা, কিম্বা মাথার ভেতরে!সাম্য রাইয়ান আশ্চর্য এক পংক্তি লিখেছেন, যা আমাদেরই স্বরূপ উন্মোচন করে—“আদিগন্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আসলে কিছুই শিখিনি আমরা”
কবি সাম্য রাইয়ান: আলো আঁধারের
ধীমান ব্রহ্মচারী
(১)
মৃত্যুপূর্ব গান
অনন্ত ঘুমের ভেতরে আমি ঢুকে গে
— স্পর্শশীল প্রজাপতি জানে না কা
— হারানো পরীর ডানা খুলে রাখো জ
— গুটিকয় ঢেউ কী প্রকারে ভারি
— জীর্ণ নীলের ভিতরে প্রলয়, শা
— অনির্দিষ্ট জনের দিকে কিছু্ মৃত্যু ছুঁড়ে দিও সত্যিকারের ফুল
— অবাক বনসাই তোমাকে ধারণ করেছে
— তিনটে বাজে মৌ, শীতরাত্রি আজ,
— তামাক ফুলের বাগান ছিলো অন্তি
— শান্ত একটা কোলাহল ছেয়ে যাচ্
— মুছে যেতে যেতে মৃদু হাসি হয়ে ঝুলে আছো উত্তাল হাওয়াঘর।
— কমলার জ্যান্ত জোঁক উদ্বেলিত
— ঈষৎ কাৎ হয়ে থাকা মৌনতা মেলে
— সামান্য প্রেমের দিকেই ধাবিত
— তারকার তরঙ্গরাশি থেকে চাপা আ
— অবাক, অবাক হও; দ্বিধাহীন ঢে
— মাঝে মাঝে এক-দুইটা মধ্যরাত দে
— ভাসমান বাঈজীর হৃদয়ে নিষ্ফল
— তুমি দ্যাখো নাই ওইখানে, নি
কবি সাম্য রাইয়ান-এর কবিতার স্বরূপ সন্ধানে
শামীম সৈকত
যে হৃদয়াবেগের সাথে শানিত বুদ্ধির সমন্বয়ে অসামান্য সুখপাঠ্য গদ্য ও সমকালীন বাংলা কবিতায় বিচরণ করে, যে সর্বদা নিজের সৃষ্টির বিষয়ে ভীষণরকম নির্মোহ থেকে সমকালের স্পন্দন আর অন্তরটাই শোনাতে চায়, যে ‘বিন্দু’ ছোট কাগজের মধ্য দিয়ে নতুন এক পথের গল্প শোনায়; সে কবি সাম্য রাইয়ান।
যার কবিতার ঝরঝরে আনুষঙ্গিক শব্দের ধূপকাঠি প্রোজ্জ্বল হয় পাঠকের মনে। পাঠক ঘোরের ভেতর খোঁজে অন্য স্বরের অন্যরকম ঘোর। খুঁজে পায় ধরলার শীতল জলে জেগে ওঠার তীব্র অনুভব। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের আনাচেকানাচে ঘোরে তার শব্দতীর; খুঁজতে থাকে আলোর মশাল। যা আমাদের মগজে গেঁথে দেয় অস্থির বাস্তবতার প্রশ্ন। ‘আদিম শ্রমিক আমি মেশিন চালাই / মেশিনে লুকানো পুঁজির জ্বীন/ চালাতে চালাতে দেখি আমিই মেশিন’।
সাম্য রাইয়ানের সমগ্র কাব্যগ্রন্থগুলো পাঠ করলে মনে হয়, যাপিত জীবনের আধখোলা চোখ নিয়ে অপরূপ বর্ণনায় তুলে আনে শীতল দ্রোহ। প্রস্ফুটিত হয় সাদামাটা চিরচেনা প্রেক্ষাপট। অথচ বুননে কী গোপন প্রেমের ধোঁয়াশার জাল! যদিও ভাবের উপমা, অলংকরণ, চিত্রকল্পে নেই কোনো জটিলতা। জন্মস্থান কুড়িগ্রাম নিয়ে দুটো পঙ্ক্তি যার প্রকৃত উদাহরণ। ‘অগণন সম্পদশালী — আরো উচ্চ দাম/ বেহিসেবি ঘুমন্ত মেয়ে — তীব্র কুড়িগ্রাম’
কবি সাম্য রাইয়ানের কিছু কবিতায় হাইকু’র ঢঙও মিশে আছে। ‘চমকে দিও না তাথৈ, উড়ে যাবে’ এর মতো এ কার অবয়ব? তাথৈ; মানব কিংবা মানবীর মতো দেখতে লুকিয়ে থাকা এ কোন মানব/মানবী? পরিচয় তুলে রেখে পা বাড়াই আরো গহিন বনে। যেখানে উড়ে হামিংবার্ড।
কবি তার কবিতা কিংবা গদ্যের প্রতি দায় রাখতে গিয়ে বলে তার সময়ের কথা। এরই দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রতিটি অক্ষর জড়ো হয়ে ছুঁড়ে দেয় শব্দবুলেট। আমি মনে করি, জোরালো ও দৃঢ় বক্তব্যের মাধ্যমে কবিত্বের নিজস্ব সত্তা ঘোষণায় সাম্য রাইয়ান সফল। তাঁর এই সফলতার ধারাবাহিকতার স্বরূপ ঘোষণা হয়- ‘যদি অব্যাহত বেঁচে থাকি/ শ্বাস নিই গ্যালন গ্যালন;/ প্রতিটি রক্তফোঁটা থেকে শব্দ জন্মাবে আর/ গহিন থেকে বেরুবে নির্ভীক সিরাজ সিকদার।’
বাংলাদেশের একটা ছোট্ট গ্রাম; কুড়িগ্রাম। এখানেই বেড়ে ওঠা তার। সাম্য রাইয়ান এই ছোট গ্রাম থেকে বৈশ্বিক সত্য ও ন্যায়ের মলিন প্রচ্ছদে ঢাকা আলো ও অন্ধকারের পার্থক্যকে বুঝে তার জীবন দর্শনে বেছে নিয়েছে বাস্তবতার হেমলক। তার এই লোকাল ট্রেনের জার্নি আমাকে অভিভূত করে। কবি, তোমার পৃথিবীর গাড়িটি থামাও; আমি নেমে যাই।
লোকাল ট্রেনের জার্নালঃ সাম্য রাইয়ানের অশেষ যাত্রার পথ
তানজিন তামান্না স্বপ্ন আর না বলা কথায় ছুটতে ছুটতে গুডবাই ভর্তি ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়তে হবে সাম্য রাইয়ানের লোকাল ট্রেনে… ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ বইয়ের প্রত্যেকটা গদ্যে ‘একটি সত্য’ জানতে চাওয়ার জানলা খুলে যেতে থাকবে ট্রেনের ছন্দে ছন্দে। আর এই ছন্দে দুলতে দুলতে পৌঁছে গেলাম কী হৃদপিণ্ডের সাইলেন্সে? লোকাল ট্রেনের জার্নালেই উদিত হবে বেঁচে ওঠার সূর্য। দৃশ্যত হবে: ‘প্রকাণ্ড এক ঋতুর ছায়া’। “আর আমার ঘরে দুনিয়াদারি নিলামে তুলে ‘পাখি সব করে রব’। এই কোলাহল জটলা পাকায়, তবু দূরের বন্ধনী থেকে কিছুটা ঘ্রাণ- হালকা-। প্রকাণ্ড এক ঋতুর ছায়ায় বেড়ে উঠছে।” [ গদ্য: দুলে ওঠে তোমার প্রদীপ] “ঘুম থেকে উঠি আর ভুলে যাই এখন মধ্যরাত কী দুপুর ! পাজেল মেলে না আমার। ওহ্ পাজেল- ওহ-! তারও কি সূত্র ভুলে গেছি ?” [ গদ্য: বিদীর্ণ আলোর ধারা] গদ্যগুলোতে আহ্বান আছে, আছে জার্নির বিস্ময়— ভাবনা এবং ভাবনায় উঠে আসা যাপিত রাত্রির ঘুমের দ্বন্দ্ব অথবা অন্তর-দ্বন্দ্ব। ভুলে যাওয়া সূত্র মেলাতে গিয়ে মিলে যাবে কোনো কোনো স্বপ্ন। স্বপ্নের ভেতর দ্যাখা যাবে— কোনো এক জমে যাওয়া প্রেম। প্রেম জমে গেলে মনে হতেই পারে “এ কী হলো আমার?” স্বপ্নের ভেতর প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারা ‘তুমি’। “তোমার চুলগুলো উড়ছে। উড়ছে প্রজাপতি আর মৃদু জলের বুদবুদ জমছে দুরুদুরু বুকে। কীরকম না? আর তুমি হাসছো! অথবা তাকিয়ে দেখছো সব, জলবৎ তরলং। অথবা চিৎকার করে বলছো, ‘সিগারেট কমাতে হবে’। [ গদ্য: একটা সত্যি কথা বলো] ‘তোমাকে’ প্রকাশ করতে করতে তুমুল অন্ধকারে ডেকে উঠবে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা। প্রচণ্ড নীরবে খসে পড়তে থাকবে রাত্রির এক একটি কাঠামো। ট্রেনের অপেক্ষায় কবি রাত পার করতে থাকবেন এক একটি নৈঃশব্দকে জন্ম দিতে দিতে। পুরো পৃথিবীর হলুদ রঙ নিয়ে তারা হেঁটে আসবে কি দৃশ্যের কাছাকাছি? হাঁটতে হাঁটতে পথ ক্লান্ত হয়ে পড়লে গেয়ে উঠবে জীবনবোধের গান। “দৃশ্যমান সকল কিছুই সত্য নয়, কখনো অদৃশ্যমান অনেক কিছুই সত্য প্রমাণিত হয়।”[গদ্য: হাঁটতে হাঁটতে পথ গ্যাছে ক্লান্ত হয়ে] ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ পড়তে পড়তে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি— নিজস্ব আঁধারের কাছে। এই দাঁড়ানোতে নেই কোনো উদ্দেশ্য! এখানে কোনো ঘ্রাণ ভেসে আসলে চোখ বন্ধ করি— পাখিরা ডেকে ওঠে! প্রকাশিত হয়ে যায়— নিঃসঙ্গ আকাশ! “এইসব বিচ্ছিরি বোধের দেশে নিজের ভেতর নিজেই গুটিয়ে থাকে নিঃসঙ্গ আকাশ। আর জীবন এতোটাই প্রাণহীন যে, টোলখাওয়া চেহারায় আঁধারে দাঁড়িয়ে লাভ নেই।”[গদ্য:টোলখাওয়া চেহারায় আঁধারে দাঁড়িয়ে লাভ নেই] এবার ফিরে আসা যাবে স্বপ্নের কাছাকাছি! লোকাল ট্রেনে ভেসে আসবে— নদীর নিজস্ব ঘ্রাণ। কবিতার পূর্ণ-দেহ নিয়ে জেগে উঠবে নদীর তীর। ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ এ উঠে আসতে থাকবে গভীর এক শব্দপ্রবাহ— প্রস্ফুটিত আত্মহন্তারক! “হাহাকার জমা আছে মনে। কতোটা চাই, ফিরে পেতে। পাওয়া হয় না। কতো স্মৃতি জমিয়ে রেখেছি মায়াপাশে। এই বৃথাবাক্সে জমিয়ে রাখা স্মৃতিচিহ্ন।” [গদ্য: কবিতার পূর্ণদেহে নদীর নিজস্ব ঘ্রাণ] ‘রাত্রি একটা অনাহুত বেদনার নাম’— গদ্যটি পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম! “ঘুম ভেঙে গেলে বুঝি কান্না পায়! না হলে জন্মক্ষণে তুমি কেঁদেছিলে কেনো?”— এই প্রশ্নে আমি থেমে থাকলাম দীর্ঘক্ষণ একটা সুমধুর ভাবনা নিয়ে। ঘুমের এতো সত্য প্রকাশ আর কোথাও দেখা হয় নাই! প্রশ্নের এতো স্বচ্ছতা লোকাল ট্রেনের জার্নালের প্রত্যেকটা গদ্যে সুতীব্র বিদ্ধ করবে সবাইকে। আর সুতীব্র উত্তরও বুনে দেয়া আছে গদ্যগুলোর ভেতরেই। “আকাশ দেখে আশ্চর্য হওয়া মানুষের অনিবার্য কর্ম নাকি! আদি থেকেই মানুষ আকাশ নিয়ে গভীর মগ্নতায় দিন কাটিয়েছে। চর্যাপদেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু কি আকাশ-নীল?” [গদ্য: শাদা অন্ধকারে অন্য মন্ত্র] লোকাল ট্রেনের জার্নাল— এই জার্নির কোনো শেষ নেই, ক্লান্তি নেই! শুধু এক রহস্যে ঘেরা স্বচ্ছতা খুব নীরবে বয়ে যাচ্ছে … দূর থেকে সন্নিকটবর্তী দূরে দেখা যাচ্ছে রহস্যের আড়ালে আরো আরো রহস্য! আর শেষ পর্যন্ত ‘পৃথিবী খুব একটা মজার জায়গা না’— এই সত্য ভালো লাগার জন্ম দিচ্ছে— উস্কে দিচ্ছে জিজ্ঞাসা… প্রথম থেকে যাত্রা শুরু করার পিছুটানের জন্ম দিচ্ছে লোকাল ট্রেন। =**=**=**=**=গদ্যগ্রন্থ: লোকাল ট্রেনের জার্নাল । লেখক: সাম্য রাইয়ান । প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০২১ ।প্রকাশনা: ঘাসফুল, ঢাকা, বাংলাদেশ । প্রকাশক: মাহ্দী আনাম । প্রচ্ছদ: রাজীব দত্ত । মূল্য: ১৬০ টাকা ।
রহস্য ও বৈচিত্রে ভরা সাম্য রাইয়ানের উৎসর্গপত্রের জগৎ
ড. সুশান্ত চৌধুরী ১৯০৮ সালে খুলনার সেনহাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের (বর্তমান দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটী গ্রাম) শিক্ষক ও কবি হীরালাল সেনের কবিতার বই ‘হুঙ্কার’ প্রকাশ পায়। দেশ তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। আর সেই স্বপ্ন জ্বেলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বইটি হীরালাল সেন উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে৷ সেই উৎসর্গের জেরে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল বিশ্বকবিকেও! সেই মামলায় রাজসাক্ষী নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্তত আদালতের রেকর্ড তাই বলে। ছোটলাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের মতলব ছিল রবীন্দ্রনাথকেও কাঠগড়ায় তোলা। আদালতে উপস্থিত বৃদ্ধ উকিল কালিপদ রায় জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণের পক্ষে উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তার পেশা নয়, সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই। সেই মামলায় আসামীকে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অবশ্য কখনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু পুলিশের সন্দেহভাজনের তালিকায় তাঁর নাম ছিল। লালবাজারের খাতায় তাঁর পরিচয় ছিল, ‘Robi Tagore, I. B. Suspect Number 11’। শোনা যায় জোড়াসাঁকো থেকে কবি রাস্তায় পা দিলেই গুপ্তচর মারফত খবর পৌঁছে যেত হেড-অফিসে। উৎসর্গপত্রের জন্য এমন আজব ভোগান্তি সত্যিই বিরল। বই উৎসর্গ মানেই যে বিড়ম্বনা তা কিন্তু নয়৷ এটি ব্যতিক্রম ঘটনা৷ একটি বইয়ের উৎসর্গপত্র কী? এপ্রসঙ্গে অনির্বাণ রায় তাঁর ‘উৎসর্গপত্র’ বইয়ে লিখেছেন, “উৎসর্গপত্র বইয়ের অঙ্গ। এক থেকে একাধিক ছত্রে তার আয়তন-বিস্তৃতি। এতে ধরা থাকে একটা বিশেষ কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিভঙ্গি, মর্জিমেজাজ, সমাজসময়ের ধূসর ছবি, ইতিহাসের টুকরো, জীবনের ভগ্নাংশ— এমন কত কিছু।’’ এবার আসি বই উৎসর্গের খানিক গোড়ার কথায়৷ প্রাচীন ও মধ্যযুগেও বই উৎসর্গের চল ছিল বলে প্রমাণ মেলে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে এথেন্সবাসী গ্রিক রাজনীতিক অ্যারিস্টাইডিস নাকি বলেছিলেন, ‘উপাসনালয় উৎসর্গিত হয় দেবতার উদ্দেশে আর বই উৎসর্গ করতে হয় মহান মানুষকে।’ তাঁর ওই উক্তির কারণেই কি না জানা নেই, পাশ্চাত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বেশির ভাগ বই-ই উৎসর্গিত হয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বা রাজপুরুষ-রাজরানিদের উদ্দেশে। ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের প্রথম যুগে বা ষোড়শ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে গ্রন্থ উৎসর্গের প্রথা পুরোদমে চালু হয়। তখন ইংল্যান্ডের রানি ছিলেন প্রথম মেরি। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ৪২ বছর, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল বিচিত্র সব বিষয়ের ৩৩টি বই ও ১৮টি পাণ্ডুলিপি। ১৬০৫ সালে মিগুয়েল দে সেরভান্তেস তাঁর ডন কিহোতে উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় কোনো উৎসর্গপত্র না দিলেও বছর দশেক পরে যখন দ্বিতীয় আরেকটি অংশ নিয়ে এক অখণ্ড সংস্করণ বের হলো, তখন ঠিকই বেশ কয়েকজন স্পেনীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রশাসকের নামে একটি উৎসর্গপত্র লিখেছিলেন। তবে বই-উৎসর্গের প্রথা আমাদের দেশে ছিল না, সংস্কৃত সাহিত্যধারায়ও এর তেমন কোনও নিদর্শন মেলে না। ইংরেজি গ্রন্থাদির অনুকরণে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে এই উৎসর্গপ্রথা চালু হতে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরে। সাধারণভাবে বইয়ের উৎসর্গগুলি উপহারের একটি ঐতিহ্য হিসেবে প্রচলিত। এই ব্যক্তিগত বার্তাগুলি উপহারের অর্থের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, সেইসাথে সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক দলিলও স্থাপন করে। একটি সাধারণ উৎসর্গ একটি বইকে একটি বিশেষ মর্যাদাবান উপহারে পরিণত করতে পারে যা ভবিষ্যতে বিশেষ অর্থ বহন করবে। অনেক গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ধরে রাখে তৎকালীন সাহিত্যের ইতিহাস, এমনকি তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে বইটির প্রকাশকালের সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির নানা চালচলন। কোনো বইয়ের উৎসর্গপত্রটি পড়ে লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানান চড়াই-উতরাই, ভাবনা, পৃথিবীর অবয়ব ও মনোজগতের নানা কূটাভাসও পাঠক অনুভব করতে পারেন। এ ছাড়া রচয়িতার নিজস্ব ক্ষোভ, রসবোধ ও মেজাজ-মর্জির ধীর বা চঞ্চল চালচলনও এতে ধরা পড়ে বৈকি। আধুনিককালে যন্ত্রশক্তি ও প্রযুক্তির কারণে বই প্রকাশ যেমন সহজ হয়ে এল, তেমনি বইয়ের উৎসর্গপত্রের বৈচিত্র্যও বাড়ল। রাজা-রানি-অভিজাতদের বৃত্তের বাইরে নানা মানবিক গল্পও জড়িয়ে যেতে থাকল সেসব ঘিরে। যেমন কার্ল মার্ক্স তাঁর মহাগ্রন্থ ডাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭) উৎসর্গ করেন প্রয়াত বন্ধু স্কুলশিক্ষক উইলহেম উলফকে। যিনি কিনা মৃত্যুর আগে মার্ক্সের জন্য বেশ কিছু অর্থকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। পুরো জীবনে লেখা নিজের সেরা বইটি তাই আর কাউকে উৎসর্গ করার কথা মার্ক্স ভাবতেও পারেননি। উৎসর্গপত্র নিয়ে নানা রকম মন–কষাকষি বা উদ্ভট কাণ্ড অবশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। কখনো কখনো প্রকাশকের খামখেয়ালিতে বা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে পাল্টে যায় উৎসর্গপত্র। আবার উৎসর্গপত্র মারফত মনের ক্ষোভ মেটানোর কাণ্ডও দুর্লভ নয়। মার্কিন কবি ই ই কামিংস একবার সেভেন্টি পোয়েমস নামের একটি বই প্রকাশের আশায় মোটমাট ১৪টি প্রকাশনা সংস্থায় পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম, প্রতিটির কাছেই তাঁকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। অগত্যা উপায় না দেখে মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে বইটি তিনি নিজেই ছাপেন, যদিও নাম দেন পাল্টে। নো থ্যাংকস (১৯৩৫) শিরোনামে বইটি প্রকাশ পেলে দেখা যায়, যে ১৪ প্রকাশকের দ্বারস্থ হওয়ার পর কামিংস বিফল হয়ে ফিরেছিলেন, বইটি উৎসর্গিত হয়েছে তাঁদেরই নামে। চার্লস বুকাওস্কির মতো প্রথাভাঙা লেখক আবার তাঁর উপন্যাস পোস্ট অফিস-এর (১৯৭১) উৎসর্গপত্রে সোজা ঘোষণাই করেছিলেন, ‘বইটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি’। ইংরেজ অভিনেতা ও লেখক স্টিফেন ফ্রাই তো আরও এক কাঠি সরেস, তাঁর দ্য লায়ার (১৯৯১) উপন্যাসের উৎসর্গপত্রের পাতায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা রেখে নিচে লিখে দিয়েছিলেন, ‘ওপরে পুরো নামটা বসিয়ে নিন।’ পাশ্চাত্য কেতায় প্রথম বাংলা বই কাউকে উৎসর্গ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৫৯ সালে প্রকাশ পাওয়া নিজের শর্মিষ্ঠা নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে। আজ থেকে ১৬০ বছর আগে শুরু হওয়া গ্রন্থ উৎসর্গের এই ধারা এখনো বাংলা সাহিত্যে বিচিত্ররূপে বহমান। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) বা হেকটর-বধ (১৮৭১)। আবার রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করার বেলায় খানিক কৃপণ ছিলেন বলতে হয়। জীবদ্দশায় প্রকাশিত ২০৮টি বইয়ের মধ্যে তাঁর উৎসর্গপত্রসমেত প্রকাশিত বই মাত্র ৬৪টি। আবার কাউকে কাউকে দুটি করে বইও উৎসর্গ করেছেন। কাদম্বরীসহ মোট ৫১ জন ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গলাভে ধন্য হতে পেরেছেন শেষমেশ। সমকালীন বাংলা কবিতা জগতে উৎসর্গ যেন আরো বৈচিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়৷ সমকালের সদা নিরীক্ষাপ্রবণ কবি সাম্য রাইয়ান কল্পজগৎ উন্মোচনের ইঙ্গিত দেন উৎসর্গপত্রের সেই ছোট্ট পরিসরেও। কয়েকটিমাত্র শব্দে কখনো সেখানে তিনি মুগ্ধতা অথবা হাহাকারে গল্প বলেছেন, কখনো বলেছেন নিখাদ ভালোবাসার কথা, কখনো রেখেছেন অপার রহস্য। যে রহস্য উন্মোচনের দায়ভার বিদগ্ধ পাঠকমহলের উপরই বর্তায়৷ সাম্যর লেখার মতো তাঁর উৎসর্গপত্রের জগৎ বড়ই বিচিত্র, আকর্ষণীয়। এগুলো পড়লে তাঁর উথালপাতাল জীবনের নানা হাহাকার ও সাহিত্যিক প্রেরণার বিষয়ে ইঙ্গিত মেলে৷ এগুলো প্রত্যেক বইয়ে বিচ্ছিন্ন আকারে থাকায় এবং এদের আকার ক্ষুদ্র হওয়ায় হয়তো অনেকের উপলব্ধি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেসব উৎসর্গপত্র একত্র করলে দেখা যাবে সাম্য রাইয়ানের নতুন এক জগত উদ্ভাসিত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গদ্যের বই ‘সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট’৷ মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার এ বইয়ের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন, “পথিক ভাই/ কামরুল হুদা পথিক;/ যিনি আমাকে সুবিমল মিশ্রর সাথে পরিচয় করিয়েছেন৷” সরল সাদামাটা উৎসর্গ৷ যেহেতু কামরুল হুদা পথিক নামে কেউ একজন তাকে সুবিমলের সাথে পরিচয় করিয়েছেন, তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে বইটি তাকে উৎসর্গ করেছেন৷ ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় সাম্য রাইয়ানের প্রথম কবিতার বই ‘বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা’৷ বাঙ্ময় প্রকাশিত এ বইটি তিনি উৎসর্গ করেন কবি রাশেদুন্নবী সবুজকে৷ উৎসর্গপত্রে লিখেন, ‘একজন মানুষ’৷ মানুষের পরিচয় দিতে কবি যখন লিখেন ‘একজন মানুষ’, তখন ‘মানুষ’ শব্দটি আমাদের সামনে একই সাথে রহস্য ও একগুচ্ছ জিজ্ঞাসা সমেত উপস্থিত হয়৷ বোঝা যায়, আমরা চারপাশে যত মানুষরূপী প্রাণী দেখি, রাশেদুন্নবী সবুজকে লেখক তাদের থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে উপস্থাপন করেন৷ তাঁর বিচারে সবুজ প্রকৃত মানুষ৷ এরপর কবির ‘হলুদ পাহাড়’ ও ‘মার্কস যদি জানতেন’ শিরোনামে দুইটি ছোট বই (যথাক্রমে ২৪ ও ১৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয় উৎসর্গপত্র ছাড়াই৷ এবং এর পরেই শুরু হয় আসল রহস্য৷ ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় কবির কবিতাবই ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’৷ ৬৪ পৃষ্ঠার এ বইয়ের অনুপম উৎসর্গপত্রটিতে কবি লিখেছেন, ‘সোনামুখী সুঁই থেকে তুমি / চুইয়ে পড় সুতো হয়ে / নিচেই বিদ্ধ আমি / সেলাই হই তোমার সুতোয়৷’ উৎসর্গপত্রটি যেন এক হৃদয়গ্রাহী প্রেমের কবিতা৷ কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে কবি এই পংক্তি লিখেছেন তা অজানাই থেকে যায়৷ শুধু থাকে ইঙ্গিত৷ এই ইঙ্গিত আমাদের কৌতুহলী করে তোলে৷ আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি৷ বইটির কবিতাগুলো পাঠ করে একটি নাম আবিষ্কার করতে পারি ‘হামিংবার্ড’ শীর্ষক কবিতায়৷ যেখানে কবি লিখেছেন, ‘চমকে দিও না তাথৈ/ উড়ে যাবে৷’ তাহলে কি তাথৈ কোন ব্যক্তির নাম— নারীবিশেষ? তাকেই কি উৎসর্গে ইঙ্গিত করেছেন? আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র৷ ২০২১ সালে প্রকাশিত হয় সাম্য রাইয়ানের আখ্যানধর্মী মুক্তগদ্যের বই ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’৷ এর উৎসর্গপত্র রহস্যময়, শিরোনামের সাথে সাজুয্যপূর্ণ— ‘ব্যাগভর্তি গুডবাই নিয়ে চললে কোথায়?’ এ তো নিছক উৎসর্গপত্রের সীমা ছাড়িয়ে কবির অন্তর্গত তরতাজা উপলব্ধির প্রকাশ। কাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন কবি? উত্তর অজানা৷ এটিও কি কোনো নারীকে? হামিংবার্ডকে? তাহলে কি যাকে কবি হামিংবার্ডের রূপকে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি কি চলে গেছেন? অজস্র কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে কবি সরে দাঁড়ান! এত রহস্য কেন তাঁর উৎসর্গপত্রে? রহস্যময় উৎসর্গ পত্রের কথা যখন উঠলই তখন যে উৎসর্গপত্রের রহস্য উদঘাটনে গবেষকদের রীতিমত গলদঘর্ম হতে হয়েছিল এবং তারা শেষ পর্যন্ত এর রহস্য উদঘাটন করতে পারেননি, সেটির কথা উল্লেখ করতেই হয়৷ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট সংকলনের উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত ‘মি. ডব্লিউ এইচ’ আদতে কে, তা খুঁজে বের করতে বিশেষজ্ঞরা গলদঘর্ম হয়েছেন বহুবার। সম্প্রতি গবেষক জিওফ্রে কেনেভলি দাবি করেছেন, ওই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আসলে বইয়ের প্রকাশক টমাস থর্পের বন্ধু উইলিয়াম হোম। উপরন্তু সনেটগুচ্ছের উৎসর্গপত্রটি আদৌ স্বয়ং শেক্সপিয়ারের রচিত, নাকি প্রকাশকই আদতে তা লিখে দিয়েছিলেন, এ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ২০২২ সালে প্রকাশিত হয় সাম্য রাইয়ানের কবিতার বই ‘লিখিত রাত্রি’৷ ৫৫ পর্বের সিরিজ কবিতার এ বইয়ের উৎসর্গে কবি লিখেন, ‘এই মাঝরাতে ক্যান তুমি দূরের পাখি হইলা কও?’ এই উৎসর্গ পাঠের পর কবির অন্তর্গত তীব্র হাহাকার আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, আমরা আক্রান্ত হই৷ ভাবি, প্রিয় মানুষ মাঝরাতে দূরের পাখি হয়ে যাবে কেন? কতোটা নিবিড় বেদনা এই একটিমাত্র বাক্যে লুকানো তার রহস্য উন্মোচনে ডুব দিতে হয় লিখিত রাত্রির গহীনে৷ তবু যদি কিছু খোলসা হয় এই আশায়! ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয় কবিতার বই ‘হালকা রোদের দুপুর’৷ এর উৎসর্গপত্রে যে অনুপম নিবেদন কবির, তা-ও একবাক্যে— ‘আমাকে বহন করো নখের মতো, বেড়ে ওঠার যত্নে৷’ উৎসর্গপত্রও মনে হয় তাঁর কবিতার মতোই কৌতূহলোদ্দীপক। নখের প্রতীকে কবি এখানে অনুল্লেখিত একজনের সঙ্গী হবার যে নিবেদন পেশ করেছেন, তা কি সত্যি হবে? নখ আমাদের কাছে খুব সাধারন, কবিও খুব সাধারনভাবেই সঙ্গী হতে চেয়েছেন, বিশেষ কিছু আয়োজন তার দরকার নেই৷ সাধারণ, স্বাভাবিকভাবেই তিনি সঙ্গী হতে চেয়েছেন৷ তথাপি নখের প্রতি আমরা যতটুকু যত্নশীল, ততটুকু যত্নহীন হলেই তিনি সন্তুষ্ট৷ এর অধিক-বিশেষ প্রত্যাশা কবির নেই৷ কিন্তু নখের প্রতীকে এরকম আহ্বান নতুন৷ সামান্য সাধারন অতিপরিচিত নখও কবির সান্নিধ্যে কতটা নিপুণ ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হতে পারে তা সাম্য রাইয়ান দেখিয়েছেন৷ তাঁর উৎসর্গপত্রগুচ্ছ পাঠ করে কবিমনের ভেতরকার এক অতল হাহাকারের নিদর্শন আমাদের সামনে উঠে আসে না? একটি চমৎকার জগৎ রয়েছে সাম্য রাইয়ানের বইয়ের উৎসর্গগুলোর৷ অনেক আড়াল, অনেক রহস্য নিয়ে তা পাঠককে আহ্বান জানায় কবিতার অন্তর্লোকে প্রবেশের৷ বিশেষত তাঁর চারটি গ্রন্থের উৎসর্গপত্র আমার দৃষ্টিতে একজনকেই উদ্দেশ্য করে লেখা৷ কবি সযত্নে তাঁর নাম এড়িয়ে পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন অভাবিত রহস্যের দ্বারপ্রান্তে৷ এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা৷ যখন হিসাব করে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা ১১টি বই উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ‘নতুন বৌঠান’ কাদম্বরী দেবীর নামে৷ উৎসর্গপত্র যেমন লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও হাহাকার, আশা-নিরাশা-স্বপ্ন ধরে রাখে, তেমনই তা সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতারও প্রকাশ ঘটায়। তাই উৎসর্গপত্রের গভীর পাঠ থেকে লেখালেখির নানা জটিলতা ও লেখকদের মানসিকতার ইতি-নেতি বুঝতে কিঞ্চিৎ হলেও সুবিধা বৈকি।
সাম্য রাইয়ান: সময়ের বিপরীতে হাঁটা শব্দসাধক
সৈয়দ আহসান কবীর সাম্য রাইয়ান সময়ের বিপরীতে হাঁটা শব্দসাধক৷শব্দের প্রজ্জ্বলিত শিখা তাঁর কবিতায় প্রাঞ্জলতা ছড়ায়। অন্যরকম মনে হয়। জেগে ওঠার অনুভূতি জাগায়। রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতার আনাচেকানাচে ঘোরে তার শব্দতীর; খুঁজতে থাকে কুপিবাতি। পাঠিকা-পাঠকের চোখে, মনে, মগজে গেঁথে দেন অস্থির বাস্তবতার প্রশ্ন। তিনি কবি সাম্য রাইয়ান। সম্প্রতি ‘মার্কস যদি জানতেন’ তার কাব্যগ্রন্থটি পড়ছিলাম। পড়তে গিয়ে ‘ম্যাডামের দেশে’ ঘুরে এলাম। যেখানে তিনি লিখেছেন- “…এটা দাস ক্যাপিটালের যুগ/ ঘরে ঘরে মার্কস ঢুকে যাবে।” আমি অভিভূত। কাব্যগ্রন্থজুড়ে অধিকাংশ কবিতায় কবি সাম্য রাইয়ান সমাজের আধখোলা চোখ বর্ণনায় মত্ত হয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। শীতল দ্রোহের গনগনে শব্দরা ভর করেছে পংক্তিমালায়। প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন সাদামাটা ভাষায়; রেখেছেন ধোঁয়াশা। যদিও পড়তে গিয়ে কিংবা ভাব বুঝতে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়নি। উপমা, অলংকরণ, চিত্রকল্প সৃষ্টি করেনি জটিলতা। মেটাফোরিক্যাল কবিতাগুলোও হৃদয় ছুঁয়ে গেছে; গাম্ভীর্যের আতিশয্যে দুর্বোধ্য হয়নি। কিছু কবিতায় তুলে ধরেছেন তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ। ‘বিশ্বরূপ’ শিরোনামে লেখা কবিতায় তাই হয়তো কবি লিখেছেন- “চর্বিত মগজের পাশে হাতঘুড়ি ঝুলে আছে হৃদয়ের গোপন কোটরে।” ‘যুদ্ধবাদ’ কবিতায় লিখেছেন- “বোমারু রোবটের হাতে শব্দের ঝুলি, ক্রমিক সংখ্যার মতো নিক্ষেপ করছে তীব্র অপরিকল্পিত শব্দের ফোঁটা; ফলত পাখিরা হচ্ছে মানুষের মতো- চিৎপটাং। অস্থিরতার মতো ভয়াবহ পৃষ্ঠাগুলো অকপটে সঙ্গী হচ্ছে মানুষের। অতিদূর নক্ষত্রের মতো আবছা হলে দূরবর্তী দৃশ্যের ছায়া, আমি তবে কীভাবে তোমাকে ছোঁব?” কবি সাম্য রাইয়ানের ওপর হাইকু’র ঢঙেও কবিতা ধরা দিয়েছে। যদিও সেখানে তিনি সমাজ সদস্যদের অবয়ব তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন। উঠিয়ে এনেছেন মানুষের মতো দেখতে কারও কারও মধ্যে লুকিয়ে থাকা নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। তাদের ‘পরিচয়’-এ তাই তিনি বোধ করি লিখেছেন- “তুমি কি তাহার কুকুর?/ লেলিয়ে দিয়েছে বলে/ আক্রোশে ছুটে এলে!” কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা ‘মার্কস যদি জানতেন’-এ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রতি নান্দনিক খেদ প্রকাশ করেছেন। আগের নির্ভয় দিনগুলোকে প্রথমে তিনি তুলে ধরে পরে বর্তমান বাস্তবতাকে পঙ্ক্তিমালার পর্বে পর্বে এঁকেছেন। পরে ফের ফিরেছেন কালজয়ী মার্কসের কাছে। বলেছেন— “মার্কস যদি জানতেন/ অন্ধকারেও কত কাণ্ড ঘটছে রোজ।” আর শুরুতে নির্ভয় দিন এঁকেছেন এভাবে— “বড় ভালো ছিল সেই প্রেমিকাসকল/ খুব ভোরে স্নান করে নিতো— হেসে খেলে/ ওরা ধোয়াজামা গায়ে খোলা ময়দানে যেত।” কবি কবিতার প্রতি দায় রেখেছেন। বলেছেন কবিজীবনের কথা। সোচ্চার হয়েছেন শব্দবুলেট ছুড়তে। সচেষ্ট হয়েছেন জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে কবিত্বের নিজস্ব সত্তা ঘোষণায়। তিনি লিখেছেন— “যদি অব্যাহত বেঁচে থাকি/ শ্বাস নিই গ্যালন গ্যালন;/ প্রতিটি রক্তফোঁটা থেকে শব্দ জন্মাবে আর/ গহিন থেকে বেরুবে নির্ভীক সিরাজ সিকদার।” এ দৃঢ়তা কবিকে কাব্যসময়ের সিঁড়িতে কাল ধরে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। ‘বাঘ’ লেখাটি একটি চমৎকার অণুগল্প হতে পারত। লেখাটি সমাজের দর্পণ বটে। সত্য ও ন্যায়ের মলিন প্রচ্ছদে উঠে এসেছে আলো ও কালোর পার্থক্য। যদিও কবিতা হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। সব মিলিয়ে গ্রন্থটি পড়ে আমার মনে হয়েছে— কবি সাম্য রাইয়ান সময়ের বিপরীতে হাঁটা নিপুণ শব্দসাধক। যা তাকে বিশেষত্ব দিচ্ছে, পরেও দেবে বলে বিশ্বাস।
হাউজ অব লর্ডস: মার্কস যদি জানতেন
মাহাদী আনাম আদিবা আমাকে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করে, ‘ভালো মানুষ মরে গেলে বৃষ্টি হয় কেনো?’ওকে বলি, ‘মানুষ প্রকৃতির সেরা সন্তান- সেরা কিছু হারালে তাই প্রকৃতি কাঁদে, এপিটাফে রঙধনু এঁকে দেয়।’ কাঠেরপুল মোড়ে দাঁড়িয়ে মাগরিবের আজান শুনছি- গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এই শহর থেকে নিয়ন বাতিগুলো মুছে যাচ্ছে- আমার কষ্ট হয়।– মাফ করবেন, আমি কি একটু সাহায্য পেতে পারি?ভাঙা ভাঙা ঘরঘরে গলায় ভীষণ দ্বিধা নিয়ে যিনি প্রশ্নকর্তা- তাঁর তামাকের পাইপটা নিভে গেছে। এবং আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তবুও টানছেন। বেশ উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা দাড়ি।— নকশালের দিন আর স্টাইল বহু আগেই চলে গেছে— তবুও আপনি এভাবে কম্বল টাইপ চাদর মুড়ি দিয়ে আছেন কেন? ওটা থেকে বোঁটকা গন্ধ আসছে।– মাফ করবেন, আমি কি একটু সাহায্য পেতে পারি?লোকটা ত্যাঁদড় আছে! তাঁর বিদিক চাদরের নীচের দিকে ওভারকোটের অংশ দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে সাধারণত কেউ ওভারকোট পরে না। দু’কাঁধ কিছুটা ঝাঁকিয়ে বললাম, ‘বই প্রকাশ করবেন? পাণ্ডুলিপি রেডি? গল্প, উপন্যাস না কবিতা? কত ফর্মা করতে চাচ্ছেন? শুনুন, প্রচ্ছদে কিন্তু আমি ছাড় দেবো না।’এবার ভদ্রলোকের দাড়ির ফাঁকে স্মিত হাসি দেখা গেলো, ‘আপনার কাছে সবাই কি বই করতেই আসে? আমার কিছু ভাঙতি দরকার— কোথাও পাচ্ছি না।’– হ্যালো কার্ল, আপনি জানেন জারের আমল চলে গেছে— এমনকি লেনিন, স্ট্যালিনও। আপনার মুদ্রা বিনিময়যোগ্য নহে।উনি চোখ দুটো প্রায় দু’হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আদি-অন্ত ভাবমার্কা লুক নিয়ে বললাম, ‘সমস্যা নেই, আর কেউ জানে না।’– তু…তু…তুমি… আপনি…– গ্যাব্রিয়েল, এসেছিল। বলল কিছুক্ষণ পর আপনি এই কিম্ভুত প্যাটার্ন নিয়ে আসবেন। এজন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইউ নো বস, আমি জানতাম! আমাকে তুমি করেই বলুন।– গ্যাব্রিয়েলের সাথে তোমার ভালো সম্পর্ক?– তাঁকে আমি ভালোবাসি, সে’ও। আমরা পরস্পর তখন সহজে হাসছি। বিন্দু বিন্দু করে জমে জল– আমরা আলাপ বাড়াই। কে কেমন আছেন- আইনস্টাইন অথবা রবীন্দ্রনাথ। “রাত বাড়ছে, হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।” মন্তু আর টুনির জন্য আমার কষ্ট হয়।– তোমাকে বিব্রত করার জন্য দুঃখিত। আদতে আমার ভাঙতির প্রয়োজন নেই। বিষণ্ণ ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ ধরে হেঁটে যেতে পারব আমি। জানো তো, মৃতদের ক্ষুধা, অবসন্নতা থাকে না! তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, নন্দিত অথবা নিন্দিত মাহাদী আনাম।– কার্ল, আপনি মৃত?– তা নাহলে ‘বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা’ কেন লেখা হলো?– আমার রাইফেল দারুণ লাগে, উইনচেস্টার রাইফেল। দেখুন, কেউ আপনাকে না বুঝলেও আপনি সত্য। সত্যের কোনো সঙ্গী কিংবা প্রমাণ দরকার হয় না।তিনি বাচ্চাদের মতো মাথা দোলান— আমি আনন্দ পাই।– আমি কি আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দেবো?– নাহ, আচ্ছা শেষ প্রশ্ন, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ কী করে? তোমার সানগ্লাস?হো হো করে হেসে উঠলেন, ‘কিছুতেই মাথায় আসছিল না– রাতে, বৃষ্টিতে কেনো এটা পরে আছ তুমি! কই পেলে এ বস্তু? গ্যাব্রিয়েল?’ আমার ছাতা নেই। ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরি। আমি একবারও পিছনে তাকাই না। কানে হুইসেল তোলে “কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস”। আমি জানি, সাম্য রাইয়ান কখনও মাথা নীচু করে হাঁটে না।
বাংলা সাহিত্যে নতুন পাঠঅভিঘাত সাম্য রাইয়ানের ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’
ড. অমিতাভ রায় ‘ব্যাগভর্তি গুডবাই নিয়ে চললে কোথায়?’ এই একটি বাক্যের ছবি ফেসবুকে কারো টাইমলাইনে পেয়েছিলাম৷ তাকে লেখকের নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি৷ পরে হঠাৎ আরেকদিন এই বাক্যটি পেলাম এক বন্ধুর টাইমলাইনে, সঙ্গে লেখকের নাম— সাম্য রাইয়ান৷ মাত্র পাঁচ শব্দের একটি বাক্যই যেন অমোঘ নিয়তির মত আমাকে টেনে নিয়েছে সাম্য রাইয়ানের সাহিত্যসম্ভারের নিকট৷ এরপর জানতে পেলাম সাম্য রাইয়ানের গদ্যের বই ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ এর উৎসর্গবাক্য এটি৷ ১৩টি গদ্য নিয়ে এ সংকলনটি বাংলাদেশ থেকে ঘাসফুল প্রকাশ করেছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে৷ গ্রন্থভুক্ত ১৩টি গদ্যকে আমরা প্রধানত দুইভাগে ভাগ করতে পারি৷ কারন দুই ধারার গদ্য এই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে৷প্রথম ধারা:• দুলে ওঠে তোমার প্রদীপ• বিদীর্ণ আলোর ধারা• পৃথিবী খুব একটা মজার জায়গা না• একটা সত্যি কথা বলো দ্বিতীয় ধারা:• হাঁটতে হাঁটতে পথ গ্যাছে ক্লান্ত হয়ে• টোলখাওয়া চেহারায় আঁধারে দাঁড়িয়ে লাভ নেই• প্রচণ্ড নীরবে খসে পড়ে রাত্রির সমস্ত কাঠামো• শিল্পী যা বলেন তা গুরুত্বপূর্ণ, যা বলেন না তা-ও গুরুত্বপূর্ণ• অন্ধকারে সাঁতার কাটে নিঃসঙ্গ সোনার হরিণ• রাত্রি একটা অনাহুত বেদনার নাম• শাদা অন্ধকারে অন্য মন্ত্র• কালোবাঘ-লালকাক পাশাপাশি শুয়ে থাক• কবিতার পূর্ণদেহে নদীর নিজস্ব ঘ্রাণ আমার মনে হয়েছে এই গ্রন্থের গদ্যগুলোকে দু’টো আলাদা গ্রন্থরূপ দিলে উত্তম সিদ্ধান্ত হতো৷ কিন্তু লেখক গ্রন্থভুক্ত দুই ধারার গদ্যকেই মুক্তগদ্য হিসেবে চিহ্নিত করে একই গ্রন্থভুক্ত করার বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে সঠিক হয়নি৷ প্রথম ধারার গদ্যগুচ্ছ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে আলোচনা করবো৷ প্রথম ধারাভুক্ত চারটি গদ্যকে ‘শাস্ত্রবিরোধী গল্প’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়৷ শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনের সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী এগুলোকে শুধু গল্পই নয়, বরং উৎকৃষ্ট গল্প বলা যায়৷ কেননা শাস্ত্রবিরোধী গল্প ইশতেহারের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এই চারটি গদ্যে৷ যে ইশতেহারের স্লোগান ছিলো, ‘গল্পে এখন যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে৷’ এই ধারার সার্থক গল্প লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, কল্যান সেন, আশিস ঘোষ, অমল চন্দ, সুনীল জানা প্রমূখ৷ বাংলাদেশে এই ধারায় আর কেউ লিখেছেন কি না সে খবর আমার জানা নেই৷ যদিও সাম্য রাইয়ান এগুলো প্রসঙ্গে কোন ভূমিকা লিখেননি বইয়ে, ফলে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানার সুযোগ হচ্ছে না৷ তবে তিনি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “… (গ্রন্থে) কিছু মুক্তগদ্য আছে যেগুলো নীরেট অনুভূতি দিয়ে গাঁথা৷ প্রলাপ৷ অন্ধকারের কুঠুরীতে বসে বকে যাওয়া কথামালা৷ জলের তরঙ্গ কিংবা শিশির-বিন্দু-প্রবাহের অনুভূতি তৈরি করবে আপনার মনে৷ এমনই তো৷ এইসব বেখেয়ালী রচনাকতক— … এটা জার্নি— এই ট্রেন আপনাকে নির্দিষ্ট কোথাও পৌঁছে দেবে না, বরং যেতেই থাকবে৷ যতক্ষণ আপনার ইচ্ছে হবে যাত্রা করবেন, কোনো রূপে আটকে গেলে ট্রেন থেকে নেমে যাবেন— এটা তো লোকাল ট্রেন, চিন্তা কী?” অর্থাৎ সাম্য রাইয়ান এগুলোকে প্রলাপের মত মুক্তগদ্য বলছেন৷ কিন্তু আমি এই চারটি গদ্যকে ‘শাস্ত্রবিরোধী গল্প’ বলতেই স্বচ্ছন্দ্যবোধ করব৷ যেমন ‘দুলে ওঠে তোমার প্রদীপ’ গল্পে সাম্য লিখেছেন, “চুপচাপ, মনে হয়, তবু যেন কেউ ওই পাড়ে আছে৷ কোনো কথা নেই, সাড়াশব্দ থেমে গেছে কত আগে! কখনো জলের মতো মৃদু বুদবুদ হয়ে জাগে! দু’ঝুটি চুল ঘুমিয়ে পড়েছে কবে…৷ ঘুমাচ্ছে কুয়াশা গুটিয়ে আস্তিন; থেমে থেমে আসে তুমুল বৃষ্টিদিন৷” ‘বিদীর্ণ আলোর ধারা’ গল্পে তিনি লিখেছেন, “আবহাওয়া দফতর বলেছে, জানে না জলের কথা— মেঘের খবর৷ আকাশে তাক করে শ্বাসের প্রোটিন, ভাবছি পড়বো প্রেমে, লিখবো রোদের কথা৷” সাম্যের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হলো সাধারণ শব্দে-বাক্যে অসাধারণকে ধারণ করা৷ বরবরই তিনি সেটা করেছেন, কি কবিতায়, কি গদ্যে! সমান পারঙ্গমতা দেখাচ্ছেন৷ শীতের কুয়াশা ভেদ করে ট্রেন আসে; লোকাল ট্রেন- যেখানে মাটি আর মানুষ এবং তাঁদের যাপিত বোধ একাকার। আমরা প্রতীক্ষা করে থাকি- সাম্য রাইয়ানের পকেটের দিকে তাকাই। তিনি শিশুর আনন্দ বোঝেন, আমাদের জন্য নিয়ে আসেন অনেকগুলো হাঁসের বাচ্চা। তাই ‘পৃথিবী খুব একটা মজার জায়গা না’ গল্পে তিনি লিখেন, “নদীর টানে বিধ্বস্ত হয়ে হয়ে মাটিতে মিশে গেলাম। দৃষ্টিসীমায় দেখি প্লাবন- মনে হয়, সে তো অন্য কেউ নয়, এই আমি- যার সাথে দেখা হলে পথে মাইশা চিৎকার করে ডাকে- পাগলা দাদা, কই যাও?শিশুটি খলখলিয়ে হাসে। জগৎ বিদীর্ণ করে হাসে। আমিও হাসি। হাসতে হাসতে বলি, পকেটে হাঁসের বাচ্চা আছে, নিবি?” প্রেম কতটা প্রকট সুন্দর রূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে তার নমুনাও যেন ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ গ্রন্থে ফুটে ওঠে৷ লেখকের অন্তর্গ নিগূঢ় অনুভূতি আমাদের নাড়া দেয়৷ তাঁর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পাঠককে চমকে দেয়া বা ধাক্কা দেয়া৷ একটি নির্দিষ্ট গতিতে তিনি পাঠককে নিয়ে জার্নি শুরু করেন৷ এরপর শেষ বাক্যে এমন অনুভূতি তৈরি করেন যাতে পাঠক ধাক্কা খেতে বাধ্য৷ আবার নতুন করে পুরোটা পড়ার আবেদন তৈরি হয় এতে করে, যখন ‘দুলে ওঠে তোমার প্রদীপ’ গল্পে তিনি লিখেন, “ঘোলাজল ভাসতে ভাসতে তোমার কাছে পৌঁছে যায়৷ বুঝতে পারি৷ প্রয়োজন নেই পুরাতন তর্কের৷ অযথা প্রজাপতি! বৃথা অক্টোপাসের মতো বন্ধু ছিলো যারা, প্রণাম জানিয়ে ফিরে এসে ভাবি, জীবন দেখায় যেন রঙধনু৷ অসুস্থ হয়ে কী লাভ, যদি তোমার শুশ্রূষা না পাই?” এবার আসি দ্বিতীয় ধারা প্রসঙ্গে৷ দ্বিতীয় ধারার নয়টি গদ্য গ্রন্থভুক্ত হয়েছে৷ এই ধারার গদ্যগুচ্ছ পাঠ করে মনে হয়েছে, নতুন ধরনের গদ্য লিখেছেন তিনি৷ এই গদ্যের ধরণ বাংলা ভাষায় প্রথম হবার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান৷ আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা/সমালোচনা পাঠ করে অভ্যস্ত৷ কিন্তু ‘কবিতাপাঠের অনুভূতি’ পাঠ করতে একেবারেই অভ্যস্ত নই৷ ‘কবিতার দুর্বোদ্ধতা’ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছিলেন, “কবিতা সম্বন্ধে ‘বোঝা’ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝিনে; কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু ‘বোঝায়’ না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা ‘বোঝা’ যাবে না, ‘বোঝানো’ যাবে না।” এই যে বুদ্ধদেবের কথা, এই কথাখানির সফল প্রয়োগ লক্ষ করলাম সাম্য রাইয়ানের ৯টি গদ্যে৷ এ প্রসঙ্গে সাম্য রাইয়ান নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “কবিতা আমরা অনুভব করতে পারি৷ এমত ভাবনা থেকেই ২০১০ সালের দিকে শুরু করেছিলাম এক নতুন খেলা— কবিতা বনাম কবিতা কবিতা খেলা! এ হলো সিরিজ গদ্য৷ এই গদ্যগুলোতে আমি বাঙলা ভাষার বিশেষত নতুন সময়ের (শূন্য, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের) নতুন কবিদের কবিতা পাঠপরবর্তী অনুভব ব্যক্ত করেছি৷ এগুলো মূল্যায়নধর্মী গদ্য নয়৷ কখনো কবিতা পড়তে পড়তে আমার মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তা বিবৃত করেছি৷ আবার কখনো কোন কবিতা পড়ে ব্যক্তিগত কোন স্মৃতি মনে পড়েছে, তা-ই উল্লেখ করেছি৷ হুবহু, অকপটে!” তিনি এখানে অর্ধশতাধিক কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন, এবং তা পাঠ করে পাঠক হিসেবে সাম্য রাইয়ানের মধ্যে যে ‘অনুভূতি’ সৃষ্টি হয়েছে তা-ই তিনি গদ্যগুলোতে অভিনব কায়দায় বিবৃত করেছেন৷ যা আমার মতো পাঠকের কাছে কবিতাকে আরো নতুন আরো আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করেছে৷ এখানে আবুল হাসান, সিকদার আমিনুল হক থেকে শুরু করে হাল আমলের সুহৃদ শহীদুল্লাহ, ভাগ্যধন বড়ুয়া, জিললুর রহমান, সৈয়দ সাখাওয়াৎ রাজীব দত্ত, আহমেদ নকীব, তানজিন তামান্না, আরণ্যক টিটো, নাভিল মানদার, আহমেদ মওদুদ, হাসনাত শোয়েব, বিধান সাহা, নির্ঝর নৈঃশব্দ্য, শুভ্র সরখেল, রাশেদুন্নবী সবুজ, মাহফুজুর রহমান লিংকন, শাহেদ শাফায়েত, শামীমফারুক, ফরহাদ নাইয়া, রাসেল রায়হান, নাজমুস সাকিব রহমান, সাইদ উজ্জ্বল, চঞ্চল নাঈম, আহমেদুর রশীদ, অনুপ চণ্ডাল, পদ্ম, শান্তনু চৌধুরী, অসীম নন্দন এরকম অ-নে-ক কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন৷ এই সকল কবি আমার পরিচিত নয়৷ বরং বলা ভাল যে, গুটিকতকের লেখার সাথেই কেবল আমি পরিচিত৷ ফলত ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ পাঠ করে আমি নিজেই অনেক কবির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম৷ এ প্রসঙ্গে সাম্য রাইয়ান তাঁর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে লিখেছিলেন, “গদ্য লিখি অনেকদিন৷ মুক্তগদ্য লিখছি প্রায় দশ বছর৷ দুই হাজার এগারোতে বিশেষ ধরণের মুক্তগদ্য লিখতে শুরু করি, এগুলো কবিতা নিয়ে, কিন্তু কবিতা সম্পর্কিত আলোচনা নয়, বরং কবিতা পড়তে পড়তে আমার মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়েছে তারই বর্ণনা৷ সংযুক্ত করেছি সেইসব কবিতার অংশ৷” ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ গ্রন্থে গদ্যের ফর্ম নিয়ে লেখকের এক্সপেরিমেন্ট পাঠককে নতুন স্বাদ দিতে সক্ষম৷ বাংলা ভাষায় সমকালীন প্রায় অর্ধশত কবির কবিতাংশ গদ্যগুলোর শরীরে প্রোথিত করে লেখক শুধু সেই কবিদের সাথে আমাদের পরিচিতই করাননি, বরং তিনি সমকালীন কবিতার যাত্রাপথটিকেই তুলে আনার প্রয়াস পেয়েছেন৷ এখানেই গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে৷ কবিতার এ যাত্রা সকল কবিকে ‘শেষ গন্তব্যে’ পৌঁছে দিবে না, একারনেই লোকাল ট্রেন, মাঝপথে কি অনেকেই নেমে যাবেন? তাহলে ট্রেনের শেষ গন্তব্যের যাত্রী কে বা কারা হবেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেবল মহাকালই দিতে পারে৷ কবি ও সম্পাদক তানজিন তামান্না ‘সাম্য রাইয়ানের অশেষ যাত্রার পথ’ শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “গদ্যগুলোতে আহ্বান আছে, আছে জার্নির বিস্ময়— ভাবনা এবং ভাবনায় উঠে আসা যাপিত রাত্রির ঘুমের দ্বন্দ্ব অথবা অন্তর-দ্বন্দ্ব। ভুলে যাওয়া সূত্র মেলাতে গিয়ে মিলে যাবে কোনো কোনো স্বপ্ন। স্বপ্নের ভেতর দ্যাখা যাবে— কোনো এক জমে যাওয়া প্রেম।” গদ্যগুলোর শিরোনাম কাব্যিক— ঘোরজাগানিয়া৷ শিরোনামগুলোই রহস্য তৈরি করে— পাঠককে আকর্ষণ করে৷ লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে আরেকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরন করতে পারছি না: “কোনো কবিতা পড়ার সময় হয়তো আমার ছেলেবেলার কোনো ঘটনা মনে পড়েছে, কোনো এক রাতের দৃশ্য মনে পড়েছে, কিংবা নতুন কোনো চিত্রকল্প ভেবেছি সেইসবই বর্ণনা করে গেছি৷ কোনো রাখঢাক নাই৷ যে ভাবে বাক্য উপস্থিত হয়েছে, সে ভাবেই তাকে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি৷ ফলে এ গদ্য কখনো কবিতার মতো এগিয়েছে আবার কখনো গল্প, আবার কখনো প্রবন্ধের রূপ ধারণ করছে হয়তো একটি অনুচ্ছেদে৷” গ্রন্থটিতে আছে অসংখ্য কাব্যিক পংক্তি, যা পাঠককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ঘোর তৈরি করে৷ কয়েকটি উদ্ধৃত করছি৷ যাতে করে পাঠক কিছুটা হলেও ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ গ্রন্থের স্বাদ পেতে পারেন৷ ১৷ ছাই উৎপাদন ছাড়া যে আগুনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তার মূল্য ভেবে ভারাক্রান্ত মন৷ এই ভার বয়ে পৃথিবীর ওজন বেড়ে যাচ্ছে৷ মন ভালো হও— মন ভালো হও— সুস্থ-সহজ হও— প্রেমের শিকার হও—৷ ২৷ কতোটা রোদের সাথে মিশে যেতে পারো তুমি মেঘ? ৩৷ জুয়ায় হেরে গেছে তুমুল কুয়াশাভোর; সব খুইয়েছে- নিঃস্ব হয়েছে। কাউকে লিখব না চিঠি। তোমার ট্রেন ধরবার তাড়া। চলে যেতে হলে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে হয়। তোমার ব্যাগে কি? ব্যাগভর্তি গুডবাই নিয়ে চললে কোথায়? ৪৷ চকচকে ব্লেড দিয়ে অনবরত কাটছিল সে স্মৃতির পাউরুটি। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তাকাচ্ছিল না এদিকে-সেদিকে, কোনোদিকেই; একমনে কাটছে তো কাটছেই। ওদিকে আরেক দৃষ্টান্ত; ব্লেড দিয়ে জলকাটার মতো করে চলছে ভূমিভাগপ্রক্রিয়া। এরকম আরো অনেক উদ্ধৃত করা যেতে পারে৷ যেখানে কবিতা-মুক্তগদ্য-গল্প মিলেমিশে গদ্যের নতুন মোহনা সৃষ্টি করেছে৷ এই মোহনায় অবগাহনে পাঠকমননে নতুন পাঠঅভিজ্ঞান সৃষ্টি হয়৷
সাম্য রাইয়ানের কাব্যপৃথিবীর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত স্বর ও শৈলী
প্রবাল চক্রবর্তী সাম্য রাইয়ান অনেকদিন ধরেই ফেসবুকে আমার বন্ধু হিসেবে আছেন। যদিও কখনো কথা হয়নি, তবুও দূরবর্তী অবস্থানে থেকেও জানতাম সাহিত্যের একজন প্রবল অনুরাগী লেখক তিনি, পাশাপাশি সম্পাদক হিসেবেও বেশ সুনাম রয়েছে তাঁর। আমি সোচ্চারে বলব, এই সময়ে একজন কবি একান্ত বেপরোয়া নাছোড়বান্দাভাবে নিজের কবিতাটা লিখে চলেছেন, তিনি সাম্য রাইয়ান। তাঁর কাব্যপৃথিবী কতটা গভীর ও শক্তিশালী, সেটি সম্প্রতি তাঁর কবিতার বই, ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ (২০২০) না পড়লে হয়তো জানাই হত না। সত্যি বলতে কি, আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই কবি এ সময়ের কবিতায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। আমি দৃপ্তভঙ্গিতে বলব, তাঁর কবিতা কোনো বিশেষ স্কুলিং বা গোষ্ঠীর ছাপ বহন করে না। কবিতার ভাষা ও ভাবনা, বিষয় ও প্রকরণে তিনি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। উপস্থিত গ্রন্থটিতে তার নিদর্শন সুপ্রচুর। এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ, যা প্রকাশিত হয়েছে ‘ঘাসফুল’ প্রকাশনী থেকে। ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির মোট ৪৮টি কবিতা নিয়ে ৬৪ পৃষ্ঠার বই। শব্দ ও শব্দার্থের খেলায় দক্ষ এই কবি বইটির উৎসর্গ ফ্ল্যাপ ও উৎসর্গ পাতা থেকেই নিজের পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে শুরু করেছেন৷ কদাপি অটোমেটিক রাইটিং নয়, অথচ যেন কবিতাই কবিকে চালিত করছে, লিখিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। যেমনটা তিনি ‘উড়ন্ত কফিন’ কবিতার প্রথম ছত্রেই বলেছেন, “আমাকে লিখেছে কেউ, তার পরে বাজারে ছেড়েছে৷” নিজের জীবনকে খোরাক করেই যেন লিখে যাচ্ছেন এই কবি। উল্লেখ্য, বইটির উৎসর্গ পাতায় তিনি লিখেছেন, “সোনামুখী সুঁই থেকে তুমি / চুইয়ে পড় সুতো হয়ে / নিচেই বিদ্ধ আমি / সেলাই হই তোমার সুতোয়৷” খুবই লিরিক্যাল ফর্মে লেখা এই উৎসর্গ পড়লেই যে শীতল পরশ হৃদয় আলোড়িত করে, তা বলাই বাহুল্য৷ বইটির ভেতরে এরকম অনেক লিরিক্যাল কবিতা আছে৷ কিন্তু যেমনটা ৮০ দশক বা তার পরবর্তী সময়ে সাধারণত দেখা যায় যে, গভীর উপলব্ধিহীন লিরিকের ছড়াছড়ি চারদিকে, দ্বিতীয় দশকের কবি সাম্য রাইয়ানের কবিতা তার একদমই ব্যতিক্রম৷ তিনি এতটাই গভীর অনুভূতির কথা লিখেছেন সহজিয়া ভঙ্গিমায় যা অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যঞ্জনা ছাপিয়ে নতুনতর এক নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম। এরকম শব্দের খেলা, শব্দার্থ নিয়ে খেলা আমরা গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের মধ্যে প্রায়শই লক্ষ করি, যা সাম্য রাইয়ানের কাব্যভাষার একটি লক্ষণীয় চরিত্র। অনেক নতুন শব্দও চোখে পড়ে, যা কবিসৃষ্ট বলেই অনুমান করি৷ যেমন: ‘মহুপাড়া’৷ একথা সকলে জানি যে, পাথর শিল্প নয়, কিন্তু পাথরের মধ্যে শিল্প লুকিয়ে থাকে। একজন ভাস্কর পাথরের অপ্রয়োজনীয় অংশকে কেটে ফেলে দিয়ে সেই শিল্পকে বের করে আনেন, তখন তা ভাস্কর্য বা প্রতিমারূপে প্রকট হয়। একজন কবির লেখকের কাজও একই৷ তাকে জানতে হয় কবিতার শরীরে শব্দ স্থাপনের অনন্য গোপন কৌশল৷ শুধু তাই নয়, তাকে আরো বেশি জানতে হয়, অপ্রয়োজনীয় শব্দ কীভাবে বাতিল করে কবিতাখানি এগিয়ে নিতে হবে৷ এক্ষেত্রে সাম্য রাইয়ানের পারঙ্গমতা নজর কাড়ার মতো৷ তিনি মাত্র দুই পংক্তির ‘শিকার’ নামীয় কবিতায় যত বিস্তৃত বিষয় বলে দেন, তাতে অধিক কথার কোন দরকারই পড়ে না৷ “প্রার্থনায় শিকার করো প্রিয়তম হরিণীকেতার ভেতরে বইছে অনন্ত ঝরণাধারা!” এই দুই পংক্তি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়৷ এ নিয়ে বিস্তর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা মাত্র দুই পংক্তির জাদুতে কবি উপস্থাপন করেছেন৷ এই বইটি মূলত মানবের মধ্যেকার বহুবিধ সম্পর্কের বয়ান রচনার একটি কাব্যিক প্রয়াস; এর ভাষাভঙ্গি, স্বর ও শৈলী সম্পূর্ণ নতুন। প্রায় প্রতিটি কবিতায় নিজস্ব মগ্নতার ছাপ স্পষ্ট। চেতনা ও মগ্নচৈতন্যের খেলায় তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে কখনো অন্ধকার, কখনো উচ্ছল আলোকধারা। এই বই পাঠকালীন সময়ে কবি সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ থেকে ইন্টারনেটে সার্চ করে তাঁর অনেক কবিতা ও মুক্তগদ্য পাঠের সুযোগ হলো৷ এবং এরই মধ্যে আমাদের আলোচ্য বইটি নিয়ে কবির একটি বক্তব্য আমার নজরে এল, যা আমার পাঠানুভূতিকেই সমর্থন করছে বলে অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করছি৷ বইটি প্রসঙ্গে কবি বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক দেশ রুপান্তর পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “কবিকে আমার কেবলই মনে হয়-জীবনব্যাপী সম্পর্কশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করে চলা ব্যক্তি। সে নানান সম্পর্ক-প্রাণের সাথের প্রাণের, প্রাণের সাথে প্রাণহীনের, ক্ষুদ্রপ্রাণের সাথে মহাপ্রাণের-সকল সম্পর্ক। এই প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন-রক্ষা-চ্ছেদ-বিকাশ বিষয়েই মনে হয় জীবনের সকল গবেষণা। সেই সম্পর্কশাস্ত্রেরই এক রূপ ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’।” এই বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি:১৷ “বানান ভুল হলে কাছের মানুষও কাচের হয়ে যায়৷” (জীবনপুরাণ) ২৷ শীতকাল ব্যর্থ হোক তোমার গ্রীষ্মের কাছে৷” (উষ্ণতায়, উত্তাপে) ৩৷ “বিশ্বাস রাখার মতো কোনো মেশিন এখনো তৈরি হয়নি৷” (তোমাকে, পুনর্বার) ৪৷ “এতো নীল ছড়িয়ে দিলাম প্রেমে, ভালোবেসে৷” (ভাষাহীন) ৫৷ “দূর থেকে দূরে হারালো যে প্রাণময়,/ আমি তাকে… তার সমূহ হৃদয়ে ভ্রমণ করেছি৷” (একে একে একা হলাম) শুধু তা-ই নয় কবিতার অন্তঃশরীরে ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, পুরাণ ইত্যাদির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার সাম্য-বর্ণিত এইসব মানব-সম্পর্কের ব্যাকরণে নতুন ও নির্ভীক একটি মাত্রাও যোগ করে। যেমন ‘জীবনপুরাণ’ কবিতায় কবি লিখেছেন— “জীবন বন্দী ক’রে মৌল আঙিনায়বোকাচন্দ্র ধর্মরথে চেপে অমরত্ব চায়৷জেনেও জানে না কেন দূরন্ত লাটিমধর্মের সীমানা আছে, মানুষ অসীম৷” খুবই আন্তর্জাতিক সুর আছে সাম্যের কবিতায়। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বর এতটাই আন্তরিক-মৌলিক যে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনেক নামজাদা কবিকে লজ্জা দিতে পারে। দার্শনিক প্রত্যয় আছে তাঁর কবিতায়৷ একজন কবিকে অবশ্যই দার্শনিক হতে হয়৷ সাম্যর কবিতায় দার্শনিক ডিসকোর্সের গভীর কথাও অত্যন্ত সহজ-সাবলীল হয়ে উঠে আসে৷ যেমন—১৷ “অনেক কলা ঝরায়ে শেষতক বুঝেছিআনন্দের কোনো মাথামুণ্ডু নাই৷” (বোধিদ্রুম) ২৷ “মনের ভেতরে আছে প্রকৃত শরীর, যাকে কখনোই জানা হয় নাই৷“ (প্রকৃত শরীর) ৩৷ “বিক্রেতার কাছে সকলই সমান, সমমুদ্রার৷” (তুমি ডাকলে না, এলেও না) ৪৷ “ঘুমন্ত মার্বেল, যা ক্রমশ গড়িয়ে যাচ্ছে৷” ৫৷ “এ জীবন, জড়িয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া অবশিষ্ট কিছু নয়৷” (লতা) ৬৷ “অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাপিত আমাদের প্রতিটি জীবন৷” (জীবনপুরাণ) তাঁর কিছু পংক্তি, কবিতা এমনই শক্তিশালী যে পাঠকের মস্তিষ্কে নিরন্তর অনুরণন সৃষ্টি করে এবং পাঠকের কল্পনার দ্বার উন্মোচন করে দেয়৷ পাঠক নিজ কল্পনার ডানা মেলে উড়তে পারেন, যখন ‘কবর দেখতে দেখতে’ কবিতায় কবি লিখেন, “চিবুক থেকে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটি যুদ্ধবিমান” তখন পাঠককে ভাবতেই হয়, কবির কল্পনার সাগরে ভাসতেই হয়৷ এ ভাসান মহানন্দের৷ পাঠকের চেনা জগত, চেনা কবিতা, চিন্তার জগৎকে উসকে দিতে সক্ষম তাঁর কলম। তাঁর বিষন্নতা, তাঁর নির্জনতা, তাঁর প্রেম এই সময়ের বাংলা কবিতার একটা মাইলফলক তৈরি করছে। তাই সাম্য রাইয়ানের কবিতা আরও ব্যাপকভাবে পঠিত ও আলোচিত হওয়া উচিত বলে মনে করি।
ব্যক্তিগত থেকে সামগ্রিক অন্তর্দহনে পরিণত হয় যে কবির কবিতা
ড. মধুমঙ্গল ভট্টাচার্য “মাত্র আটাশ বছর গেল, অথচঘুরে ঘুরে মনে হয় কয়েক শতাব্দী আগেহারিয়ে গিয়েছিলাম ধূ ধূ রাস্তার পরে।রাত-দিন একাকার, শহর-গঞ্জ-গ্রামদেখেছি সকল— পরিমিত পদক্ষেপে। অবশেষেনিক্ষেপিত আমি নষ্ট রেস্তোরাঁয়।”(আটাশ বছর পর/ সাম্য রাইয়ান) আটাশ বছর বয়সে কবি সাম্য রাইয়ান নিজেকে নষ্ট রেস্তোরাঁয় আবিষ্কার করেছেন৷ এই কবিতাটি পড়ার পর একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল৷ আমি ভাবছিলাম— একজন মানুষ যদি জীবনের আটাশ বছর অতিবাহিত হবার পর নিজেকে নষ্ট রেস্তোরাঁয় আবিষ্কার করেন তাহলে তার অনুভূতি কেমন হতে পারে৷ ‘আত্মকথা’ প্রসঙ্গে কবি অরুণেশ ঘোষ একবার বলেছিলেন “১১ বছর বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম জীবন নিরর্থক। বেঁচে থাকা উদ্ভট। জন্ম অকারণ ও আকস্মিক। ছক আগে থেকেই করা আছে, জন্ম মাত্রই দুটো শ্রেণীর যেকোনো একটাতে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। হয় দাস না হয় প্রভু। হয় অত্যাচারিত না হয় অত্যাচারী। শোষক নয়তো শোষিত। মানব সভ্যতা এর বাইরে কিছু জানে নি।” কোথায় যেন সাজুয্য খুঁজে পাচ্ছি দুই দেশের এই দুই কবির অনুভূতির মধ্যে৷ যদিও পুরোপুরি মেলানো যাচ্ছে না, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে অরুনেশ ঘোষ আত্মকথায় যা বলেছেন, সাম্য এত বছর পর পরিমিত ভঙ্গিতে তার নতুন উপলব্ধি প্রকাশ করতে একই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন৷ দ্বিতীয় দশকে আত্মপ্রকাশকারী কবি সাম্য রাইয়ান অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা কবিতায় নিজস্ব ভাবনার বীজ বপন করতে সফল হয়েছেন। আজকের এই অস্থির সময়ে দালালি আর দলাদলি করে সহজেই সাফল্য লাভের বিষয়টি মানুষ আত্মস্থ করে নিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে যথার্থ কবি হয়ে ওঠা কোনকালেই সম্ভব নয়। সেজন্য নিজস্ব এলেম থাকা দরকার। সাম্য সেই অগ্নি পরীক্ষায় কর্ণের মতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন৷ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্রান্তজেলা কুড়িগ্রামে বসেই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সাম্যের গ্রন্থ সংখ্যা দশ। পর্যায়ক্রমে তাঁর রচনাগুলি হল: কাব্যগ্রন্থ— • বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা (২০১৬) • হলুদ পাহাড় (২০১৯) • মার্কস যদি জানতেন (২০১৮) • চোখের ভেতরে হামিংবার্ড (২০২২) • লিখিত রাত্রি (২০২২) • হালকা রোদের দুপুর (২০২৩) গদ্যগ্রন্থ— • সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট (২০১৫) • লোকাল ট্রেনের জার্নাল (২০২১) সম্পাদিত গ্রন্থ— • উৎপলকুমার বসু (২০২২) • জন্মশতবর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০২৩) কেবলমাত্র সংখ্যার নিরীখে নয়, বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও সাম্য রাইয়ান ক্রমশই নিজের স্বকীয় শিল্প প্রতিভা মেলে ধরেছেন অনায়াসে। সাম্যের প্রথম কবিতাপুস্তিকা পরিচায়িকা অংশে যথার্থই লেখা হয়েছিল, “ঘটনার বয়ানসূত্র থেকে আলো ছড়ানো একটা কথামুখ দেখতে পাচ্ছি। নদীফলে ভেসে যাচ্ছে তীর, ঘনবুনটের জাল ভরে উঠছে ব্যর্থমাছে। গানবাহী শামুকপুত্র চিনে নেবে মহাকাল, পৃথিবীর ছায়া। নিবিড় দৃশ্যের মিউজিয়ামে দাঁড়িয়ে তবু একজন কবি, একা; তোমাপৃষ্ঠের নিচে প্রাণপ্রবাহের উপর একই সমতলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। গ্যালনসম বিষাদ শুধু বেরিয়ে আসে কলমের ডগা দিয়ে। একবার বিষাদ লিখে আমি কলমের নিব ভেঙে ফেলি। পূর্বনির্মিত পশমী জঙ্গল থেকে কাগুজে শরীরে শাদায় লেপ্টে যায় দীর্ঘ হতাশার মতো ম্লাণ উপাখ্যান। কী করে নির্মিত হয় কবিতাগাছের ফল; মানুষের কাছে আজ অব্দি সেসব অমীমাংসিত বিষ্ময়!” সাম্য রাইয়ানের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য এবং কাব্যকুশলতা সত্যিই বিষ্ময় জাগানিয়া৷ প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা’ থেকেই তিনি পরিণত কবি-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি লিখেছেন,“বিগত সময়ের কর্মকে কেটেকুটে, ব্যাপককাটাকাটি হলেও নতুনে রয়েছে ছাপ, পুরানের চিহ্নিত হচ্ছে ধীরে, না-লেখা কলম, তেলের কাগজতা-হোক, তবু আবিস্কৃত হোক প্রকৃত যাপন… আদিম শ্রমিক আমি; মেশিন চালাই।মেশিনে লুকানো আছে পুঁজির জিনচালাতে চালাতে দেখি আমিই মেশিন”(মেশিন) কিংবা “এইখানে আমি একা, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক।তারপরও সে আছে এখানেইমাড়াইকৃত চালের মতো শুভ্র শরীর নিয়েএখানেই কোথাও সে রয়ে গেছেঅপ্রকাশিত প্রজাপতি হয়ে। শাদা প্রজাপতি এক জীবন্ত এরোপ্লেন।হাত বাড়ালেই তার উন্মাতাল গানউঠে আসে হাতে কান্নার সুর।”(শাদা প্রজাপতি) অথবা ‘নৈশসঙ্গী’ কবিতার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায়, যেখানে কবি লিখেছেন,“এই রাস্তা চলে গেছেঅধিকতর নিঃসঙ্গতার দিকে৷পুরনো শহরে বয়সী শামুক, হেঁটে যায়অক্ষয়দাস লেন পেরিয়ে— পকেটে মুদ্রা নাচে৷গলির মুখে নাচে পুলিশের গাড়ি৷ বেদনাহত কোকের বোতল ছুঁয়েনৈশ বন্ধুর সাথে ট্রাফিক পেরিয়ে হাঁটি৷অদেখা প্রতিবেশিনীর নিঃশ্বাস কাঁধেটের পাই, আমরা তখন মেঘের ছায়ায়অন্ধকার, বৃষ্টিহীন গ্র্যাণ্ড এরিয়ায়!” এভাবেই ব্যক্তিগত পরিসর থেকে রাষ্ট্রব্যাপী অদ্ভুত অন্ধকারের নগ্নচিত্র অনায়াসেই ফুটে ওঠে সাম্যের কবিতায়। তিনি তাঁর ‘শাদা প্রজাপতি’র মতো চোখে চারপাশের চেনা জগৎটাকে এমনভাবে অবলোকন করেন যা মননশীল পাঠককে তাঁর কবিতার মাধ্যমে অনির্বাণ কল্প-বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। রাষ্ট্র-পুলিস এবং আগ্রাসনকে কত সহজ-সাবলীলভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আগ্রাসনের বিপরীতে শিরদাঁড়া টানটান করে কবি এক বাক্যে সকল সাম্রাজ্য-অহং চুরমার করে দিলেন! সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, কবিতায় সাম্য রাইয়ানকে একরৈখিক আঙ্গিকে চিহ্নিত করা যায় না৷ কবিতায় তিনি বহুরৈখিক, একেকটি কবিতার বইয়ে তাঁকে আমরা নতুন রূপ-বর্ণে আবিষ্কার করি৷ এটি আসলে কবির নিজেকে আবিষ্কারেরই প্রক্রিয়া৷ সাম্যের কবিতার বইগুলো পড়তে পড়তে আমরা ক্রমাগত যেন নতুন ধরণের আবিষ্কার প্রক্রিয়ার সাথেই পরিচিত হতে থাকি৷ ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ বইয়ে আমরা যে ফর্মের কবিতার সাথে পরিচিত হই— তা অত্যন্ত লিরিকাল, উপচে পড়া প্রেম—৷ ৬৪ পৃষ্ঠার এ বইয়ে কবিতা আছে ৪৮টি৷ সাম্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, গভীর দার্শনিক অভিব্যক্তি তিনি অতি সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে পারেন৷ মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথাখানি— ‘সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে / সহজ কথা যায় না বলা সহজে৷’ সহজ কথা সহজে বলারই শুধু নয়, বরং জটিল-গভীর কথাও সহজে বলার অনায়াস ভঙ্গিমা সাম্য রপ্ত করেছেন৷ যা আমাদের বিস্মিত করে৷ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ‘জীবনপুরাণ’ কবিতার পংক্তি— “বানান ভুল হলে কাছের মানুষও কাচের হয়ে যায়!” এ যেন আমার-আমাদের মনের কথা৷ কত সহজ, সাবলীল; অথচ এর গহীনে লুকায়িত গভীর দর্শন৷ যার উপলব্দিক্ষমতা যত শক্তিশালী, সে পাঠক সাম্যের কবিতা তত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন৷ এপ্রসঙ্গে সাম্য নিজেই লিখেছেন ‘জীবনপুরাণ’ কবিতায়— “গভীর, সহজ সুরে দর্শন জাগে / অনুরাগে৷” ‘শিকার’ কবিতায় কবি লিখেছেন— “প্রার্থনায় শিকার করো প্রিয়তম হরিণীকে; / তার ভেতরে বইছে অনন্ত ঝরণাধারা!” মাত্র দুই পংক্তি! মাত্র দুইটি! অথচ কী গভীর বক্তব্য৷ প্রিয়তম হরিণীকে শিকার করতে বলছেন কবি৷ অথচ হিংস্রভাবে নয়, প্রার্থনার মতো করে৷ শিকারের যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম, এই কবিতা পাঠের পর সেই রূপ আমাদের সামনে ভেঙেচুড়ে যায়৷ যাকে শিকার করার কথা বলছেন, তাকেই তিনি প্রিয়তম বলে সম্বোধন করছেন৷ অর্থাৎ এই শিকার অন্যরকম শিকার৷ এখানে শিকারের হিংস্রতা নেই৷ জখম নেই৷ আসলে আছে প্রেম৷ প্রেম দিয়ে তিনি শিকার করতে চাইছেন, আসলে কবি এখানে ‘শিকার’ শব্দটি নিজের করে নেয়া বা আপন করে নেয়া অর্থে ব্যবহার করেছেন৷ কবি হিসেবে তিনি যথার্থ কাজই করেছেন৷ আগ্রাসন দিয়ে নয়, বরং প্রেম দিয়ে কবি দুনিয়া জয় করার মনোভাব পোষণ করেন৷ এটাই বাংলার আদি দর্শন৷ যা সাম্যের দর্শনের বিশেষ শক্তি৷ তিনি এ বাংলার মাটিবর্তী কবি৷ তাই তিনি ‘গভীর স্বপ্নের ভেতর’ কবিতায় লিখেন— “ফড়িং নয়, ধরতে চেয়েছি ফড়িংয়ের প্রেম৷” ফড়িং প্রতীক ব্যবহার করে কবি এখানে বস্তুকে নিজ কড়ায়ত্ত করার পরিবর্তে ভাবকে আলিঙ্গনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন৷ এ বইয়ের প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই প্রেমের জয়গান গেয়েছেন কবি, জীবনের জয়গান গেয়েছেন৷ এই প্রেম শুধুই মানব-মানবীর নয়৷ অনেকটা সহজিয়া দর্শনের প্রেম৷ প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের প্রতি প্রেম এ বইয়ের প্রধান বিষয়৷ ‘নির্বাসনের বনে’ কবিতায় কবির বৃক্ষপ্রেম আমাদের আশ্চর্য করে৷ কত সাবলীলভাবে তিনি বৃক্ষকে মানুষেরই সমান মর্যাদায় ভালোবাসা দিয়েছেন তা টানাগদ্যে রচিত কবিতাটি পাঠ করলে বোধগম্য হয়—“গাছটা অসুস্থ; ওকে ডাক্তার দেখাবো। হাতে অনেক কাজ এখন। তোমার কাছে ফিরে নদীমাতৃক হবো। সুবাসিত পাতাবাহারের কাছে কয়েকটা আকাশ জমা আছে; রাত গভীর হলে সেই গল্পটা শুনতে হবে আবার। কেন যে আসে উদগ্র শুক্রবার; সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যায় আমার; কোনোকিছু ঠিক থাকে না! পঠিত গানের নাম ধরে ডাকি তবু কোথা থেকে উঠে আসে সব ব্যর্থ কবিতামালা। যে অসহ্য ওষুধবিক্রেতা জানে না মেঘেদের প্রকৃত বানান, তাকেও তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ি যেতে হবে। এদিকে আমি একটা খসে পড়া নক্ষত্র পকেটে জমা রেখেছি; বৃষ্টি ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিলো!” এর পরের কাব্যগ্রন্থ ‘লিখিত রাত্রি’র কবিতাগুলো আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্রে ‘চোখের ভেতরে হামিংবার্ড’ বই থেকে একদমই ব্যতিক্রম৷ আলাদা শিরোনামহীন, সংখ্যা চিহ্নিত ৫৫টি কবিতা নিয়ে এ বই কবির বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে৷ এ বইয়ের প্রতিটি কবিতা পাঁচ পংক্তি বিশিষ্ট এবং প্রতি পংক্তি ১৮ থেকে ২০ বর্ণ বিশিষ্ট৷ এ যেন আরেক নতুন কাব্যধারা, যা সাম্যের নিজস্ব ভঙ্গিমা৷ পুরো বইতে সাম্য আশ্চর্যভাবে স্ব-মেজাজ ধরে রেখেছেন৷ একই সুর-ভঙ্গিমায় পুরো বই তিনি সমাপ্ত করেছেন৷ এ সত্যিই রাত্রির গল্প৷ অনেক রাত নাকি একটিই রাত অনেক চোখে? বইটি পড়তে পড়তে এ প্রশ্নই আমার মাথায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিলো৷ সবগুলো কবিতায় রাতের বিবরণ দিয়েছেন কবি৷ আসলে তিনি রাতই লিখেছেন৷ নামকরণ শতভাগ সার্থক৷ বইটির ফ্ল্যাপ উদ্ধৃত করি— “পঞ্চান্ন পর্বের এই সিরিজজুড়ে রাত্রির গল্প— অনেক রাত— রাতের পর রাত যা লিখিত হয়েছে— এক রাত্রিতে এসে তা পূর্ণরূপ নিয়েছে৷ সেখানে বিস্তৃত হয়েছে রাত্রির নিজস্ব আসবাব— কুকুর, পতিতা, নাইটগার্ড, পাখি, কবি, প্রেম, বিবাহ, ট্রাক ড্রাইভার…!” কবি সাম্য রাইয়ানের হাতে যে রাত লিখিত হয়েছে, কেমন তার রূপ? মলিন, মোলায়েম, কোমল? নাকি রুক্ষ, কঠোর, কঠিন? এর উত্তর খুঁজতে আমরা পাঠ করবো তাঁর কবিতা— “যেতে যেতে পথে, মধ্যরাতে; কুকুর, পুলিশ ওবেশ্যাকে নিঃশব্দে বলি: পথ আটকানো নিষেধ। এরাত শুধুই প্রেমিক, কবি ও পাগলের। গান শেষেদ্যাখো পুরোটা জুড়ে শুধু ছেড়া পাতাফুল পড়েছিলো যা, সকল খারিজ হলো অন্ধবাগান থেকে৷”(ঊনপঞ্চাশ) উন্নত মন্দিরের কাছে প্রার্থনা করেছি – এ রাতপূর্ণদৈর্ঘ্য হোক; নীলাভ ভায়োলিন স্থায়ী হোকআদরের করোটিতে। মৃত শরীরের স্মৃতিবাহীসকল জাহাজ জেগে উঠুক মানুষমেশিনেরঅযৌন শিরদাঁড়ায় টিক টিক শব্দঘন্টা হয়ে।(তিন) এরকম আরো আরো কবিতাংশ উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করছে৷ এই কবিতাগুলো পড়তে শুরু করলে এমনই ঘোর তৈরি হয়, যা থেকে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর৷ আমার ধারণা, এ বইটি ক্ল্যাসিক কবিতার রূপ পেতে পারে৷ শঙ্খ ঘোষের ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’, উৎপলকুমার বসুর ‘পুরী সিরিজ’, ভাস্কর চক্রবর্তীর ‘জিরাফের ভাষা’ যেমন রচনার দীর্ঘকাল পরেও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে সক্ষম, সাম্য রাইয়ানের ‘লিখিত রাত্রি’ও সেসরকম দীর্ঘকাল পরেও অগ্রসর পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে বলে আমার ধারণা৷ আমি প্রথমবার বইটি পড়ে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না দ্বিতীয় দশকে এত শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছে৷ নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার যে প্রবণতা সাম্যের কবিতায় বিদ্যমান, পরবর্তী কবিতার বইগুলোতেও কবি তাঁর সে সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন এইই প্রত্যাশা৷ চেতনার ক্যানভাসে কবির আঁকা অন্তর্দহনের চিত্র আমাদের বিমোহিত করুক আগামীতেও৷
নেশায় চুর এক জেলে: শব্দমাছ তুলে আনেন অবচেতনের বিপজ্জনক সীমা থেকে
ফেরদৌস লিপি কবি সাম্য রাইয়ানের ‘হালকা রোদের দুপুর’-এ আপনি ঢুকে পড়ুন—ঘোরলাগা দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য ঘন ঘাসের জঙ্গল পেয়ে গেলেন, হাঁটছেন, শুনছেন— পদশব্দ বা ঘাসমাড়ানো খসখস, পাঠক আপনার মনের তুলোট ত্বকে বিঁধে যাচ্ছে তারই অভিজ্ঞতার প্রেমকাঁটাগুলো। সাম্য— অভিজ্ঞতাগুলো তাঁর এমন বাস্তব—যেন পুড়ে যাচ্ছে কোনো সিগারেট, আর ধোঁয়ার আকারে জন্মাচ্ছে অবধারিত—কবিতা। কবিতাগুলো যেন উঠে আসে শব্দের পেট চিড়ে মাকড়সা-সুতার মতো মুহূর্তে পাঠককে জড়িয়ে ধরে। এবং ধরেই রাখে, আবেশিত ক’রে ঠিক চিরুনি+কাগজ রিলেশনশিপ—চুম্বকিত ক’রে। তাঁর কবিতা পাঠে ‘অন্য এক জীবন’ বাস্তব হয়ে ওঠে—পাঠকের কাছে মনে হয় যেন— তিনি লিফটের সেই ‘আরোহী’ যিনি নিজেকে ওজনহীন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক হোঁচটেই নিজেকে ওজনযুক্ত ‘বস্তুপিন্ড’ মনে করেন আর পুনরায় ফিরে আসেন গতানুগতিক জীবনে, ঐ কিছুকালব্যাপী ধাবমান লিফটে হঠাতই বাস্তব হয়ে ওঠে ভিন্ন এক অনুধাবন, সেই ‘অন্য এক জীবন’ যা এক ওজনশূন্য শূন্যতা। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ থেকে শব্দে উৎসারিত ভাবনা পাঠককে তাড়িত করে— যেদিকে ধূপ ও ধোঁয়া উড়ে যায়। আমাদের জানা জগতের বাইরেও নিশ্চিত আরও জগতকে চকিতে দৃশ্যায়িত করে। সাম্যের কবিতাগুলো পক্ব, সহজ এবং গভীর। আছে দার্শনিক আহবান এবং পিছল সূচিমুখ কেবল ঢুকে পড়া যায় ভাবনায় আর ঢুকে যাওয়াটাও অবধারিত কেননা পাঠকের জন্য দ্বিতীয় কোনো উপায় রাখেন না কবি সাম্য। আর শব্দগুলো ধাবমান ক্ষুরের গতিজড়তার মতোই অসাবধানে ভেঙে দেয় সমস্ত সচেতন বোধ পাঠকের। তার কিছু পংক্তিকে আপাতভাবে মনে হতে পারে সম্পর্কহীন কিন্তু গভীরে অব্যর্থ এক টান ক্রিয়াশীল থাকে সবসময় চুম্বকের চূর্ণিত গুঁড়োর মতো। আমাদের স্পৃষ্ট করে, হুল ফুটানো অবশ করা পংক্তি “পৃথিবী এক ঢেউ ভুলে যাওয়া নদী” এ যেন বুঝে উঠবার কিছু নয়,সহজাত ভালো লাগা—অথবা রবীন্দ্রনাথের “কবিতা যতটা বোঝবার, মনে গিয়ে ততটাই বাজবার”, স্তব্ধতা ভেঙে এগিয়ে চলা কোকিলের কম্পিত সুর —আমাদের বোধের ভেতরে পৃথিবীর তরঙ্গময় আদিমতম অবস্থার অনুরণন উঠে আসে। কবির সুপ্ত অতীত ঝলকানির মতো ক্ষনিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে যখন অনুভবকে অনুবাদ করেন সরল ভাষায়— “পাখি নেই তবু ডানা ঝাপটানো আছে”। কবির কবিতায় উঠে আসছে সুররিয়ালিস্টিক ভাবনার অতিচেতনা— “ডানা আঁকো— সশব্দে ঝাপটাও” সত্যিই যেন পাঠক দূর থেকে শুনে উঠছে ডানার ঝাপট— উড়ে যাচ্ছে রক্ত-মাংসে নির্মিত কল্পনার অবয়ব। কবির কবিতায় আমরা পাই এক ভিন্ন জগতের প্রতিবেশ, ধরলার প্রতি সুতীব্র স্মৃতিকাতরতা। আর এক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সবকিছুই জগতের— অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো সংগোপন চাপে দূরে দূরে থেকে— তবুও ভেতরে রেখেছে যেন মিলিত হবার এক প্রবল উন্মাদনা—কবির ভাষায় “অনেক মানুষ —যারা হৃদয় ফেলে এসেছে ধরলার জলে, সকলে একত্রিত আজ” —ইন্দ্রীয়জ এমন গোপন অভিজ্ঞতা শেয়ারিংয়ে পাঠকমাত্রই মননে ব্রেকফেইল অভিঘাত নিয়ে আসে। “তোমার উপশিরা যেদিকে এঁকেছে পথ শুধু সেই দিকে যাবো” এই একটি লাইনেই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য আচমকা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কেঁপে ওঠে কিংবা স্মরণে আসে গোপন অঙ্গকে আরও ঘনরহস্যময় করে রাখবার জন্য চেষ্টারত মেরিলিন মনরোর সেই তৎপর হয়ে ওঠা ‘হাত’—যেন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলেই অসতর্ক উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছিল-প্রায় সৌন্দর্যের অপার রহস্য—কিন্তু মুহূর্তেই জেগে উঠলো অতন্দ্র হাত! ধরলার পাড়ে বেড়ে ওঠা কবি কী অদ্ভুত কাব্যিক প্রতিভায় শিরা-উপশিরার উপমায় জীবন্ত বয়ে দিলেন প্রিয় নদীকে—কবিতায়। এবং সাগর অভিমূখী ধরলার প্রবাহের অন্তরালে আমরা দেখে উঠি আমাদেরই অনন্ত জীবনপ্রবাহকে। আমরা আরও ইঙ্গিত পেয়ে যাই নদীর প্রতি মানুষের লালিত প্রেম, মানুষের ক্রমবিকাশ আর জীবনইতিহাসের। “আলিঙ্গনরত ঠোঁট আমার আত্মকথা যেন” এখানে কবি তার অস্তিত্বকে স্প্রে করে দিলেন, আমরা পাচ্ছি তুমুল ঘ্রাণ। প্রেমের অনন্ত বিস্তারিত বিক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে পুঞ্জীভূত, যেন জমাট হয়ে আসা স্বতন্ত্র তারাদের ঘনীভূত অবস্থা। কবির ‘আমার’ শব্দটির ব্যবহারে আমাদের অভিভূত হতে হয়, কেননা এই ‘আমার’ তো ডারউইনের প্রথম হয়ে-ওঠা মানুষ থেকে শেষ হয়ে-যাওয়া মানুষ পর্যন্ত সমস্ত মানবমহাবিশ্বকে বোঝায়! মানুষের প্রেম, কাম-সঙ্গম, জন্ম-মৃত্যুকে বোঝায়! জীবনের প্রতি— পৃথিবীর প্রথম জন্মইতিহাস থেকে পরবর্তী শেষ অবধি—অনন্ত অমোঘ টানকে বোঝায়! শব্দের এরকম অনড় ব্যবহার, পাঠক বুঝে যায় পংক্তির প্রতিটা শব্দ কবির বোধ থেকে চুয়ে চুয়ে পড়া, রসসিক্ত, যথাস্থানে স্থাপিত। আরোপিত কিছু নয় কবিতায় খুব সহজেই চলে আসে ইম্প্রেশননিস্ট থিংক— “অনেক সন্ধ্যার আগে জানা হয়ে গেছে ফসলের নির্জনতম সুঘ্রাণ” —সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ফেরা পাখিদের মতোই উড়ে আসে মৃত্যুর আভাস। ‘নির্জনতম’, ‘সুঘ্রাণ’ শব্দদ্বয় মনে হতে পারে জীবনানন্দীয় কিন্তু তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাস্নাত হয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠকের কাছে বিশিষ্ট। এভাবে একের পর এক শব্দ তুলে এনেছেন, ডুবে-ডুবে, কবি সাম্য রাইয়ান— মহাজগতের রহস্যজাল হাতড়ে হাতড়ে নিজস্ব কাব্যিক দক্ষতায়, অভিজ্ঞতা বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভায়, শৈল্পিক মনন-কলায় নিবিষ্ট থেকে থেকে—সাধনায় তিনি প্রকৃতই এক জেলে যিনি নেশায় চুর হয়ে আছেন আর শব্দমাছ তুলে আনছেন অবচেতনের বিপজ্জনক সীমা থেকে। এ আলোচনায় আমি সাম্যের “হালকা রোদের দুপুর” বইটিতে কলোনিবদ্ধ চল্লিশটি কবিতা পরিবারের দীর্ঘ সারি থেকে কয়েকটির উপর বিচ্ছিন্নভাবে ফোকাস করবো। তার আগে, সাম্য সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেয়া ভালো—তিনি অধুনা দ্বিতীয় দশকের একজন অগতানুগতিক কবি— একারণে যে তিনি স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কবিতা লেখেন না, তাঁর অবচেতনের গর্ভে সচেতন শব্দের জাইগোট ক্রমে পুনঃপুন বিভাজিত হতে হতে পূর্নাঙ্গ আঙ্গিক বা আকারের এক একটা অবিরল প্রবাহের মতো কবিতার জন্ম হতে থাকে, যেন “জৈব অবয়বের নিয়মানুযায়ী উৎকৃষ্ট কবিতার প্রত্যেকটি প্রতঙ্গ, প্রত্যেকটি কণিকা এক অবিভাজ্য অমোঘ সংঘটনের লগ্নতায় আবদ্ধ” —অরুণকুমার সরকার যেমন বলেছেন। জন্মেছেন নব্বই দশকের ডিসেম্বরে, তিস্তা-ধরলার তীরঘেষা কুড়িগ্রাম জেলায় প্রকৃতির নিবিড় কোলে মাথা পেতে বেড়ে উঠছেন। তিনি মূলত কবি, তাঁর নেশা-পেশা-ধ্যান সবকিছুই কবিতাকে ঘিরে। এছাড়া সৃষ্টিশীল গদ্য লেখেন। পাশাপাশি তিনি ২০০৬ থেকে ‘বিন্দু’ (www.bindumag.com) নামক ছোটো কাগজের সম্পাদক হিসেবে শিল্পসাধনার পরিচর্যায় নিবিষ্ট আছেন। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বই তাঁর বেরিয়েছে— ‘বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা’ (কবিতা), ‘সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয়’ (নোটগদ্য), ‘মার্কস যদি জানতেন’ (কবিতা), ‘হলুদ পাহাড়’ (কবিতা), ‘চোখের ভেতরে হামিং বার্ড’ (কবিতা), ‘লোকাল ট্রেনের জার্নাল’ (মুক্তগদ্য), ‘লিখিত রাত্রি’ (কবিতা), ‘হালকা রোদের দুপুর’ (কবিতা)। ব্যক্তিগতভাবে কাছ থেকে তাঁকে জানবার সুযোগ হয়েছে আমার। কবিতার জগতে তাঁর বিস্তৃত বিচরণ আমাকে অবাক করে, এতটা এই তাঁর এত অল্প বয়সে (অনুর্ধ্ব তিরিশ)! যদিও কবিতার ইতিহাসে এসব বয়স-টয়স ব্যাপার কিছু না তবুও বিষ্মিত হতে হয় নতুন কোরে। সাম্য তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা থেকে কবিতা লিখে যান, দেখেছি চায়ের স্টলে বসে বা ধরলার পাড়ে বসে চলতি খোঁশগল্পের ভেতরও চলছে তাঁর নিউরণে কবিতার ক্রিয়া, মোবাইলে লিখে চলছেন কবিতা, পাঠ করে শোনালেন আবার গল্পে ফিরে এলেন! এবং সেসব কবিতা আসলে কবিতাই! এ কারণেই যে “সূক্ষ্ণ মাত্রাতিরেকের সাহায্যে কবিতা বিষ্ময় জাগাবে” এবং মনে হয় তা আমারই (বা যোগ্যতর পাঠকের) “মহত্তম চিন্তার শব্দরূপ”। ‘হালকা রোদের দুপুর’ এর কবিতাগুলোয় কবি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, কল্পনা, আর মননের এক জটিল বুনটকে স্পষ্ট আর সহজ সংঘবদ্ধতায় চিত্রিত করেছেন। কবির ভাবনাসমূহকে পদ্য নয়, ‘গদ্য’ই তাঁর সাবলীল ও সচেতন অনায়াসে নিজের করে নিয়েছে, যেন কবির নয়, এ দায় ছিল গদ্যেরই নিজের। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে শঙ্খ ঘোষের একটি কথা আমাদের মনে হতে পারে: “এমনি এক ঘুমের এই কবিতা, এক অবচেতনের, যে অবচেতন থেকে জেগে ওঠে প্রবহমান মহাসৃষ্টির সঙ্গে নিজের লীনতার মুহূর্তজাত এক প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা।” পাঠক, এরকম এক উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি—“মিনিবাসে চেপে। দুপুর রঙের মিনিবাস। কতোটা বাড়ছিলো বেলা— মনে নেই। ঝলসে যাচ্ছিল বাস— ছালছাড়ানো মুরগির মতো। বিহ্বল মেহগনি গাছের পোশাক। কোথাও দু-একবার ভুলবশত ফুটে ওঠা রোদে দেখা যায়, যেন চকমকি পাথর বিশেষ৷ সারিবদ্ধ পেতলের সানকির মতো ঠোকাঠুকি লাগে— জ্বলে ওঠে আদিম আগুন। এই সুর পরিচিত। এই পথ সকলের চেনা। যার পাশে বয়ে গেছে তুমুল হর্ষধ্বণি আর বেনামী যৌবন।”(হালকা রোদের দুপুর–চার) কবি বলছেন— “দুপুর রঙের মিনিবাস”, সময়টাই কি মিনিবাস? যার রংটা দুপুর রঙের (কমলা রং?)।সময়টা ধাবমান, সত্যি তো! মিনিবাস দৌড়চ্ছে, একটা গন্তব্যের দিকেই যাচ্ছে। ভেতরে নিয়ে সব যাত্রী, সমস্ত জগৎ! তাদের সমস্ত যাপন অধীর এক অপেক্ষায়, গন্তব্য যেদিকে…। কবি নিজেও এক যাত্রী। সমস্ত চারপাশটাই গড়িয়ে যাচ্ছে, মিনিবাস, যাত্রী, ধাবমান—গলে গলে পড়ছে গতি। মনে পড়ে দালির সেই সময়-ঘড়ি “দ্য পারসিসটেন্স অব মেমরি”র কথা। সবকিছু মেনে নিয়েই কবি বসে আছেন এক মহাকালের মুখোমুখি, অধীর অপেক্ষায় তো আমরাও অর্থাৎ সমস্ত জগতই। এবং বাইরে তাকিয়ে আছেন কবি বাসটার জানলা দিয়ে, দেখছেন আবহমান পরিচিত পৃথিবী-জগৎ সময়-বাসের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়চ্ছে কিভাবে সবকিছু বদলে যাচ্ছে গন্তব্যের দিকে যেতে যেতে, বেলা বাড়ছে ভেতর ও বাইরের রঙ পরিবর্তিত হচ্ছে, সবকিছুকে পেটের ভেতর নিয়ে দ্রুত ছুটছে কবির “দুপুর রঙের মিনিবাস” অর্থাৎ সময় স্বয়ং। যদিও সময়ের ভেতর-বাহির বলে কিছু নেই—সেই সুপরিচিত লাইন বারন্ট নর্টনের— “Time present and time past are both perhaps present in time future” অথবা দ্য ম্যাজিক মাউন্টেনের “Time has no divisions to mark its passage,there is never a thunder-storm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.” তবুও অভূতপূর্ব ধীশক্তির দ্বারা কবি সময়কে দুপুরের রঙে চিত্রিত করেছেন, একটা নির্দিষ্ট আকারে সময়কে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন।বিহ্বল মেহগনি গাছ, এবং গাছের পোশাকের কল্পচিত্রে কবির অভিনবত্ব দেখি। এবং পেতলের সানকির মতো ঝলকিত দেখে ওঠা সারিবদ্ধ গাছ, অদ্ভুত! আগেই বলেছি কুড়িগ্রামের নিবিড় ছায়াঘন কোলে বেড়ে উঠেছেন এই কবি। এখানকার নদী, গ্রাম, মাঠ, প্রান্তর কবির পরিচিত। প্রকৃতির এইসব প্রশান্ত পথে আর দৃশ্যের ভিড়েই যেন কেটে গেছে কবির শৈশব-কৈশোর। আর ধাবমান “দুপুর রঙের মিনিবাসের” মতো যৌবনও চলমান। এখানকার আলো, বাতাস, জল শুষে নিয়েই কবি বড় হয়ে উঠেছেন। এক্ষণে স্মরণে আসছে সার্ত্রের “ফেসেস” গদ্যের কথা। যেখানে মানুষের শরীরকে তুলনীয় করছেন তিনি ব্লটিং পেপারের সাথে। ব্লটিং পেপার যেমন কালি শুষে নেয়, মানুষের চোখ-কান-নাক-ত্বক তেমনই শুষে নেয় তাপ, আলো, বাতাস, শব্দ, জল! তাই এসব আবহাওয়া, জলবায়ু কবির অস্তিত্বে মিশে আছে। কিছুতেই তিনি ভুলতে পারেন না সেইসব ফেলে আসা চনমনে রোদ আর দুপুর: “চনমনে রোদে সেলাই করছি জুতো। পুরনো মহিষের আহামরি চামড়া। মুছে যাচ্ছে নাম। একা ঝরে যাচ্ছে হালকা রোদের দুপুর। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হোসেন খাঁ পাড়া গ্রাম। না গিয়েও মনে হয়, পৌঁছে গেলাম সূর্য মাথায় করে। নিবেদক কেউ ছিলো না, গানগুলো পোস্ট হয়ে গেছে। তুমি কিছু পোস্টকার্ড দিও জিপার ভাঙিয়ে। হারানো মেটাফোর খুঁজে ফিরিয়ে দিও ক্রুশবিদ্ধ নারীদের নামে৷”(হালকা রোদের দুপুর–আঠারো) এর অন্তর্বস্তু আসলে কবির নিঃসঙ্গতা আর স্মৃতিচারণ। বোর্হেস তাঁর ‘Everness’ অর্থাৎ ‘নিরন্তর’ কবিতায় যেমনটি বলেন: One thing does not exist: Oblivion. বিস্মৃতির কোনো অস্তিত্ব নেই, কেননা মহাবিশ্বই একটি স্মৃতি, একটি চেতনা। আমরা মহাবিশ্বের অংশ, আমরা নিজেই মহাবিশ্ব, এবং সেই স্মৃতি ও চেতনার অভিব্যক্তি আমরা। সাম্য কবিতায় তুলে আনেন তাঁরই ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা, অত্যন্ত সচেতন থাকেন সেই সৃষ্টির সময়। তাঁর অবচেতনের স্পেস ঢেকে দেন সচেতনতার মোটা আবরণে। এবং বিষয়বস্তু থেকে যারপরনাই নিজে থাকেন দূরে। আমাদের মনে পড়তে পারে “অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ” এর কথা।যেখানে ব্যক্তিক আবেগ চিরন্তনতা পায়। আর এরকম ব্যক্তিক আবেগ বা কল্পনা মিশে যায় নৈর্ব্যক্তিকতার সাথে, বুদ্ধি বা প্রতিভার ঘন আড়ালে। এই কবি এভাবে চিরন্তনতার মোড়কে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেন দৃষ্টিগ্রাহ্য আবেগ যা তাঁরই মূহুর্তের অভিজ্ঞতাজাত:“দগ্ধ হচ্ছে বন, আর তুমি ডুবে যাচ্ছো। এ কেমন ঋতু! তীর্থবনে—কৃষকের মৃত্যু ফুটে আছে রক্তিম কাঁটায়। ধ্বণিহীন, শোকবার্তার কাছে দৈব অনুরোধ, অনির্বাণ প্রেমিকার মতো জড়িয়ে দাও ফসলের ক্ষেতে। যা কিছু উজ্জল মোড়কে, ঘ্রাণযুক্ত স্মৃতির পোশাক, খুলে, নগ্ন করে দাও। ঋতুর পাশে নদী। বালু তোলার শব্দ। কৃষকের সমাধিতে রোপন করো দূরাগত ফসলের ঘ্রাণ। তারপর যথারীতি কান্নার দিকে যাও। নিজস্ব চোখের কাছে হাত পেতে ডাকো মেঘমল্লার, বর্ষার মৌসুম।”(হালকা রোদের দুপুর–তেইশ) পৃথিবীর সব দেশের কবিতায়ই চিত্রকল্প এক বিরাট জায়গা দখল করে আছে। আমরা ইমেজিস্ট শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে সবাই অবগত। ফরাসি ও ইউরোপীয় ইমেজিস্ট চিত্রশিল্পী ও কবিদের জানি।চিত্রশিল্প এবং শব্দশিল্পে মূর্ত-ইমেজ মানুষের অনুভূতিকে সহজেই কাঠামোয় রূপ দিতে পারে।এক্ষেত্রে এজরা পাউন্ড যেমন বলেন: “An ‘image’ is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of mind” আমরা আমাদের জীবনানন্দকেও জানি ইমেজের নৈপুণ্যতায় কতটা সিদ্ধহস্ত! আলোচ্য এই কবির কবিতায় নিখুঁত চিত্রময়তায় পাঠকের সামনে দৃশ্যের পর দৃশ্য জীবন্ত হয়ে আসে। এবার এইরকম একটা কবিতা পাঠকের সামনে তুলে দিচ্ছি— “দুপুরে বর্ষা এলো, মধ্যরাতে ফের। জলের তলে অবাক পাহাড়, বিম্বিত বুঝি- নাচে, দুলে দুলে ওঠে পাহাড়চূড়ার ফুল! এমন আনন্দ থেকে দূরে সরে যায় স্মৃতির ঈর্ষা, কিছুটা নির্ভার তবু স্বাদের আড়ালে। পুরনো বনের অধিক সবুজ সমুদ্র বুকে; ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেউ লাজুক ভঙ্গিতে নেচে ওঠে আর বাতাশের সুরে কথা কয়। কিছুটা ঈর্ষা আমাদের বাগানবাড়িতে পোঁতা ছিল। ঘঁষা কাচের মতো প্রেম চলে এসেছিলো নদীর ছন্দে, উদ্বাস্তু পাতার অধিক।”(হালকা রোদের দুপুর–ত্রিশ) সাম্য তাঁর পূর্বসূরিদের সকল সম্পদ যেন আত্মসাৎ করে নিয়ে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন অর্থাৎ নিজস্ব কবিতার সাম্রাজ্য—এরকম একটা দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কবিতার ভূগোলে এসেছেন।সবকিছু ভেঙ্গেচুরে শুরু করতে চান তিনি নতুন করে। তাঁর শব্দ, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, আঙ্গিক, ভাষা এবং ভাব আমাদের সেরকম করেই ভাবায়; আমাদের চমকিত করে, আনন্দিত করে, প্রবহমান সময়কে যেন অবরুদ্ধ করে, একটা অবিচ্ছেদ্য সূতায় গেঁথে রাখে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আমরা অনুভব করতে থাকি এমন কিছু যা আমাদের চিন্তার সীমাকে অতিক্রম করে যায়। যেন একটা সাংগীতিক সুর ভেতরে খেলে যায়; সুতীব্র, অবিচ্ছেদ্য প্রবাহের মতো আমাদেরও সাথে নিয়ে চলে যায় কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আমাদের কাছে সেই সুর আর বোধগম্য নয়, তবু আমরা ভেসে চলি, চলতে হয়। যেরকম লেখেন এই কবি:“কাঠ চেরাইয়ের শব্দ ভেদ করে ফুটে ওঠে দুপুরের রোদ। মাথা তুলে উঁকি দেয় শস্যদানা, প্রান্তরাভার তলে। কিছুদিন আগে নিহত শিশুদের দেখা হলো কমলা রঙের সাথে। সেই শিশু, যারা যীশুর ন্যায় বিস্মিত হন্তারকের ভালোবাসা পেয়েছে। মর্মরধ্বণি শুনেছে দমকা হাওয়ার গর্তে। তুমি বলো দু-একটা সত্যের ঘূর্ণি- দেখাও অলৌকিক ডানা। পৃথিবীর কাছে সকল অনুভূতি জাগতিক আবর্জনা। সকাল অব্দি তার আয়ুর গৌরব। কী ভীষণ ধারালো, তবু মৃত্যুর দাসত্ব। দ্যাখো এইবার দুপুরের রোদ।”(হালকা রোদের দুপুর–চৌত্রিশ) ঠিক এরকম কিছু ভেবেই মোৎসার্টকে নিয়ে হয়তো কিয়ের্কেগার্দ বলেছিলেন একবার: “If ever Mozart become wholly comprehensible to me,he would then become fully incomprehensible to me.” অনুভব কতটা তীব্র হতে পারে! কতটা সংবেদনশীল হতে পারেন কবি, প্রশ্ন থেকে যায়। অবচেতনের কতটা গভীর থেকে উঠে আসে অনুভবের সিসমোগ্রাফিক তরঙ্গ আর সেই কেন্দ্র থেকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে বোধের সচেতন ত্বকে আমাদের—সাম্যের কবিতা পাঠে কিছুটা তার আঁচ করা যায়।এসব অনুভব আসলে অন্তহীন গন্তব্যের দিকে ক্রমে প্রসারমান। এসব অনুভবকে বলা যায় প্রকৃতির আদিমতম মৌল উপাদান। এসব অনুভব যেন নৈঃশব্দে গড়া, ব্রাক বা পিকাসোর বর্ণপ্রাচুর্য্যে ভরা উজ্জ্বল চিত্রপট। কবিতার এরকম পংক্তি কখনো নির্মাণ নয় এসব কবিরই মৌলিক সৃষ্টি। সাম্যের কবিতার অংশবিশেষ:“আমাকে বহন করো নখের মতো, বেড়ে ওঠার যত্নে। উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া এই নভোযান, মেতে উঠেছিলো শব্দে। গন্তব্যের ছায়ায় পেয়েছিলো কোমল পানীয়, বিশুদ্ধ আহার। সবুজ পত্রালি, অপূর্ব ইচ্ছের দিগন্তে কারো খাদ্যকষ্ট নেই৷ নিবিড়তম গাছ উপচে পড়ছে ফলে। ফলাহার অনুভব করো৷”(হালকা রোদের দুপুর–সাইত্রিশ) বোদলেয়ার প্যারিসে একবার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে ভবিষ্যতের শিল্প সম্পর্কে বলেছিলেন যে— “He will be truly a painter, the painter who will know how to draw out of our daily life, its epic aspects and will make us see and understand in colour and design, how we are great and poetic in our neckties and polished boots.”একথা যেকোনো ভালো বা মহৎ শব্দশিল্পীর বেলায় খাটে মনে করি। আলোচ্য এই কবি যখন শব্দরঙে কবিতার ক্যানভাস আঁকেন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখে উঠি যেখানে দৃশ্যমান থাকে জীবনের মহান কাব্যময়তা কিংবা সচেতন পাঠক পিকাসোর “বেতের চেয়ারে স্টিল লাইফ” ছবিটিকে একবার ভাবুন আর ঐ তাতে আঁকা ফরাসি পত্রিকাটির কথা ‘JOU’—যেন প্রবহমান নিত্য জীবনেরই টুকরো প্রমাণ। এবার সাম্যের কবিতা থেকেই এমন এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পড়ে নিতে পারি, যেখানে দেখা যায় কবির নিত্য জীবন হয়ে উঠছে আমাদেরই আবহমান জীবনের কথকতা:“মিছেমিছে। খেলনা বাড়ির গ্রাম। বৃহৎ পরিখা ঘিরে সুরভর্তি গাছ। যেটুকু বিকেল, সেটুকুই ঘুম। ফিরে আসা সকলের নয়। তবুও সন্ধ্যা-ভোরে তৈরি হচ্ছে বাড়ি। ধর্মচ্যুত নুড়িপাথর একের পর এক, সারিবদ্ধ- বেলোয়ারি জীবনের পরে নতুন আশ্রয়ে বাঁচে বিপুল সঙ্গমে। শস্যহীন ময়দান চাপা পড়ে মহাজীবনের ভারে। প্রার্থনায় উর্দ্ধমুখী হাতে হেমন্তের দাগ। ডালিম ফোটার মৌসুমে হারিয়ে ফেলা দুপুর ভীষণ যৌনকাতর।”(হালকা রোদের দুপুর–আট) অন্য একটি কবিতার অংশবিশেষও দেখা যাক:“যে রাস্তাটা চলে গেছে রিভার ভিউয়ের দিকে, আমি তার পাশে উবু হয়ে বসি। হাওয়ায় গল্প বলে সিগারেট ধরাই। মনে হয় রাত। জানি না, আসলে কি রাত? খোশগল্প করি বেহুদা কুকুরের সাথে৷”(হালকা রোদের দুপুর–পঁয়ত্রিশ) কবির যাপিত জীবন অবশেষে ভাগফলে নিয়ে আসে সংখ্যাঘন বিষাদ, ‘হালকা রোদের দুপুর’ যেন কবির অতীত জীবনস্মৃতির ত্রিমাত্রিক ল্যান্ডস্কেপ। এবং ক্রমশ তা ধূসর হতে থাকা চলচ্চিত্রের রিলে ফিল্ম। কবি মনে আসে মহাকালের মরচে ঘষে তুলতে না পারার ব্যর্থতা, ভয় আর হতাশা; যা পাঠক মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। আমাদের মনে পড়তে পারে বার্গম্যানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘সেভেনথ সিল’ এর কথা। যেখানে নায়ক জীবনের অর্থ খুঁজে চলে অবিরাম, এই এক ঘেয়ে জীবনের অর্থ কী?ঈশ্বরের নীরব থাকার প্রতি রুষ্ট হয় সে। সে চায় ঈশ্বর থাকুন, একটা আশ্রয় চায়,কিন্তু ঈশ্বর কেন এসে দেখা দেয় না, এর জন্য সন্দেহও হয় তার, জীবনের প্রতি সে হতাশ হয়ে পড়ে, তবুও বাঁচতে চায় ঈশ্বরকে কাছে পেতে চায়, জীবন নামক প্রশ্নের উত্তর চায় শেষ অবধি, সে মৃত্যুকে বিলম্বিত করবার জন্য মৃত্যুর সাথে দাবা খেলে তাকে হারিয়ে দেয়।এবার সেরকম একটা কবিতাই আমরা পড়বো পাঠক যাতে আছে জীবনঘনিষ্ট প্রশ্ন, ভয়, হতাশা— এই কবির অন্তর্গত জগতের:“ব্যর্থ কামানদাগানোর মতো তুমিও চলে যাচ্ছো ক্রুর হাসির ভেতর। কখনো আহত শব্দ, এই ফিরে আসা কেবল নিজস্ব কল্পনা। লেপ্টে থাকা বিকেলে কেউ বুঝি গেয়ে ওঠে গান। দ্রিম দ্রিম ডাকে দূরের ড্রামার। তবুও কীভাবে ঘুম বিষাদবিকেলে? চলচ্চিত্র দ্যাখো নাগালের জানালায়, অনেক সবুজ আর নিশ্চুপ আকাশ। আনমনা দিগন্তে শুধু উজ্জল তোমার পত্রালি, চিরহরিৎ চোখের পালক। আগের দিনের মতোই, বিকেলকে গড়িয়ে যেতে দাও আরো কিছুদূর।”(হালকা রোদের দুপুর–চল্লিশ) বইটিতে সাম্প্রতিকতম ভাষা কবিতা বিষয়ে সাম্যকে পুরোপুরি সচেতন দেখা যায়। বিষ্ময়কর শব্দখেলা খেলেছেন। এবং যুক্ত শব্দের প্রয়োগ, সম্পূর্ণ দুটি আলাদা শব্দের মধ্যে সংযত সমন্বয় এনেছেন।যদিও ষাটের দশকের বাংলা কবিতায় এরকম প্রচুর যুক্তশব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। সবচেয়ে ভালো দিকটি হলো সেসব যুক্ত শব্দ সাম্যের মৌলিক সৃষ্টি। সেসব শব্দের সাথে কেবল তাঁরই প্রথম হয়ে উঠেছে বোঝাপড়া এমনকি নিশ্চিতভাবেই সেসব শব্দের জন্ম দিয়েছেন সাম্য তাঁর রহস্যময় ‘কল্পনা প্রতিভা’র দ্বারা। যেমন: ‘প্রকৃতিপুরুষ’, ‘চিত্ররথ’ যেভাবে ব্যবহার করেছেন উদ্ধৃত কবিতায়, পাঠক মোহিত হবেন পাঠ করুন অংশবিশেষ:“উড়ছে শ্যামশোভা। সূর্য তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে জাগিয়ে তুলেছে। ভ্রমনবিলাসীর সাথে, তুমি নাও স্নেহের পোশাক। অধিক আনন্দে প্রকৃতিপুরুষ— ফুটে আছে বাগানের গাছে গাছে। সকল সঙ্গে, ব্যক্তিগত দিনে দেখেছি চিত্ররথ।”(হালকা রোদের দুপুর–ষোল) কখনো এরকম মনে হতে পারে যে সাম্যের কবিতা পাঠে—তাঁর অবচেতনের অবিরাম সংযত ও বুদ্ধিস্নাত প্রবাহে আমরা ভেসে যাচ্ছি কিংবা আমাদের রক্তের গভীর উত্তাপে আরও বুদবুদ উঠে যেতে থাকে, নিরুপায় হয়েই কি বলবো সেসব তাঁর spontaneous overflow of powerful feelings বা আরও একটু এগিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন “ভেতর দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা”, যা দ্বারা আমরা অবিরত তাড়িত হই! অথবা কবিতা পাঠে “কখনো কখনো মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়” পংক্তিতে পংক্তিতে কবির সেই হৃদয়ের স্পর্শ আমরা পাই। আদতে কবিতার তো কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কবিতা সয়ে যায় হৃদয়ে, মনে। এবং এ-ও তো সত্য যে কবিতা হয়েও ওঠে, কবিতার আছে শরীর আছে রক্ত, আত্মা। কবিতার আছে শ্বাস ও প্রশ্বাস; জন্ম আছে, আছে মৃত্যু, আবার মৃত্যুহীনতাও আছে, কবিতার নিজস্ব এক অনুভব আছে। প্রকৃত কবিমাত্রই বুঝতে পারেন কবিতার জন্মকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া— “কোনো একটা মুহূর্ত—তাঁর সমস্ত শরীর যেন দ্রব হয়ে আসছে, শরীরের মধ্য থেকে জেগে উঠছে ঊর্মিমালার মতো একটা ছন্দস্পন্দ—অদৃশ্য, অলক্ষ্য ছন্দবিদ্যুৎ—অথচ কোনো ভাবনা বা শব্দ দেহ নিয়ে আসেনি তখনও তাঁর চেতনায়” যেমন যথার্থই বলেছেন রবার্ট ফ্রস্ট। আমরা লক্ষ্য করে উঠবো সাম্যের কবিতা হয়ে ওঠার পেছনে সেরকমই এক অলক্ষ্য অবচেতনের অবভাস, সংগোপন নড়াচড়া শব্দভ্রুণশিশুর:“নিরালা দাঁড়াবার অপার সম্ভাবনা— ক্রমশ সুদূর! বিশুষ্ক ঘাসের প্রান্তরে চৈত্রের শিশুটির সাথে সুগোপন আয়োজন…। আরো বেলা হবে— সঘন নিবিড়। তবে কি শুধুই শব্দরাগ, সবুজ ঘনঘোরে তুলে নাও কিছু আলোফুলের ঘ্রাণ। স্নানের জলতোলা হলে, এই মহাভারত, চিত্রশোভাময়, হাওয়ার ঢেউয়ে কেঁপে ওঠে চাঁদ, কিছুটা মেঘের আড়াল। প্রেমের সকল গান মোহ-আরক্তিম, অগ্নিগামী! পরম অগ্নি তফাতে একক পুরুষ রঙ হয়ে মিশে যায়। নিশুতিতে, বৈষ্ণবীর গানে আশব্দ ফিরেএসো, বাইনোকুলারে চন্দনা নদীর মতো, ঘনঘোর রসকলি, প্রমুখ উদাস। চকিতে উন্মোচিত রাত বৃষ্টির অবসরে সহসা নিরুদ্দেশ৷”(হালকা রোদের দুপুর–পনের) নদীঘেরা এক মফস্বল শহরে বেড়ে ওঠা এই কবি নদ-নদীকে যে অস্তিত্ত্বে ধারণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। তিস্তা, ধরলা বা ব্রহ্মপুত্র নদের দু’পাড়ের দৃশ্য আর উত্তাল নদী-জীবন দেখে দেখে তিলে তিলে যার জীবনকে বুঝে ওঠা তিনি তো নদীকেই নিজের প্রতিরূপ ভেবে নিবেন। একজন কবি যখন কবিতা লেখেন তাঁর সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা, পৃথিবীতে তাঁর কৌণিক অবস্থান এমনকি সমস্ত জগতকেই নিজের শরীর বা কল্পিত আত্মার বিন্দুবিসর্গের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে গুলিয়ে নিয়ে এক এক করে শব্দ তুলে নিয়ে আসেন ধূলিধূসর অতল অচেনা গহবর থেকে, তারপর অবিরাম লিখে যান— যেরকম সাম্য লিখছেন:“নাবিকের নিজস্ব বাগান। সমদ্বিবাহু গাছের আকারে- জলের একান্ত সাইরেন। অতলে নেমেছো তুমি- কামিনী ফুলের সন্তান, তাকাও তাকাও চোখ বড় করে ফুলবতী মায়ের দিকে। পরিচিতি নদের কিনারে, প্রতিচ্ছবি আলো হয়ে আছে৷”(হালকা রোদের দুপুর–ছয়/ অংশবিশেষ) নদীই কি নাবিকের “নিজস্ব বাগান”? যেখানে নাবিক নিঃসঙ্গতা ঝরিয়ে অজস্র ঢেউয়ের পরিচর্যা করেন। ঢেউগুলো ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, পরিধিতে বৃক্ষের মতো আকাশে নয়, তীরে— মাটির সাথে ঢেউয়ের-জীবন-স্পন্দন বিলীন হয়ে যায়, এ বিলীনতা যেন কবির—কবিতার ঐ নাবিকের। নদীর ঢেউয়ের ভেতরেই কবি খুঁজে চলেন নিজের হারানো প্রতিচ্ছবি আর “সব ভালো কবিতাই তাই নিঃসঙ্গ একক” হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। ‘দুপুর’, ‘নদী’, ‘রোদ’, ‘বর্ষা’, ‘গান’, ‘সুর’, ‘নাবিক’, ‘বাড়ি’, ‘গ্রাম’, ‘শরীর’, ‘গাছ’, ‘তীর’, ‘সঙ্গম’, ‘যৌনতা’, ‘জীবন’, ‘জল’, ‘শস্য’, ‘সিগারেট’, ‘ফুল’, ‘ঘুম’, ‘আহার’, ‘বাগান’, ‘পাতা’, ‘পাহাড়’, ‘ঘোড়া’, ‘জন্ম’, ‘ক্ষত’, ‘উল্লাস’, ‘প্রেম’, ‘হাঁস’, ‘কৃষক’, ‘ফসল’, ‘মদ’, ‘পোস্টকার্ড’, ‘প্রজাপতি’, ‘পঙ্গপাল’ ইত্যাদি প্রচুর ক্লূ-শব্দ কবিতার জট খুলে নিতে কিছুটা গাণিতিক সূত্রের মতোই সহায়তা করেছে। আমরা এসব পরিচিত শব্দের ভিতর দিয়েই আমাদের দৈনন্দিন জীবনচিত্রগুলো অতিক্রম করে যাই—সকাল থেকে দুপুর, বিকেল থেকে রাত,আবার একঘেয়ে আবর্তন—এই তো জীবন, এই তো নিরবিচ্ছিন্ন সময়। ‘হালকা রোদের দুপুর’ সামগ্রিকভাবে এভাবেই আমাদের নিজস্ব জীবনের খতিয়ান মেলে ধরে আমাদেরই সামনে, সমস্ত জগতের সাথে জীবনের এক অবিভাজ্য অমোঘ সংযোজনকে দেখে নিতে দূরবীনে যখন চোখ রাখি আমরা তখন প্রত্যেকেই এক নিঃসঙ্গ দর্শক, “যৌথভাবে একা”—দেখে উঠি আল্টিমেটলি আমাদেরই একলা জীবন, জীবনের দূরতম এক আবছা ভূগোল: “আপেল স্বাধীন নয়, যৌথভাবে একা। নিহত দুপুরের পরে নদী থেকে উঠে আসে বালু, অবৈধ উপায়ে। গান ছেড়ে নেমে আসে ফুল নয়নতারাবনে। ফুটে উঠেছিলো তারা ভুতুড়ে পাঁচিল ঘেষে, আগামী আশায়। আমার থেকে কিছু আলোবাতাশ হাতে তুলে নাও। হালকা রোদের কাছে বসো। এই পাতাঝরাশব্দ— সেও তো নিখুঁত জ্যামিতি। আমার রঙজ্বলা চুলের মতো ছন্দহীন নয়। সে অন্যরকম ভালো, আকর্ষণীয় ঘুমের ভেতর।”(হালকা রোদের দুপুর–আটত্রিশ)
সাম্য রাইয়ানের ‘লিখিত রাত্রি’: হৃদগহনের অনবদ্য চিত্রকল্প
আহমেদ তানভীর ছোট ছোট কাব্যকথা। আহা, কী যে মধু! মনে হয়— “জামাজুড়ে শুধু মধু ও মহুয়ার ঘ্রাণ৷” এই কবিতাবইয়ে আহামরি কিছু নেই। আবার এমন কিছু আছে যা আর কোথাও নেই। তাইতো— “কী বলি-কার কাছে বলো, সকলই সকল”৷ শব্দবুনন আর বয়ানভঙ্গি বুঁদ করে রাখে দীঘল সময়ব্যাপী৷“চারদিকে রোজ ঘন হয়ে ফোটা অন্ধকার পেরিয়েআমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। আর এর মাঝে যদিএরকম হতো, বাড়িটাই আসতো আমার দিকেতাহলে এর অধিক, ঝড়-বাদলের রাতওকী সুসজ্জিত শোভন প্রেমে কাটিয়ে দেয়া যেত!”(লিখিত রাত্রি ৮) সাম্য রাইয়ান চলনে-বলনে ও মননে কবি বটে; জীবনের হিসাব-নিকাশ বোঝাপড়া তবু তার পাকা চিন্তকের মতো৷ কেননা তিনি তার সৃজনকর্মে প্রতিভাত করেছেন এমন সব ভাবনার বিন্দু-কণা— সব দেখেশুনে বোধ জাগে— একজন কবি অতি অবশ্যই জীবনের নিবিড় পর্যবেক্ষক৷ অবশেষে পাঠকমনও কবির সঙ্গে একাত্ম হয়— ভাবে— “ফিতে বাঁধাটাই শেখা হলো না জীবনজুতোর৷« পাঁচ পংক্তি বিশিষ্ট ছোটছোট কাব্য— মোট পঞ্চান্নটি৷ পড়তে গিয়ে ঝিমিয়ে পড়া মন জেগে ওঠে৷ ভালোবাসে জীবনকে— ঘৃণাও করে জীবনকে৷ কবিকে ভালোবাসা৷
সাম্যবাদ
আহমেদ মওদুদ প্রায় একযুগ আগে একটা কবিতাপত্রে প্রকাশিত আমার এবং সাম্য রাইয়ানের কবিতাই মূলত আমাদের নিকটবর্তী হওয়ার পালে হাওয়া লাগায়। সেই হাওয়ায় হিম হয়ে যাওয়ার বদলে উষ্ণ হয় আমাদের সম্পর্ক। ফলে আমরা সর্ম্পকিত হই লিটল ম্যাগাজিন তথা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার অপ্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় যাতে আলো ফেলে প্রিয় পত্রিকা ‘বিন্দু’ এবং যার সম্পাদক কবি সাম্য রাইয়ান। বয়সে সাম্য আমার এক দশক পিছিয়ে থাকলেও বহুল বির্তকিত দশক বিবেচনায় দু’জনে আবার একই দশকের কবি হিসেবে কিঞ্চিৎ চিহ্নিত। সাহিত্য-পলিটিক্সের যুগে নিঃস্বার্থভাবে আমিসহ অনেক লেখককে চিহ্নায়নেও অবদান রাখেন সাম্য। বলতে দ্বিধা নেই সম্পাদনার ভূমিকায় থেকে গত এক দশকে এক ঘড়া কবিতা, গোটা কয়েক প্রবন্ধসহ নানান তালের লেখা সাম্য লিখিয়ে নিয়েছেন আমাকে দিয়ে। আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি, অনেক লেখকের পেছনে দিনের পর দিন লেগে থেকে তিনি কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে৷ কী যেন এক যাদুশক্তির বলে বিন্দুর একেকটি সংখ্যার ঘোষণায় সাম্যর আহ্বানে লেখকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাড়া দেন৷ বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ সংকটের কালেও সাম্য কোন ঘোষণা দিলে সে বিষয়েই লেখকরা লিখে ফেলেন৷ এর জন্য প্রচুর শ্রম দিতে হয় তাকে৷ লেখকদের বই যোগার করে দেয়া, কখনো বই বা কখনো ফটোকপি কুরিয়ার করে বা পিডিএফ করে পাঠানো, কীভাবে লিখতে হবে সেসবের নানান দিকনির্দেশনা এসব বিপুল পরিশ্রম তিনি করতে পারেন বলেই তার মননশীল উদ্যোগে প্রচুর লেখক সাড়া দেয় প্রতিবার৷ বাংলাদেশের প্রান্তিক জেলায় বসেই তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক লেখক তৈরি ও পরিচর্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন৷ তার বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ‘অনুসারী’ তৈরি করেন না৷ প্রত্যেককে নিজের মতো বিকশিত হতে, নিজের মতো লিখতে প্রাণিত করেন, যা বর্তমান সময়ে বিরল৷ তিনি প্রায়ই বলেন, ‘আমি কারো শিষ্য না, কেউ আমার শিষ্য না’৷ যা শুধু তার মুখের কথাই নয়, বাস্তব জীবনেও তা তিনি প্রয়োগ করেন৷ প্রয়োজনীয় বইয়ের সন্ধান দিতে তাঁর জুরি নেই৷ একজন সফল সম্পাদক মূলত লেখককে তাড়িত করেন, অনুপ্রাণিত করেন লেখার জন্য। সেদিক থেকে সম্পাদককে লেখার অনুপ্রাণ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ফলে প্রাণে প্রাণ মেলাবার যে তাগাদা তা লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক হিসেবে সাম্য রাইয়ানের শতভাগ রয়েছে বলেই মানি। এছাড়া কবি হিসেবেও তিনি ইতোমধ্যেই আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ; বাকিটা সময়ের বিবেচনাতেই থাকুক। বাংলাদেশের একটা প্রান্তিক জেলা শহরে থেকেও জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মানের একটা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের সাহস দেখানো নিতান্তই দুঃসাহস বটে। অথচ কেবলমাত্র লিটলম্যাগজিন ‘বিন্দু’ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি সাম্য, করোনার আগে ‘বিন্দু’র উদ্যোগে আয়োজন করেছিলেন ৩ দিন ব্যাপী আর্ট ক্যাম্পের, যা ছিল দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা লিটল ম্যাগাজিনের লেখক-সম্পাদক, চিত্রশিল্পী, ফিল্মমেকার, থিয়েটারকর্মী সহ আর্টের নানা মাধ্যমে কাজ করা ব্যক্তিদের মিলনমেলা। করোনা পরিস্থিতির কারনে পরবর্তী বছরগুলোতে সে আয়োজন আর হয়নি৷ কুড়িগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে, শহীদ মিনার চত্বরে, শিল্পকলা একাডেমীর মাঠে, কলেজ মোড়ে এমনকি রাস্তার ধারেও একক উদ্যোগে অসংখ্যবার আয়োজন করেছেন লিটলম্যাগ মেলা৷ লিটলম্যাগের সাথে মানুষকে পরিচয় করানোর জন্য জেলা বইমেলায় লিটলম্যাগের নামে স্টল নিয়ে সারাদেশ থেকে প্রকৃত লিটলম্যাগ খুঁজে খুঁজে এনে বিক্রয় ও প্রদর্শনী করেছেন এক যুগের অধিক সময় থেকে৷ ২০০৮ সালে তাঁরই উদ্যোগে ‘লিটল ম্যাগাজিন চর্চা ও সংরক্ষণ কেন্দ্র’৷ লিটলম্যাগ বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তার প্রবন্ধ লিখে লিটলম্যাগ আন্দোলনকেই বিকশিত করে চলেছেন তিনি৷ ‘অনলাইন লিটলম্যাগ’ শব্দবন্ধটি তারই সৃষ্ট৷ নতুন দিনের পরিবর্তিত সমাজ-বাস্তবতার নিরীখে লিটলম্যাগ মুভমেন্ট কেমন হতে পারে, তারই রূপরেখা তিনি দাঁড় করিয়েছেন ‘অনলাইন লিটলম্যাগ বলতে কী বোঝায়’ শীর্ষক প্রবন্ধে৷ এছাড়া বাংলাদেশে লিটলম্যাগাজিনের পাঠক বিষয়ক গবেষণা করে লিখেছেন ‘বাঙলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন: পাঠক বেড়েছে, পাঠক কমেছে’ শীর্ষক প্রবন্ধ৷ এছাড়াও লিটলম্যাগ বিষয়ে আরো একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন ‘নীরবতা ভেঙে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুক সশস্ত্র পিঁপড়ে’৷ এছাড়া অনেক ছোট ছোট বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ফেসবুকে, ব্যক্তিগত ব্লগে এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ও বক্তৃতায়৷ এছাড়াও বিন্দুর প্রতিটি সংখ্যার সম্পাদকীয়র দিকে নজর দিলে তাঁর পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও প্রখর ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়৷ যেখানে তিনি সেই সময়কার সাহিত্য পরিস্থিতি ও লিটলম্যাগ বিষয়েই সর্বাধিক আলোকপাত করেছেন৷ এইসকল লেখা পাঠকের সামনে লিটলম্যাগের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে দিনের আলোর মতো উন্মোচিত করে, লিটলম্যাগ নিয়ে অনেক ধোয়াশা দূর করে৷ একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সমকালীন সময়ে বাংলাদেশে লিটলম্যাগ বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ লেখায় সাম্য রাইয়ান অনন্য অবস্থানে রয়েছেন৷ করোনাপরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক সুবিমল মিশ্র, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত ও কবি শাহেদ শাফায়েত প্রয়াত হলে সাম্য রাইয়ান উদ্যোগ নিলেন কুড়িগ্রামেই তাঁদের স্মরণসভা করার৷ ‘বিন্দু’র অনন্য উদ্যোগ ছিলো সেটি৷ ৭ই এপ্রিল ২০২৩ তারিখে কুড়িগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ কুড়িগ্রামের মতো একটি জেলায় এরকম আয়োজন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র সাম্যর জন্যই৷ সত্যিকার অর্থে উত্তরবঙ্গে লিটলম্যাগের প্রচার-প্রসারে সাম্য রাইয়ানের অনন্য ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে৷ এছাড়াও বন্যার মতো দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতেও ‘বিন্দু’ সম্পাদক সাম্য রাইয়ানের নেতৃত্বে আমরা ঝাপিয়ে পড়েছিলাম মনে পড়ে৷ ভাবতেই পারিনি একটি লিটলম্যাগের পক্ষ থেকেও এরকম উদ্যোগ সফল করা যাবে৷ কিন্তু সাম্য তা করে দেখিয়েছেন৷ আমি একদিন সেখানে শ্রম দিয়েছিলাম৷ মনে পড়ে, ২০২২ এর বন্যায় বিভিন্ন অঞ্চল যখন ডুবে গেছে, সাম্য উদ্যোগ নিলেন কুড়িগ্রামের চিলমারী, উলিপুর সহ কয়েকটি উপজেলায় খাবার বিতরণের৷ আমি গিয়েছিলাম৷ দেখেছি এক মহাযজ্ঞ৷ তৎকালীন জেলা উদীচী কার্যালয়ের একদিকে চলছে রান্না, অপদিকে চলছে প্যাকেজিং, রাস্তায় অপেক্ষমান ট্রাক৷ পাঁচ শতাধিক মানুষের মধ্যে সেদিন খাবার বিতরণ করা হয়েছিলো৷ এত বড় আয়োজন কীভাবে সাম্য সফল করেছিলো ভেবে আজও অবাক হতে হয়৷ একটা লিটলম্যাগের পক্ষ থেকে এত বড় যজ্ঞ সফল করা শুধুমাত্র সাম্য রাইয়ানের পক্ষেই সম্ভব৷ আবার কেবলমাত্র লিখে বা সম্পাদনা করেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেননি সাম্য, বিপ্রতীপ ধারার লেখকদের বই প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘বাঙ্ময়’ নামের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। সর্বসাকুল্যে অধমের সাতখানা গ্রন্থের মধ্যে চারখানাই প্রকাশ হয় ‘বাঙ্ময়’ থেকে। একটা কিশোর উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণও মুদ্রণ কার ‘বাঙ্ময়’। বিপ্রতীপ ধারার সাহিত্যের প্রসারে সাম্য শুধু বিন্দুর প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করেই এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করেননি৷ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছেন বিন্দু’র ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে ‘কবিতা কনর্সাট’ নাম দিয়ে প্রচার করেন কবিকন্ঠে কবিতা। বিপ্রতীপ ধারার সাহিত্যকে যত উপায়ে মানুষের কাছে পৌঁছনো যায় তা নিয়ে রয়েছে সাম্য রাইয়ানের আলাদা গবেষণা৷ এইসবের বাইরেও সাম্যর রয়েছে এক প্রতিবাদী সত্ত্বা৷ যার ফলে সাম্য সম্পাদিত ‘বিন্দু’ হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের সাহিত্যের আরেক রূপ৷ এর ফলস্বরূপ ২০১৮ সালে ঢাকায় অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ‘পুলিশি বই চেকিং’ পদ্ধতির বিরোধীতা করে বিন্দুর স্টলে ফেস্টুন লাগানোয় বিন্দুর স্টল ভেঙে দেয় বাংলা একাডেমী৷ বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা৷ বাংলাদেশের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটেছে কি? কবিতা, কবিতা আর কবিতা। কবিতা দিয়ে মোড়ানো যেনো সাম্য রাইয়ানের আদি-অন্ত। একদিকে নিজে কবিতা লিখে যাচ্ছেন অন্যদিকে অন্য কবিদের লেখা প্রকাশের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শুধুই কি কবিতা! কবিকেও ধারণ করছেন নিজের হৃৎপিন্ডের নির্যাসে তৈরি লিটল ম্যাগজিন বিন্দুতে। কখনো স্বাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, কখনো কবিকে নিয়ে সংখ্যা করছেন কখনোবা প্রয়াত কবিদের নিয়ে করছেন ক্রোড়পত্র। যেমনটা করেছিলেন ২০১৬ সালে কবি উৎপলকুমার বসুকে নিয়ে। পরে, ২০২২ এর বইমেলায় অবশ্য উৎপলকুমার বসুকে নিয়ে ‘বিন্দু’র একটি ঢাউস সংখ্যাই করে ফেলেন সাম্য। এছাড়াও করেন মাসুমুল আলম সংখ্যা এবং অতি সম্প্রতি করেন সৈয়দ সাখাওয়াৎ সংখ্যা। এরকম আরো অনেক সাহিত্যিক, যারা পাঠকের সামনে সঠিকভাবে প্রকাশিত না, সকল দলবাজির উর্ধে উঠে তাদের তুলে ধরার দায়িত্ব যেন সাম্য নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন৷ তো যিনি দিনমান অপরাপর সাহিত্যিকদের নিয়ে সংখ্যা করার পরিকল্পনা করে কাটান তাকে নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যপত্র ‘তারারা’র সাম্য রাইয়ান সংখ্যা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। কবি সাম্য রাইয়ানের কবিতার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়। ************************