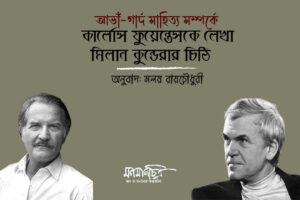যন্ত্রণার অমৃত কেলাস
অসীম কুমার দাস
মানববিদ্যার কিছু কিছু কেন্দ্রীয় ধারণা আছে যাদের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। কবিতা এই ধরনের একটি ধারণা যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে অ্যারিস্টটল থেকে পল ডে মান পর্যন্ত মহান সাহিত্য সমালোচকরাও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কবিতার প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করবার। এবং নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ এবং মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।
কোলরিজ বা এলিয়টের মতো যাঁরা একাধারে কবি ও সমালোচক– তাদের বিষয়টি একটু স্বতন্ত্র। কবিতা আসলে কী তা সংজ্ঞায়িত করবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন, কিন্তু তাঁরা এ-বিষয়ে তীব্রভাবেই অবহিত ছিলেন যে, শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতার হৃদয়কে ধরা যায় না। কারণ শেষ বিচারে কবিতা গ্রীক পুরাণের প্রোটিউসের মতো একটি সত্তা, যার রূপ এবং প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। জীবনানন্দ, ইয়েটস, এলিয়ট, পাউন্ড প্রভৃতি মহান কবিদের এ-ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য সুবিধা ছিলো। কারণ তাঁরা জানতেন যে বুদ্ধি একটি পর্যায়ে এসে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। তখন বোধ কাজ করে, অন্তর্নিহিত অবচেতনা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আর তখনই কবিতা ভিনাসের মতো সমুদ্রের নীল জলরাশি থেকে জেগে ওঠে তার মৃত্যুহীন, রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে, সুপ্রাচীন পৃথিবীর স্তব্ধতাকে চূর্ণ করে।
নিঃসন্দেহে কবিরা নিজেরাও কবিতা-সৃষ্টির জন্মরহস্য সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত নন। তবে তাঁদের স্বজ্ঞার ভেতরে অন্তর্লীন আলো আর অন্ধকারে আভাসিত হয়ে ওঠে এক ধরনের প্রজ্ঞা যার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই– শুধু ছায়া আছে। তবে এই ছায়ামূর্তি শুধুমাত্র মায়া নয়। এই ছায়ার অভ্যন্তরে প্রতিমূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের কল্পনাপ্রতিভার মহত্তম অভিব্যক্তি — যে অভিব্যক্তি আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যায়৷ এবং এই স্বাতিক্রমের গতি নক্ষত্রলোকের অভিমুখে ধাবমান।
তাই বিশুদ্ধ সমালোচকেরা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আরতি দেখেন, খুব জোর ধূপের ধোঁয়া এসে তাদের নাসিক-গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার তাদের নেই৷ সেখানে প্রবেশাধিকার শুধু কবিদের আছে। তাঁরা দেবতাকে দর্শন করেন– প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। তবে দেবতার অজানিত চোখের আলোরাশি তাঁদের আত্মার ভেতরে বিলোড়ন তোলে। আর এই বিলোড়িত জ্যোতিস্নাত বোধ অনূদিত হয় কবিতায়– যে কবিতা হোমারের আলোহারা সমুদ্রের সোমরস।
তবে কবিদের এই বিলোড়িত বোধ এবং নক্ষত্র ছোঁবার প্রণোদনার সাথে দুটি আনুষঙ্গিক উপলব্ধি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, একটি হচ্ছে ‘অলৌকিক আনন্দের ভার’ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘সীমাহীন মহাজাগতিক শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা’। এই দুটি অনুভূতিকে পৃথক করা যায় না। কারণ পৃথকীকরণের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে কবির অপমৃত্যু।
এই সঙ্কটাবস্থা কবিদের নিয়তি। এর থেকে মুক্তি নেই একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য আমি শারীরিক মৃত্যুর কথা বলছি না। তবে ধাঁধার মতো শোনালেও মৃত্যুর সাথে আর্টের একটা যোগাযোগ আছে। কথাটা পাস্টারনেক ডক্টর জিভাগো–তে বলেছেন। তবে তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আর্ট যদিও মৃত্যুর সহোদরা ভগ্নী, কিন্তু এই মৃত্যুমুখরিত চেতনা থেকেই আর্ট অন্তহীনভাবে জীবনকে নবজন্ম দেয়।
পাস্টারনাকের এই প্রগাঢ় উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় অন্তত আধুনিক আর্টের সাথে মৃত্যুচেতনা, বিভীষিকা, যৌন বিকৃতি, উন্মত্ততা, নিস্তব্ধতা, শূন্যতাবোধ ইত্যাদি বিষয়ের একটি অনস্বীকার্য যোগসূত্র রয়েছে৷ কাফকা, কামু, হারম্যান ব্রখ, কনর্যাড, পিকাসো, দালি প্রভৃতি মহান শিল্পীদের কীর্তি এই সত্যের উজ্জ্বলতম উদাহরণ সন্দেহ নেই।
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কবিদের চৈতন্যের এই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সাথে আর্টের সম্পর্কটা কী ভাবে মেলানো যায়। কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আর্ট হচ্ছে বাস্তব জগতের আভাস-ঋদ্ধ শৃঙ্খলাহীনতার রূপান্তরিত প্রতিসাম্য। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে একটি অব্যাখ্যাত প্রহেলিকা। শিল্পী ও কবিদের জীবনাচরণ এবং কল্পনার জগতের ভেতরে পরিলক্ষিত হয় একটি নৈরাজ্য-দীর্ণ অস্থিরতা ও যন্ত্রণা। অথচ এই নৈরাজ্য আর যন্ত্রণার আবর্ত থেকে উঠে আসে এমন সব শিল্পকর্ম যেগুলি পূর্ণাঙ্গ ও সুশৃঙ্খল — অর্থাৎ সেখানে বাস্তব জগতের নৈরাজ্য এবং শৃঙ্খলাহীন অপরিপূর্ণতা অবিশ্বাস্যভাবে অনুপস্থিত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় দান্তের লা দিভিনা কোম্মেদিয়া এবং শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ এবং দ্য টেমপেস্ট। বিশেষত বোদলেয়রের মতো কবিদের শিল্পকর্মের বিচার করতে গেলে এই সত্যটির যথার্থতা আমাদের বিস্মিত করে। কারণ বোদলেয়র বা র্যাঁবোর কবিতার সাথে তাঁদের জীবনাচরণকে মেলানো যায় না নিঃসন্দেহে।
কিন্তু গভীরভাবে বিষয়টিকে অনুধাবন করলে এই আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত স্ববিরোধিতার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় সম্ভব। কারণ কবিতার প্রাণকেন্দ্র ও উৎস হচ্ছে এক আশ্চর্য ধরনের দ্বন্দ্ব। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কবিতা বা শিল্প একটি সমাপ্তিবিহীন যুদ্ধের পরিণতি। এবং এই যুদ্ধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য৷ এখানেই কবিতার শক্তি ও অনিবার্য অনন্যতা নিহিত।
অনিবার্যভাবে সমালোচকেরা প্রশ্ন করবেন, কবিতা তথা শিল্প কোন ধরনের যুদ্ধ থেকে উৎসারিত ধ্যানমালা? আমার ধারণা, প্রথমত, কবিতা হচ্ছে মানবীয় চৈতন্যের সাথে জড়বিশ্বের এক অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত, কবিদের ভাবনা, বেদনা এবং যন্ত্রণার সাথে কবিতা হচ্ছে শব্দমালার সীমাবদ্ধতার আমৃত্যু সংগ্রামশীলতার জ্বলন্ত দলিল। এই সংগ্রামশীলতার কোনো চূড়ান্ত সমাধান নেই। কারণ পৃথিবীর মহত্তম কবিদের পক্ষেও তাঁদের অপরিমেয় চিত্রকল্প, ভাবনা এবং যন্ত্রণার দ্বারা নির্মিত কল্পনাবিশ্বকে মানবীয় ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে রূপান্তরিত করা অসম্ভব।
এ-ছাড়া ভাষাশিল্পীদের সাথে অন্যান্য শিল্পীদের একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন একজন চিত্রশিল্পী অথবা ভাস্কর রঙ, প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা ইত্যাদি মাধ্যমের সাহায্যে তাঁর স্বপ্ন ও আস্পৃহাকে অভিব্যক্ত করেন। রঙ অথবা প্রস্তরখণ্ড অথবা মৃত্তিকা মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহার্য বস্তু নয়৷ কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন ভাষা ব্যবহার করেন। অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভাষা জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয় স্বাভাবিকভাবেই। ভাষাশিল্পীদের অসুবিধা এখানেই। তাঁদের কাজটা একটু কঠিন এ-জন্য যে, এই জীর্ণ ভাষাকে তাঁদের নতুন মাত্রা দিতে হয়– অতি-পরিচিত শব্দসমূহকে মণ্ডিত করতে হয় এক অপ্রত্যাশিত ও অপরিচিত সৌন্দর্যের অর্থময়তায়।
তবে কবি তথা ভাষাশিল্পীদের এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনন্য সুবিধাও আছে। রঙ অথবা প্রস্তর মানুষের যত কাছাকাছি, ভাষা অপেক্ষাকৃতভাবে নিঃসন্দেহে আরও গভীরসঞ্চারী। ব্যাপারটা স্বতঃস্বচ্ছ– কারণ ভাষা মানুষের রক্ত ও চেতনার অভ্যন্তরে বসবাস করে৷ তাই একজন মহাকবি যখন মানুষের রক্তের ভাষাকে অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতময়তায় মণ্ডিত করতে সক্ষম হন তখন মানুষের রক্ত আর চেতনা যতটা বিলোড়িত হয়, মানুষকে ঠিক ততটা আলোড়িত ও আনন্দিত করাটা একজন মহান চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের পক্ষেও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না বলে আমি মনে করি৷ এবং এই জন্যই সম্ভবত কবিতা তথা সাহিত্য মহত্তম শিল্প। এখানে কোনো কোনো সমালোচক সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন৷ কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি আমি অপরিসীম ভালোবাসা রেখেই এই ধারণা ব্যক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সঙ্গীতেরও কিছু অনিবার্য সীমাবদ্ধতা আছে৷ বীঠোফেন, মোৎসার্ট, বাখ প্রভৃতি মহত্তম সুরস্রষ্টারা আমাদের উপলব্ধি ও আবেগের ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর ঘটান– আমাদের মর্ত্যচেতনাকে নক্ষত্রলোকের অভিমুখে নিয়ে যান। কিন্তু আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে তাঁরা ততোটা উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু কবিতা তথা সাহিত্যের আত্মার ভেতরে বোধি, বুদ্ধি ও আবেগের ত্রিবেণী-সঙ্গম পরিলক্ষিত হয়। এখানে এসে বুদ্ধি, বোধ এবং অভিজ্ঞতার গভীরতম উপলব্ধিসমূহের সীমান্তরেখা অবলুপ্ত হয়। শিল্পের প্রায় প্রতিটি প্রজাতি অন্তত মহত্তম কবিদের কীর্তির প্রাণকেন্দ্রে এসে লাভ করে একটি অবিশ্বাস্য, একীভূত পূর্ণতা। সেখানে শিল্পের প্রতিটি শাখা একে অপরকে আলিঙ্গন করে এক ঐন্দ্রজালিক প্রতিসাম্য-ঋদ্ধ পরিপূর্ণতায়। এই উক্তির ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা স্বত:স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যখন আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে পাঠ করি হোমার, সোফোক্লিস, এসকাইলাস, কালিদাস, দান্তে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান।
কবিতা নামক শিল্প মাধ্যমের এই রকম স্বয়ম্ভু ও অদ্বিতীয় ”mode of existence’ এর জন্য একটি বিষয় দায়ী বলে আমার মনে হয়। সেটা হলো এই যে, কবিতা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দ্রজালময় ধ্বনির ওপরে– এবং সেই ধ্বনি বিশেষভাবে অর্থময়। এক বিচারে যদিও সব ধরনের ধ্বনিপুঞ্জেরই কোনো না কোনো অর্থ থাকে– যেমন সঙ্গীতে ব্যবহৃত ধ্বনির থাকে অন্তর্লীন দ্যোতনা। তবে সঙ্গীতের ধ্বনি আক্ষরিকভাবে কোনো বিশেষ ভাব ও ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না– বরং তা এক সামগ্রিক উপলব্ধির বিশ্ব নির্মাণে সবচেয়ে পারঙ্গম। কবিতাও এ-ধরনের অর্থময়তার পরিব্যপ্তি ঘটাতে সক্ষম সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিতায় অর্থময়তার এই আততি যেভাবে ঘটে, তা একটু অন্য প্রকারের। যেমন, কবিতায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দেরই একটি আভিধানিক অর্থ থাকে। কিন্তু কবির ‘স্বপ্নকল্পনা’ (imagination) আপাতবিচ্ছিন্ন শব্দাবলীর ভেতর থেকে একটি বিশাল ও অপ্রত্যাশিত রকমের নতুন অর্থকে সূর্যালোকের অজস্রতায় প্রতিস্থাপন করে। অর্থাৎ একটি অন্ধকার শব্দের সাথে অন্য একটি অন্ধকার শব্দের সংঘর্ষের ফলে জ্বলে ওঠে অর্থময়তার আলো– এবং সেই আলোর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় পার্শ্ববর্তী আরো একটি অনালোকিত শব্দ৷ তার পরে শুরু হয় খাণ্ডবদাহন।
কিন্তু খাণ্ডবদাহনের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান করে এক উদাসীন ও অধ্বনিন মহাবিশ্ব, যা অর্থপূর্ণ করে তোলে এই ‘স্বপ্নকল্পময়’ অলাতচক্রের মৌলিক প্রক্রিয়াকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কবিতার কাঠামোর ভেতরেই প্রবলভাবে উপস্থিত অধ্বনিন মহাবিশ্বের উদাসীনতা, যার প্রতীক হিসেবে ক্রিয়াশীল একটি শব্দের থেকে আর একটি শব্দের দূরত্বমোচনকারী শূন্যদেশ। এই শূন্যদেশ আবার একটি কবিতার আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিকেও বলয়িত করে রাখে। অর্থাৎ শূন্যদেশের স্তব্ধতা শব্দসমূহের ভেতরে সংঘর্ষের জ্বলে ওটা সূর্যাবর্তকে অর্থময় করে তোলে। কিন্তু এর ফলে একটি অদ্ভুত ‘ড্রামা’র সৃষ্টি হয় যার প্রধানতম বিবদমান চরিত্র দুটি হচ্ছে যথাক্রমে শব্দমালার অ্যালকেমি এবং শূন্যদেশের দ্বারা আভাসিত মহাবিশ্বের অ-মানব নিস্তব্ধতা– যার নিত্যসঙ্গী হলো ধ্বংস, মৃত্যু আর উন্মত্ততা। ধ্বংস, মৃত্যু আর উন্মত্ততার প্রসঙ্গ এলো কারণ এই তিনটি অবভাসের মূর্ত প্রতীক হলো পরতম অনুপস্থিতি, যা কবিতার অধিকাঠামো হিসেবে ক্রিয়াশীল অমানব নিস্তব্ধতার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শেষ বিচারে কবিতা হচ্ছে শূন্যদেশের মহাজনশূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে-থাকা এক মর্মর পিরামিড যা ক্রমাগত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে।
বাংলা নবর্বষ: ঋতুযোগ ও বিবিধ
আজিজ কাজল

বাঙালির আচরণের মেজাজ ও ধরন এবং ঋতু-প্রকৃতির মেজাজ ও ধরন যেন একে অপরের অন্যতম পরিপূরক। ঋতুর আচরণে অনেক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য হলেও মানসিক আচরণ ও পেশাগত আচরণে বাঙালির ঋতু নির্ভরতা ফেলনা নয়। কেননা কোন মাসে নতুন ধান হয়, কোন মাসে কোন ফসল বা তরিতরকারী সুবিধাজনক। কোন সিজনে সমুদ্রে মাছের চাহিদা বেশি। এবং বেচাকেনার মুনাফা অধিক হয়। বাগানে কোন সময় কোন ফল-ফলাদি ভাল হয়। কোন প্রজেক্টে কোন মাছের চাষ দুর্যোগহীন সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যায় ইত্যাদি। মোটামুটি নগর জীবনের মানুষের চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যে মূল পেশা ছাড়াও সহায়ক পেশা হিসেবে বাঙালির ঋতু-নির্ভরতা কোন মতেই অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
মানুষের শারীরিক গঠন, কথা বার্তা আচরণে প্রকৃতি অনেক বড়ো অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বারের হিসেবে অথবা অনিবার্য জীবনাচরণের হিসেবে ইংরেজি বার বা তারিখগুলো আমরা প্রতিদিন মনে রাখি। তেমনি ইংরেজি হিসেবের পাশাপাশি নানা কারণে, বাংলা ঋতুর বাংলা সন বা তারিখের হিসেবও অনেকের মনে রাখতে হয়—সনাতন ধর্মাবলম্বীর দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, সরস্বতী পূজা, কালিপূজা, মনসা পূজা, আশ্বিনে রেঁধে কার্তিকে খাওয়ার হিসাবসহ বিভিন্ন উৎসব, পালা-পার্বণ, কোষ্ঠী গণনা ও বিয়ে সাদীতে তারা(অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষের হিসাবসহ) বাংলা তারিখ বা সনগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের রোজা, ঈদ, রবিউল আউয়াল, মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, ইদুল ফিতর, ইদুল আজহা এসব দিনগুলো গণনার হিসাবেও অনেককে আরবি সনের পাশাপাশি বাংলা সনকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিতে দেখা যায়। ইংরেজি ক্যালেন্ডার, দিনপঞ্জিতেও বাংলা সন বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান পায়। এছাড়াও আছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা বা বৈশাখি পূর্ণিমা(বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বলে, এবং এটি বৈশাখ মাসে উদযাপন হয় বলে বৈশাখী পূর্ণিমাও বলে) মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণাসহ বিবিধ আচার অনুষ্ঠান। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্রিসমাস বা বড়দিন, ইস্টার সানডে সহ সব ধরনের অনুষ্ঠান, মোটামুটি ঋতু-ভিত্তিক বা ঋতু-নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
পহেলা বৈশাখ। বাঙালির সম্পূর্ণ নিজস্ব-সংস্কৃতির বিশাল একটি পরিচয়ের বাহক বাংলা নববর্ষের কথা বললে, হাজার বছরেরবাংলা, বাঙালি এবং পরম্পরাভেদে (যদিও স্থান-কালভেদে দুই বাংলার সম্মিলিত নানা বৈশিষ্ট্যকে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জন্য স্বীকারকরতে হবে) বাংলাদেশের কথা চলে আসে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মনে করেন, বাংলার নদীমাতৃক পূর্ব বঙ্গে হয়েছে ভাটিয়ালি গানের বিস্তার। আর শুষ্ক বঙ্গে হয়েছে ভাওয়াইয়া গানের বিস্তার। আর বাংলা ও পশ্চিমাঞ্চলে হয়েছে কীর্তন ও বাউলের। এভাবে বাংলার মানসসংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংগীত, আধ্যাত্মচিন্তা ও দর্শনকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে ওঠেছে। এবং এইসব বিষয় যে অনেকবেশি প্রকৃতিলগ্ন তাতিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। সুতরাং এভাবে আসে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা। আসে মাটিজাত মরমী শিল্পী লালনের কথা।হাসন রাজা, রাধারমণ, আসকর আলী পণ্ডিত, শাহ আব্দুল করিম, উকিল মুন্সি, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, শেফালি ঘোষ, আব্বাস উদ্দীন, আব্দুল আলীম, পল্লীকবি জসীম উদদীন, আসকর আলী পণ্ডিত; আসে মাইজভাণ্ডার, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি সারি, লোকগান, লোকসাহিত্য, লোককথা, কিংবদন্তি, মিথ, এক তারা, ঢোলসহ মৃত্তিকালগ্ন পলিময় নানা সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনার কথা।
এখানে কেউ করেছেন মরমীবাদের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্ম এবং অধ্যাত্মের যোগসাধনার চর্চা। কেউ করেছেন সহজ সরল পল্লীর জয়গাঁথা।কেউ করেছেন এই বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও মানুষের জয়গান। প্রাণসঞ্চারী তথা হৃদয়ভেদী আঞ্চলিক গানের সরাসরি অমৃতবচনের গান ও শিল্পের চর্চা। রয়েছে বাঙালির নিজস্ব রসনা ইলিশ, শুটকি, লইট্যা, ভেটকী, টেংরা, পুঁটি, মলা, ঢেলা মাছ ইত্যাদি। আসেএখানকার নিজস্ব জলাধারসহ পুকুর, দীঘি, নদ-নদীর কথা। আসে মাটির শানকি, কলস, শাড়ি, শীতল পাটিসহ কামার, কুমারপালমশাই এবংপটুয়াদের কথা—এককথায় এই নববর্ষ হচ্ছে আমাদের বাঙালি জাতির নিজস্ব অশত্থ বা বটবৃক্ষ। আর উল্লেখিতঅনুষঙ্গগুলো হচ্ছে তার শক্তিশালী সতেজ-শাখা, ডাল পালা, অমৃত ফলের নিকুঞ্জ।
নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ে বিবর্তনের ধারায় বাঙালির নিজস্ব মহোৎসব এই নববর্ষ, তার বড় একটা জায়গা অধিকার করে আছে। এই উৎসবেরভেতর থেকেও সে নিতে চায় আমাদের নৃ-গোষ্ঠীর যাপনবৈচিত্র্য-ঐতিহ্যসহ কৃষ্টি-সংস্কৃতির নানা আধার।পাহাড়ী জনবসতিলগ্ন এলাকাগুলোতে অনেক নৃ-গোষ্ঠীসহ বাঙালিদের বাস। তাদের উর্বরা মাটিতে ফলানো ফল-ফলাদি, শাক-সবজির কদর এখন অনেক বেশি। গ্রাম ছাড়িয়ে এসবএখন নগরের স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরাও উচ্চমূল্যে ক্রয় করছে। আছে কামরাঙা। ধনে পাতা। ধনে মরিচ। বাতাসা মরিচসহ বিবিধ মরিচ। বেলুম্বু ফল। বেল বা শ্রীফল (সংস্কৃত নাম বিল্ব ফল) তাল। আম। দেশি কমলা। লিচু। জলপাই। জাম। কাঁঠাল। পেয়ারা। বাতাবি লেবু বা এলাচি লেবু (অঞ্চলভেদে আবার একেক ফল ফলাদি, সবজির সাইজ আর স্বাদ একই বা কাছাকাছি বলে অনেক সময় নামেও কিছুটা ভিন্নতা বা তারতম্য আছে) এ জাতীয় ফলগুলো আমাদের পলিময় দেশেরমাটিতেই নিজ স্বাস্থ্যগুণে সমৃদ্ধ। উল্লেখিত সবজি বা ফল-ফলাদিগুলো একেক সিজনে, পুরো বারোমাসে অথবা ঋতু-নির্ধারিত সময়ে হয়েথাকে। এসব খাবার-দাবার বাঙালির রুচি-অভ্যাস জীবনাচরণে, নিজেদের আবহাওয়া এবং মাটি-গুণের প্রতি আলাদা কদর ও ভালবাসাবাড়ায়। যদিও ওষধিগুণসম্পন্ন এসব আইটেম এখন গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির আওতাভুক্ত হয়েছে। এবং একে পুঁজিকরে দেশে বিভিন্ন ধরণের ঔষধালয়ও জেগে ওঠেছে। কেননা আমাদের গ্রাম্য চিকিৎসা পদ্ধতি সেই পাঁচ হাজার বছর আগের (পাক-ভারতের) আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্রের উত্তরাধিকারকে নানা প্রকরণে বহন করে চলেছে। পুরনো কবিরাজী, আয়ুর্বেদ হারবাল চিকিৎসারপাশাপাশি এই চিকিৎসা পদ্ধতিও নিরাময়ের অমোঘ শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এসব আইটেম এখন সর্বত্র সুলভ।
বাংলার প্রান্তিক মানুষ এমনকি অনেক শহুরে মানুষেরাও এখনো গ্রাম্য বিষয়গুলোর সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত; তার যথা-উদাহরণ— বৈশাখ আসলে শুরু হয় অন্যরকম তোড়জোড়। এবং স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিষয়ের প্রতি থাকে আলাদা দুর্বলতা। হাট বাজার থেকেশুরু করে সর্বত্র মিলে শুরু হয় তরমুজ, বাঙ্গি, গজা-মজা-মিঠাই-খৈ কড়ই কটকটি কেনার ভীড়; এমন বিবিধ মজাদার শুকনো খাবারে ভরপুর থাকে পুরো গ্রাম-বাংলা এমনকি শহর বন্দর।
বাংলা নববর্ষ হচ্ছে বাংলার নিজস্ব বটবৃক্ষ।বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাংলা নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রশাখা। এখন সময় হয়েছে নিজেদের ঋতুজ শস্য ও ফল-ফলাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার—বাংলার সিজনা বা ঋতুজ জিনিসের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে; এর মাঝেই লুকিয়ে আছে আমাদের নিরাময়েরও অমোঘ শক্তি।
শিক্ষকরূপে ঔপন্যাসিক
চিনুয়া আচেবে
অনুবাদ: আলম খোরশেদ
আমি যে-ধরনের লেখালেখি করে থাকি তা আমাদের অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নতুন, তাই আমার লেখার সঙ্গে পাঠকের যে-জটিল সম্পর্ক সেটা নিয়ে বিশদ আলোচনার সময় এখনো হয়নি। তবুও আমি মনে হয় এই সম্পর্কের অন্তত একটা দিক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি, কালেভদ্রে যার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় শিক্ষার কারণে আমাদের লেখকেরা যদি ভেবে থাকেন যে, ইউরোপীয় লেখকের সঙ্গে তাদের পাঠকের যে-সম্পর্ক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে আফ্রিকায় তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া যায়। আমরা ইউরোপ থেকে জেনেছি যে, একজন লেখক কিংবা শিল্পী থাকেন সমাজের প্রান্তে- তার মুখে দাড়ি, পরনে অদ্ভুত পোশাক আর ব্যবহার পাগলাটে। সমাজের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, বদলা হিসেবে সমাজও তাকে শত্রুতার না হলেও সন্দেহের চোখে দেখে। তাকে কোনো দায়িত্ব দেয়ার কথা সমাজ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না।
এ সবই আমাদের জানা, যে-কারণে আমাদের কেউ কেউ খুব উন্মুখভাবে সমাজের কাছ থেকে শত্রুতা প্রত্যাশা করে কিংবা এমন ভাব দেখায় যেন সমাজের কাছ থেকে তারা ঠিক সেই ব্যবহারই পাচ্ছে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে লেখকেরা সমাজের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটা জানতে আগ্রহী নই, সে তো তাদের বইয়েই আছে, অন্তত থাকা উচিত। যার তেমন উল্লেখ নেই সেটা হচ্ছে, সমাজ তার লেখকদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে।
অবশ্য আমি ধরেই নিচ্ছি যে, আমাদের লেখক এবং তার সমাজের অবস্থান এক জায়গাতেই। আমি জানি আফ্রিকান লেখকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তাদেরকে ইউরোপীয় ও মার্কিনি পাঠকদের জন্য লিখতে হয়, কেননা আফ্রিকান পাঠক, যদি আদৌ তা থেকে থাকে, পড়ে কেবল পাঠ্যবই। এ নিয়ে অনেক বাকবিতন্ডাও হয়েছে। আমি জানি না আফ্রিকান লেখকেরা সবসময়ই এই বিদেশি পাঠকদের কথা ভাবেন কি না। আমি যা জানি তা হচ্ছে, তাদের তা ভাবার দরকার নেই। অন্তত আমার নেই। গত বছর আমার থিংস ফল অ্যাপার্ট বইয়ের সুলভ সংস্করণের বিক্রির খতিয়ানটা এ-রকম : ব্রিটেনে ৮০০ কপি, নাইজেরিয়ায় ২০,০০০ কপি, অন্যত্র ২,৫০০ কপি। নো লংগার অ্যাট ইজ বইয়ের বেলাতেও এটা সত্যি।
আমার অধিকাংশ পাঠকই তরুণ। তারা হয় স্কুল কলেজের ছাত্র নতুবা সদ্য পড়াশোনা শেষ করেছে। তাদের অনেকেই আমাকে তাদের এক ধরনের শিক্ষক হিসেবে ভাবে। এইতো সেদিন আমি উত্তর নাইজেরিয়া থেকে নিচের চিঠিটা পেয়েছি:
প্রিয় চিনুয়া আচেবে,
আমি সাধারণত লেখকদের কাছে চিঠি লিখি না, তা তাদের লেখা যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমার অবশ্যই আপনাকে বলা উচিৎ আপনার থিংস ফল অ্যাপার্ট ও নো লংগার অ্যাট ইজ বই দুখানি আমি কতখানি উপভোগ করেছি। আমি আপনার পরবর্তী বই অ্যারো অভ গড পড়ার জন্যও উন্মুখ হয়ে আছি। আপনার উপন্যাসগুলো তরুণদের কাছে উপদেশরূপে কাজ করে। আমি বিশ্বাস করি আপনি ভবিষ্যতে এরকম আরো অনেক বই লিখবেন।
বন্ধুত্বময় শুভকামনায়,
আপনার বিশ্বস্ত,
আই. বুবা ইয়েরো মাফিন্দি
এটা খুব পরিষ্কার এই বিশেষ পাঠকটি আমার কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করে। কিংবা ঘানার সেই পাঠকটির উদ্দেশ্য বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ থাকে না, যে খুব করুণ এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিল, আমি কেন থিংস ফল অ্যাপার্ট বইয়ের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটি যোগ করতে অবহেলা করেছি, সেই সঙ্গে এমন আব্দারও জুড়ে দিয়েছিল যেন আমি তাকে সেগুলো লিখে পাঠিয়ে দিই যাতে করে সে পরের বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। প্রাকৃত নাইজেরীয়তে আমি এই জাতীয় পাঠকদের ’নাবালক পাঠক’ বলি এবং আশা করি এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই ঘানাতেই আমি এক তরুণী স্কুলশিক্ষকের দেখা পেয়েছিলাম যে আমাকে সাক্ষাৎমাত্র ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিল আমার নো লংগার অ্যাট ইজ বইয়ের নায়কের সঙ্গে তার প্রেমিকার পরিণয় না ঘটানোর জন্য। কোনো গালভারি সমালোচক এসে যখন আমাকে বলে আমি বইটি এভাবে না লিখে অন্যভাবে লিখতে পারতাম তখন আমি সাধারণত যেরকম দুর্বোধ্য সব শব্দ করে থাকি তার বেলাতেও তা-ই করেছিলাম। কিন্তু আমার সেই নারী শিক্ষকটিকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছিল না। সে রীতিমত সিরিয়াস। আমি কি জানি, সে আমাকে প্রশ্ন করে, যে আমার বইয়ে যে-রকম বর্ণনা করেছি ঠিক সেরকম অবস্থায় প্রচুর মেয়ে রয়েছে যারা খুবই উপকৃত হত যদি আমি দেখাতে পারতাম প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সাহসী অন্তত একজন পুরুষও আছে ?
অবশ্যই আমি তার সঙ্গে একমত হইনি। কিন্তু সেই তরুণী এতটা আবেগ দিয়ে কথা বলছিল যে, যুবসমাজকে তাদের খামখেয়ালিপনা বিষয়ে জ্ঞানদানের এক দুর্লভ সুযোগ নষ্ট করেছি আমি, তার এই অভিযোগে (খুব সিরিয়াস অভিযোগ নিঃসন্দেহে) খানিকটা অস্বস্তি অনুভব না করে পারছিলাম না। এখানে এ কথা বলে নেয়া দরকার যে, কোন আত্মমর্যাদাবান লেখকই তার শ্রোতাবর্গের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে না। সমাজের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের এবং প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত স্বাধীন থাকা উচিত তার। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে চাই খুব সতর্কতার সঙ্গে। আমি কেন নাইজেরীয় সেই পত্রিকা সম্পাদকের মত ইউরোপীয় শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরি সভ্যতার ’হৃদয়হীন দক্ষতা’-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাব, যখন আমাদের সমাজের ঠিক এই জিনিসটারই দরকার খুব ?
বিভিন্ন সমাজের নিজস্ব চাহিদা বিষয়ে আমার চিন্তা ধারালো হয়েছিল অল্প কিছুদিন আগে একটি ইংরেজি পপ গান শুনে যার শিরোনাম ছিল ’আমি গোসল করবো না পাক্কা সাতদিন’। প্রথমে আমি অবাক হয়েছিলাম এটা ভেবে যে, যেখানে এর চেয়ে আরো অনেক অর্থপূর্ণ ওয়াদা করার সুযোগ রয়েছে সেখানে সে কেন এমন এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করতে গেল ? পরে আমার মনে হলো যে, এই গায়ক এমন এক সাংস্কৃতিক স¤প্রদায়ের সদস্য যারা আত্মসন্তুষ্টির আদিযুগে পরিচ্ছন্নতাকে ঈশ্বরবিশ্বাসের সমতুল্য বলে প্রায় ধর্মদ্রোহের অপরাধ করেছিল। আমি তখন তাকে নতুন আলোকে দেখতে পাই- প্রতিশোধের এক স্বর্গীয় প্রতিনিধিরূপে। যদিও আমি সাহস করে বলতে পারি যে, আমাদের সমাজে তার এই বিশেষ গুণটির তেমন প্রয়োজন পড়বে না কেননা আমরা স্বাস্থ্যকে ঈশ্বরে পরিণত করার মত পাপ করিনি এখনো।
বলাবাহুল্য, আমাদের নামের পাশে আমাদের নিজস্ব পাপ ও ধর্মদ্রোহের অভিযোগ রয়েছে। আমি যদি ঈশ্বর হতাম তাহলে তার মধ্যে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক বলে গণ্য করতাম আমাদের জাতিগত অধমর্ণতাকে – তা সে যে-কারণেই হোক- বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয়াটাকে। এখন এ নিয়ে উত্তেজিত হওয়া কিংবা অন্যকে দোষারোপ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে, অন্যেরা তার জন্য যত দায়ীই হোক না কেন। আমাদের যা করার দরকার, তা হলো পেছন ফিরে দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করা কোথায় আমাদের ভুল হয়েছিল, কখন বৃষ্টি আমাদের হারিয়ে দিতে শুরু করেছিল।
বিজাতীয় শক্তির দাসত্বের কালে আফ্রিকান মানসে যে বিপর্যয়গুলো ঘটে গিয়েছিল তার দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমার বাবাদের প্রজন্মের খ্রিস্টানেরা ১৯৪০ এর দশকের গোড়ার দিকে স্থানীয় মেয়েদের স্কুলে যখন গস্পেলের আবির্ভাব বার্ষিকীতে নাইজেরীয় নাচ হয়েছিল তখন যে-ধাক্কাটা খেয়েছিল তার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। এ যাবৎকাল তারা সভ্যভব্য, খ্রিস্টীয় একটা নাচই উপস্থাপন করত, যার নাম আমার যদ্দুর মনে পড়ে, মেপোল। সেই দিনগুলোতে- আমি যখন বড় হয়ে উঠছিলাম- আমার মনে আছে গরীবগুর্বো, অখ্রিস্টানেরা ছাড়া আর কেউই স্থানীয় গ্রামীণ পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করত না। খ্রিস্টান ও বড়লোকেরা (সাধারণত সমার্থক তারা) তাদের টিন ও অন্যান্য ধাতুসম্ভার প্রদর্শন করত। আমরা কখনো জলপাত্র নিয়ে ঝর্ণার ধারে যেতাম না। বয়সোপযোগী ছোট্ট একখানা গোলাকার বিস্কিটের টিন ছিল আমার, আর বাড়ির বড়রা নিয়ে যেত চার গ্যালনের কেরোসিন টিন।
আজ অবস্থা অনেক পাল্টেছে, তাই বলে একথা ভাবা বোকামি হবে যে, ইউরোপের সঙ্গে আমাদের প্রথম মোকাবিলার অভিঘাত আমরা পুরোটা সামলে উঠতে পেরেছি। তিন কী চার সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রী, যে ছেলেদের স্কুলে ইংরেজি পড়ায়, একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে, সে কেন ’হারমাটান’-এর কথা বলতে গিয়ে, শীতের বর্ণনা দিয়েছিল। সে বলেছিল অন্য ছাত্ররা তাহলে তাকে গেছোমানব বলত! এখন, আপনি নিশ্চই ভাবতেন না আপনার আবহাওয়ায় লজ্জার কিছু থাকতে পারে, ভাবতেন কি? কিন্তু দৃশ্যত আমরা তা ভাবি। এই ভয়ঙ্কর লজ্জাকে কীভাবে উৎপাটন করা যেতে পারে? আমি মনে করি লেখক হিসেবে এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এই ছেলেটিকে এই কথা বুঝিয়ে বলা যে, আফ্রিকার জলবায়ু লজ্জার কিছু নয়, যে, তালগাছও কবিতার যোগ্য বিষয় হতে পারে।
এখানে আমার জন্য একটা প্রকৃত বিপ্লবের সুযোগ রয়েছে- দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্য আর আত্মঅবমাননার গøানি ঝেড়ে ফেলে আমার সমাজকে আমি তার নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করতে পারি। এবং এটা নিঃসন্দেহে শিক্ষারই প্রশ্ন, শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থে। এখানে আমি মনে করি আমার লক্ষ্য ও আমার সমাজের আকাঙ্খার মিলন ঘটে। কেননা কোনো চিন্তাশীল আফ্রিকানই তার আত্মায় যে গভীর ক্ষত তার বেদনাকে এড়াতে পারে না। আপনারা সবাই আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব, আফ্রিকান গণতন্ত্র, আফ্রিকান সমাজতন্ত্র, আফ্রিকান কৃষ্ণত্ববাদ ইত্যাদির কথা শুনেছেন। এসবই আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে তৈরি করা পাটাতন বিশেষ। একবার নিজের পায়ে দাঁড়ানর পর আর সে-রকম কিছুর দরকার পড়বে না আমাদের। কিন্তু আপাতত মনে হয় এটা বস্তুর ধর্মের মধ্যেই পড়ে যে, আমদেরকে বর্ণবাদের বিরোধিতা করতে হবে, সার্ত্র কথিত বর্ণবাদবিরোধী বর্ণবাদ দিয়েই, শুধু এটাই প্রমাণ করতে যে, আমরা আর সবার সমকক্ষই শুধু নই, তাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতও বটে।
লেখক তার ওপর অর্পিত শিক্ষা ও চেতনার পুনর্নবীকরণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন না। সত্যি বলতে কি তাকে সবার আগে এগিয়ে চলতে হবে। কেননা তিনি হচ্ছেন- এজেকিয়েল এমফাহলেলে তাঁর আফ্রিকান ইমেজ বইয়ে যেমন বলেন- তার স¤প্রদায়ের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সদস্য। ঘানার দর্শনের অধ্যাপক উইলিয়াম আব্রাহাম একই কথা অন্যভাবে বলেন : ”আফ্রিকান বিজ্ঞানীরা যেখানে আফ্রিকার বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলোর সমাধানে তৎপর, আফ্রিকান ঐতিহাসিকেরা আফ্রিকার ইতিহাসের গভীরে প্রবেশে উন্মুখ, আফ্রিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আফ্রিকার রাজনীতি নিয়ে ভাবিত সেখানে আফ্রিকান সাহিত্যিকদের কেন এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে, যাকে তাঁরা নিজেরাই অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচনা করেন ?”
আমি অন্তত এ থেকে মুক্তি পেতে চাই না। আমি খুব খুশি হব যদি আমার বইগুলো (বিশেষ করে যেগুলো অতীতাশ্রয়ী) পাঠকদের শুধু এটুকুই শেখাতে পারে যে, তাদের অতীত- তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও- বর্বতাময় এক দীর্ঘ রাত্রি ছিল না, যা থেকে তাদের উদ্ধার করে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপী ইউরোপীয়রা। হয়তবা আমি যা লিখি তা বিশুদ্ধ শিল্প থেকে একেবারে আলাদা ফলিত শিল্পমাত্র। এই দুটোকে আমি পরস্পরবিচ্ছিন্ন বলেও ভাবি না। হাউসা লোককথার এক সাম্প্রতিক সঙ্কলনের একটি গল্প, প্রথামত আশ্চর্য সব ঘটনা বর্ণনার পর এভাবে শেষ হয় : ”তারা সবাই আসে এবং একসঙ্গে সুখে জীবনযাপন করে। তার একাধিক পুত্রকন্যা ছিল, যারা বড় হয়ে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।”
আমি যেমন অন্যত্র বলেছি, আপনি যদি একে একটি নির্বোধ পরিসমাপ্তি বলে মনে করেন, তাহলে আপনি আফ্রিকা সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারেন না।
(১৯৬৫ সালে লিড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া এই বক্তৃতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনের নিউ স্টেট্স্মেন পত্রিকার জানুয়ারি ২৯, ১৯৬৫ সংখ্যায়। ডাবলডে অ্যাঙ্কর বুক্স থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত মর্নিং ইয়েট অন ক্রিয়েশন ডে গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত হয় পরে।)
লেখক পরিচিতি : আধুনিক আফ্রিকী কথাসাহিত্যের জনক চিনুয়া আচেবের জন্ম ১৯৩০ সালে নাইজেরিয়ায়। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক চিনুয়া ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস Things Fall Apart: এ আফ্রিকার গ্রামজীবনের লোকাচার, লোকভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন আফ্রিকী ইংরেজির জন্ম দেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের আফ্রিকী লেখক ও শিল্পীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ঔপনিবেশিক শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরোধিতায় তিনি তাঁর লেখনীকে সদা সচল রাখেন। তাঁর অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে No Longer at Ease, Girls at War, Arrow of God, Anthills of Savannah ইত্যাদি। ২০১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
আহমদ ছফাঃ সার্বক্ষনিক সত্ত্বা ও তাঁর অভিঘাতের উদ্দাম চৈতন্য
আলমগীর ফরিদুল হক
…এর পর মাস যেতেই আমাদের রক্তাক্ত দেশ স্বাধীন হলো, সদ্য জন্মপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশে আন্দরকিল্লার তাজ লাইব্রেরী’ হাক্কানী লাইব্রেরী, পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী থেকে বই কেনা শুরু, বাঙলা যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতে না পারলেও বাঙলা পড়ে যেতে পারি! আশ্চর্য লাগে বৈকি ৬৮, ৬৯, ৭০ সালে প্রকাশিত আমাদের বাঙলা সাহিত্য, অনূদিত সাহিত্য, এমন কি কিশোর সাহিত্য কি শক্তিশালী উন্মেষ আর উদ্ভাসন ছিল তা ভাবাই যায় না! একদিন তাজ লাইব্রেরী থেকে পেয়ে গেলাম ‘নিহত নক্ষত্র’, লেখক আহমদ ছফা, তাঁর ভাষা ভঙ্গী’তে আছে একটা টকবগে সতেজ বর্নাণাক্রম! বাড়ি’তে এসে বললাম এই লেখকের নামের বানান ভুল আছে, আমার মনে হলো সেই যুগে ভুল ছাপা হয়েছে! হবে ‘সফা’ অনেক’টা আমাদের চট্টগ্রামের ক্যাপ্টেন সফা’র মতই হবে হয়তো! তবে এই নামের বানান নিয়ে কোন কিছুর সুরাহা হয়নি, তবে কে যেন বলল চাটগাঁয় আঞ্চলিক টান রাখা হয়েছে হয়ত তা ইচ্ছাকৃত! এরপর থেকে একে একে, ‘জাগ্রত বাঙলাদেশ’, ‘ওঁম’, ‘বুদ্ধিবৃত্তির নূতন বিন্ন্যাস’ কিনে ফেলি কিন্তু এর পরবর্তি কালে আর কিছু কেনা হয়নি! উনি আমার কাছে বিস্মৃত না হলেও একটু দূরের হয়ে গেলেন। তখন রুশ ও ফরাসী দেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্র নিয়ে মেতে আছি! ছফা ভাইয়ের সাথে পরবর্তিতে আমার পরিচয় ঘটবে তা আমি কি ভেবেছিলাম! এমনি কতো স্বপ্ন ছিল দেখা করবো লোকশিল্প ও সাহিত্যের গবেষক মনসুরুদ্দিন, শিল্প গুরু এস এম সুলতান, দেবেশ রায়, সুবিমল মিশ্র, অসীম রায়, আহমদ ছফা, খন্দোকার মুহম্মদ ইলিরাশ, হাসান আজিজুল হক, জ্যেতিপ্রকাশ দত্ত, হায়াত মাহমুদ প্রমুখ আমার প্রিয় মানুষ গুলোকে কাছে থেকে দেখবো, পরিচিত হবো। তাই কি হয়! কিন্তু আমাদের দেশজ চিন্তক আহমদ ছফা’র সাথে ঢাকায় এক ঘটনা চক্রে অনির্বায ভাবে দেখা হয়ে গেয়েছিল। জেনেছিলাম তিনি চাটগাঁর মানুষ, তা তাঁকে কখনো চাটগাঁয় দেখিনি! তবে চট্টগ্রামে মেডিক্যালের হবু ডাক্তার বন্ধু’দের আড্ডায় পরিচয় ঘটলো ইরানী ছাত্র আসাদ রাজাগভির সাথে। তার কন্ঠ থেকে দীর্ঘ যুগ পরে হঠাৎ করে শুনলাম ছফা ভাইয়ের কথা ! সেই ‘নিহিত নক্ষত্র’এর কথা আমার মনে আবার জেগে উঠলো! সে নাকি চট্টগ্রাম মেডিক্যালে ভর্তির আগে ছফা ভাইয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে একই হলে ছিল অনেক বছর! আসাদ যা চেহারা চারিত্র্য বর্ণনা দিল ছফা ভাইয়ের, তাঁর কথায় খুবই সাধারণ শ্রমিকের মত দেখতে হাইলি চার্জড একজন মানুষ! না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না ইত্যাদি! তাকে দেখতে খুবই মন চাইতো! তাঁর কাঁধে থাকতো একটা টিয়ে পাখি! দিন দুপুরে বাসের কন্ট্রাটরগীরি করতেন, ঘরে বাইরে কিনবা খোলা জায়গায় বাঁশি বাজাতেন, বাঙলা একাডেমী থেকে গবেষণা করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গাভী পালাতেন, যে গাভীটির দুধ পান করতেন, গাভীটি বাগানের লতা পাতা ফুল সবজী খেয়ে ফেলতো সে ব্যাপারে ছফা ভাইয়ের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না! ইত্যাদি ইত্যাদি ! সব শুনে টুনে এই মানুষটি’কে সনাক্ত করার চেষ্টা করি। কে উনি? উনি’কে? মানুষ পাখি সব কিছুতে তিনি সার্বক্ষনিক অভিঘাত করে চলেছেন! তিনি যেন কারলস কস্তানেডাস সেই রেড ইন্ডিয়ান সন্ত এর মতন ! যার জ্ঞান আছে ফলে তাঁর কোথাও থেকে ভয় নেই। তাঁর আছে মানব জীবনের গভীর চেতনা, যার কোথা থেকে কোন ভয় নাই!

ক্লু বিয়ারিং ল্যাঙ্গুয়েজে প্রথম শনাক্তিঃ
জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরীয়ান মতিউর রাহমান একদিন খবর দিলেন, বললেন, ছফা ভাইকে চেনেন? উনি আপনাকে দেখতে চেয়েছেন, যেভিৎটস সাহেবও আপনার তল্লব করেছেন উনার রুমে! কে উনি? ও বুঝেছি, না ওনাকে চিনি লেখার মাধ্যমে, তবে কখন দেখিনি! তা উনি এখানে কি করছেন, মতি ভাই বললেন, আরে জানেন না! ছফা ভাই যেভিৎটস’কে হাত করে ফেলেছে, সে ছফা বলতেই পাগল! দেখি পিটার যেভিৎটসের সাথে একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষ বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন, আর চোখের বলয়ে মনি’টার মুভমেন্ট যেন সেন্ট্রিফিউগাল, চারদিকে ঘুড়পাক খাচ্ছে, যেন মনে হল ভদ্রলোক খুব টেনশনে থাকেন, একটা হাইপার ইম্পালসেও ভোগেন। এটা যেন তাঁর সৃষ্টিশীলতার ইম্পালস্! প্রতিনিয়ত কিছু গড়ছেন, ভাঙছেন, আমার মতন হাতের আঙ্গুলির মুদ্রা গালের কাছে এবং মাথাটা খুবই সোজা এবং অনড় শিরদাড়া! যেভিৎটস সাহেব পরিচয় করে দিলেন! ‘দিস ইজ আর সাফা’। উনাদের সাথে বিশাল পৃথুলা এক রমণী কালচারাল আটাচে বসে, খুবই ভালো মানুষ, আজ আর তাঁর নাম মনে নেই! যেভিৎটস সাহেব বললেন তোমাকে ডেকেছি সালমান রুশদি’র স্যাটানিক ভার্সেস সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে! পশ্চিমের ধর্মীয় প্রেমিজে ইসলামের অবস্থান সনাক্ত করে বললাম, সংক্ষেপে বললাম এগুলো কিছু সিম্পটম পশ্চিমের টু মেইক রিলিজিয়ন আ ডিবেটেবল প্রেমিজ! এই ভাবে ছফা ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়। পরিচয়ের পর্ব এখানে থেমে থাকেনি! পরবর্তিতে আমাকে নিয়ে যান মিরপুরের বাড়িতে, তারপর খুব কাছেই বাঙলা মটরের বাড়ীতে। অনেক পড়ে ছফা ভাই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডক্টর মফিজ চৌধুরীর সাথে, নিয়ে গেলেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ী, এই আবার অন্য ঘটনা! পেইন্টিং পাগল আমি কি করে ছুটে চলে গেছি আবুল খায়ের লিটুর সংগ্রহ দেখতে ঘরের ভেতর অন্য ঘরে! ঘরে ঘরে যশস্বী শিল্পীদের সকল ছবির কি সম্মিলন!
ঢাকায় ছফা ভাই আর পিটার যেভিৎটসের অনুরোধে সুলতানের রেট্রিস্পেক্টিভ এর জন্যে আমাকে বলা হলো। আমি বন্ধু পাবলো’র (জিয়াউদ্দিন খান) মাধ্যমে বড় বড় মাপের সেই বিশাল আকারের ক্যানভাসগুলো যেন এ,কে, খান ফ্যামেলী এবং এম আর সিদ্দিকীর ফামিলী থেকে যেন সংগ্রহ করে আনি। তাঁদের ছবিগুলো নিয়ে যে ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল এই বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে, যা হোক এই বিষয়ে আজ কিছু বলার অবকাশ নেই এখানে, তবে এই রেট্রস্পেক্টিভে আমারো ভূমিকা ছিল যা আমাদের কিছু কাছের মানুষজন মুছে দেয় সহজে! এই বিষয়ে শিল্পীগুরু সুলতান ভাই ভাল বলতে পারতেন! কিন্তু মোদ্দা কথা এই চিত্র উৎসব সম্ভব হয়েছিল কিন্তু ছফা ভাইয়ের উদ্যোগে এবং তাঁর সংকল্পে!
I refuse to live in history’s pages,
I must live in days still to come,
I must overtake history, become something more.
So father, I will not go to school,
There they teach the history of days long dead.
I prefer ideals I can feel
To ideals which are locked in a frame,
I prefer building my road as I travel
-Haribhakta Katuval
আহমদ ছফা’র বই পড়ে তাঁর মনঃস্তত্ত্ব ও চেতনার সাথে সম্পৃক্ত হলেও ব্যাক্তির সাথে সংস্পর্শে এসে আমার মনে হল যেন একজন শিক্ষকের দ্বারে এসে পৌঁছে গেলাম! দেশের অনেক লেখক’কের সাথে পরিচিত না হলেও তাদের লেখলেখির সাথে কম বেশী পরিচিত! কিন্তু ধীমান লিখিয়েদের আর চিন্তকদের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলাম তাঁদের যাদের সাথে, তাঁদের মধ্যে লেখক আহমদ ছফা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াশ, অন্যতম। শুধু তাঁদের কাছের মানুষ বলে জেনেছি। তাঁদের কথা আদব কায়দায় কারো প্রতি কোন হেজিমনি আরোপ করে না! কিন্তু ছফা ভাইয়ের সংস্পর্শে আসা আমার কাছে তা মনে হল ‘ইটস ফর দ্যা লাইফ টাইম ইভেন্ট, এভেন দ্যো ইউ হাভ আ ভোইজ অফ ডিসসেন্ট’! তিনি সবাই’কে গ্রহন করতেন, স্থান দিতেন তাঁর মানসিক সেই বিস্তৃত প্লাস্টিক ফর্মে! যে মনটাকে যত টানা যায় তত বিস্তৃত হয়। তাঁকে পেয়েছি আমার শিক্ষকদের মতন অন্য এক শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতিটি শব্দ স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল! তাঁর কথার ভঙ্গীতে যেমন একটা শক্তিশালী যুক্তি ও শব্দ ঘাতুনি, তেমনি তাঁর আছে লিখিত ব্যাখ্যায় সাতন্ত্র প্রাতিস্বিক একটা বৈশিষ্ট্য। তিনি বড় ভুমিস্থিত, বড় ইন্টারএক্টিভ, বড় এঙ্গেইজিং এবং নিজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন একটি সত্ত্বা! তাঁর আলাপচারিতায় একটা নূতন অভিঘাত তৈরি হয়, একটা অনুধ্যায়ী চিন্তায় মনে হবে তাঁর বিশ্লেষণ একটা মেরুকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মেরুকরণ করা হয়, তাঁর কথায় ‘ঝালিয়ে তোলা’ মত, কিন্তু মেরুকরণের পদ্ধতি কিন্তু পশ্চিমের কোন কন্টিনেন্টাল বোধি বা তত্ত্বের প্রেক্ষিত ছাড়াই তিনি করে যাচ্ছেন তাঁর অজস্র অলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যে, যুক্তির শৃঙ্খলায় ও যুক্তির তোড়ে! তাঁর আলোচনার ভিতটি কেবলি স্বদেশের ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিচারস, এবং কেবলি ঘুরছেন শেকড় বাকড়ের নিয়ে একটা নূতন ইতিহাসের সন্ধানে, এই আমার কাছে পরম পাওয়া! কারণ আমরা সবাই একটি পূর্বলিখিত ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা’কে যেন সুরক্ষা করার জন্যে জন্মেছি! ছফা ভাই কিন্তু তা ভেঙ্গে দিতে চান তাঁর নয়া মেরুকরণে। আমার স্মৃতিতে এখন জাগরূক কিন্তু এর কোন রেফারেন্সে তার চৌহদ্দি’র রূপরেখা টানা যাবে না! কিন্তু তাঁর অকাট্য মেনিফেস্টো ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ এখানে উল্লেখ করতে হবেই। তিনি বাঙালীর মুসলমানের পিছিয়ে থাকা মনের বিশ্লেষণ করেছেন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি, মানসিক পূর্বাপর সকল পরিপ্রেক্ষিতে, যা ইতিহাসে আত্মহননের নামান্তর। সেই প্রান্তিক ব্রাত্যজনের ইতিহাস তিনি গভীর গাত্রে প্রোথিত করেছেন! সে হল আত্ম-সমালোচনার সাবালকত্ব! এবং বড় নির্মোহ ভাবে যেন উপলদ্ধি করতে তিনি উৎসাহী। যা তিনি একটা আত্ম-উন্নয়নের আত্ম-সম্প্রীতির লক্ষ্যে যেন এগিয়ে যেতে পারে তারই সুপ্রার্থী। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে সাব-অল্টার্ন, পোস্ট কলোনিয়াল, কিংবা হিস্টিরিওগ্রাফির রেফারেন্স এড়িয়ে যান, কিন্তু সে প্রেমিজগুলো তাঁর বিশ্লেষণে সংশ্লেষে যেন নড়ে চড়ে উঠে, জেগে থাকে।
আমাদের সে সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়ার সময় রাজনীতিকে দেশ ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত করেছিলেন যারা, তাঁর কণ্ঠে আমি শুনছি তাঁদের সেই কণ্ঠ যেন কিন্তু আরো সোচ্চার ভাবে বেজেছে, প্রথাগত ক্ষেত্র’কে বিসর্জন দিয়ে ! আত্মসমালচনার দিকটি তাঁর মধ্যে বার বার পারদের ব্যারোমিটারের মত উঠা নামা করে! আলোচনার উপস্থাপন এবং বিস্তৃতি যেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মত এখানে এবং শেষে যেন ঝালার কাজ করে শেষ করছেন, ‘বাঙালী মুসলমানদের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যেও নয়, মুসলমান হওয়ার জন্যেও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুন তার মনের উপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত রয়েছে, সজ্ঞানে সে বাইরে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু’বছরে কিংবা চার বছরে হয়ত এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনের ধরণ-ধারণ এবং প্রবণতাগুলোও নির্মোহ ভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়ত পাওয়াও যেতে পারে।’ দার্শনিক আহমদ ছফা এখানে এক অনন্য সামাজিক হিস্টিরিওগ্রাফির জন্ম দিয়েছেন তাঁর সমকালীন ও ভবিষ্যতের কাছে।
for you
there might be another song
but all my heart can hear is your melody
– Stevie Wonder
ছফা ভাই তাঁর অলাতচক্রে যে ডাইলেক্টিক্স উপস্থাপন করেছেন তা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় অবস্থানকারী শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধা, চোরছেঁচর, নেতা, পার্টিকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, ভুঁইফোঁড়’দের নিয়ে চাঁছাছোলা এক পরাক্রম দলিল চিত্র! একদিকে বলা যায় তিনি চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের ভূমিকা উনি একাই পুরণ করেছেন ৮০’র দশকে অলাতচক্রের মত দলিলটি লিখে! জহির রায়হান এই কর্মটি সম্পাদন করতে পারতেন প্রামাণ্য চিত্রে, একটি ভিন্ন মাধ্যমে, কিন্তু এক অবিশ্বাস্য জনক ভাবে উনি অন্তর্ধান হলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার অনতিবিলম্বে। এই যেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মতন রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গেলেন! এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে আজো এই দুই বাঙালীর অন্তর্ধানের রহস্য উন্মোচনের জন্যে উভয় দেশের সরকারই কোন সঠিক ও প্রকৃত উদ্যোগ নেয়নি! জনশ্রুতি আছে যে শিল্পী জহির রায়হান ছফা ভাইয়ের মতন উনি সেলুলডের ফিতেয় ধারন করেছিলেন কলকাতার শরণার্থী, বুদ্ধিজীবী ও নেতাদের কর্মকান্ড নিয়ে দৃশ্যজ ডাইরী! যাতে ছফা ভাইয়ের মতন না দেখা বিচিত্র ঘটনার ডায়ালেক্টিক্সে ভরা! এবং আমরা জহির রায়হান যে ডাইরী লিখতেন এবং কলকাতার দৃশ্যজ দিনলিপির কথা জানতে পারি খুব সম্ভবত সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবিরকৃত সম্পাদিত জহির রায়হান রচনাবলীতে লিখিত ভুমিকাতে। তবে এই খেরো খাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে হয়তো শাহরিয়ার কবির জানতে পারেন! যাই হোক, আমি অনুমান করি যা ছফা ভাইয়ের মতন একই মাত্রাগত অভিপ্রায় ছিল, যাতে পার্টিগত আত্ম-সমালচনার সুযোগ ছিল যা পরবর্তিতে একটা নূতন স্যন্থেসিস দিতে পারতো ! এই আত্ম-সমালোচনা দিকটি, আজকের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই সুপ্রযুক্ত!
অলাতচক্রের শীজোফ্রেনিক সত্ত্বা, একটা দুর্মর প্রকাশেঃ
Politicians laugh and drink –drunk to all demands
–Stevie Wonder
ছফা ভাইয়ের অলাতচক্রের মত উপন্যাসের ভেতকার ডায়ালেক্টিসে যাব না, এবং ওই তুখোড় তীরন্দাজের লেখক সত্তা’কে নির্ণয় করতেও যাবো না ! কেবলী ছফা চরিত্র’কে আমার মত করে দেখার চেষ্টা করব। স্কটল্যান্ডের স্টাভিস্টক মানসিক হাসপাতালের মনোবিজ্ঞানী রোনাল্ড ডি লাইং’কৃত শীজোফ্রেনিয়ার সংজ্ঞাটি আমার কাছে কেন যে মনে হয়েছে বারংবার আহমদ ছফার সত্ত্বা অন্বেষণে! লাইং ষাটের ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের বিদ্রোহী ছাত্রদের বাম দৃষ্টিতে শিজফ্রেনিয়া’কে কেবল মানসিক ব্যাধি হিসেবে দেখতে অপরাগ। ষাটের যুদ্ধবিরোধী সন্তানেরা আজকের ইরাক আফগানিস্তানের যুদ্ধবিরোধী সত্ত্বার মতন, কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় ন্যায় ও বিবেক’কে সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটায়, এবং ঘটাতে পারে। লাইং এই সংগ্রামী সত্তা’কে বলেছেন শীজোফ্রেনিক সত্ত্বা, যাদের জন্ম হয়েছে সমাজের অপর্যাপ্তি থেকে, যাদের জন্ম হয়েছে সমাজের বৃহত্তর সামাজিক শরীরের শূন্যতা থেকে । অন্যদিকে তাঁর শীজোফ্রেনিয়ার সনাক্তিকরণ অনেকটা মিশেল ফুকোর সমার্থক। তিনি পাগল’ এর ব্যাখ্যায় সমাজ’কে এক্সটার্নাল শক্তি হিসেবে দায়ী করেছেন। এঁরা এন্টি এস্টাবলিস্ট শ্রেণীর, তাদের বাঙময় সত্ত্বা সমাজের মুক্তি ও জাগৃতির দিকে তাঁদের লক্ষ্য। তারা সমাজের ডায়ালেক্টিক্স বোঝে, নৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন প্রশ্নে প্রয়োজনে আত্মহুতি দিতে যারা পিচ পা হয় না! ছফা ঠিক তেমনি! এই শীজোফ্রেনিক সত্ত্বা নিজের কোন অবলম্বন না থাকলেও এই সত্ত্বা কারো উপকারের জন্যে, স্পষ্ট চেতনার লক্ষ্যে যেন নিজের শেষ অবলম্বনটুকু ছেড়ে চলে যাবেন! প্রয়োজনে তিনি দিগম্বর হয়ে, মানে ইংরেজীতে যাকে বলে Buck naked!, নিরালম্ব হয়ে ছুটে যাবেন সেই মানুষের অণুতে মানবিক ভোর’কে প্রোথিত করতে! আহমদ ছফা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর সর্বাক্ষনিক ডায়ালেক্টিক্সের জানালা খোলা খাপে রেখেছিলেন, ফলে তাঁকে দেখি মুক্তিযুদ্ধে প্রতিনিয়ত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মত বা ঋত্বিক সৃষ্ট নিশিকান্তের মত কিংবা আমাদের হালের দার্শনিক শ্লাভোয যিযেকের কিংবা সিডনী লুমেটকৃত ‘টুয়েলভ এংরি ম্যান’র ডেভিসের মত একটা ‘এভার এঙগেজিং’ এর একটা প্রেমিজ তৈরি করে যাচ্ছেন অনবরত। তিনি এসটাব্লিশমেন্ট গোত্রের কেউ ছিলেন না ফলে তিনি সেই ষাটের ছাত্রদের মতন ঢাল খোলা মুক্ত চিত্ত যেন। এখানে তাঁর গদ্য নির্মাণকৃতিও শীজোফ্রেনিক বর্ণাক্রম যা স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাল সময়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে! তিনি উপন্যাসের যে ক্যানভাস হাতে ধরেছেন সে অস্থির, অনিশ্চিত, উত্তাল (আনন্দের উত্তাল, উদ্দামতা অর্থে নয়) যুদ্ধে আশ্রয় প্রাপ্ত কলকাতায় মুক্তিকামী মানুষের পরিসর! এখানে আহমদ ছফা তাঁর গদ্যরীতি এই অস্থির সময়ের ব্যাখ্যায় শীজোফ্রেনিক। তাঁর এই পরাক্রম বর্ণপ্রভা ওই প্রতিনিয়ত সংযোগ (‘এভার এঙগেজিং’) আর প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত করে চলেছে ! ছফা’র শীজোফ্রেনিয়া এখানে সংগঠিত প্রতিটা অণু পরমাণুর সাথে সেই পূর্বের উল্লেখিত এঙগেজিং সত্ত্বা, কি মানুষের উপকারে, কারো চিকিৎসা নিমিত্তে, কারো রেশন কার্ড তৈরিতে, কারো দেহজ বিকারে, বিবেকের দংশনে, রাজনৈতিক অসততায়, রাগে দুঃখে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিটা রক্তহরণ ও ক্ষরণ হয় নিজের ভেতর। লাইংকৃত সংজ্ঞায়িত শীজোফ্রেনিয়ার প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা ছফার রক্তক্ষরণের প্রতিবাদী কণ্ঠ প্রায়ই রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে দেখি! অর্থাৎ অন্তরভেদী রক্তপাত হয়! এই শীজোফ্রেনিক সত্ত্বাকে দেখতে পাই আমরা অলাতচক্রের যতীন দা’র মুখে যখন তনু’কে আমাদের লেখক দানিয়েলের সাথে পরিচয় করে দেয়া হয় এই বলে যে, ‘আর ও হচ্ছে দানিয়েল, অনেকগুণ, কালে কালে পরিচয় পাবে। তাঁর সর্বপ্রধান গুণ হলো সে ভয়ানক রাগী। নাকের ডগার কাছ দিয়ে মাছি উড়ে যাওয়ার সময় দু-টুকরো হয়ে যায়!’ এখানে আমার যা মনে হয়েছে, যদিও কষ্টকল্পিত শোনাবে না হয়তো, মাছির দু’টুকরো হয়ে যাওয়া যেন ডায়ালেক্টিক্সের কথা। মাছির একটুকরো থিসিস, অন্যটা এন্টি থিসিস ! দুই টুকরো হাওয়ায় ছুড়ে ফেলে ঝেড়ে বের হয় তৃতীয় মাত্রা! ছফা ভাইয়ের দুর্মর ডায়ালেক্টিক্ বিশ্লেষণ প্রসূত স্যন্থেসিস! শীজোফ্রেনিক গদ্যভঙ্গি যে যাই বলুক, তাতে সংকটের বহুমাত্রিকতার ভিতর থেকে তিনি দিতে চান বিপরীত স্রোতের অভিযাত্রার সংকেত! কলকাতায় তাঁর উপস্থিতি না হলে মনে হতো বাঙ্গালীরা আমরা ইতিহাসের একটা আরামদায়ক কমফোর্ড জোনে ব্যাপৃত থাকতাম! তাঁর শীজোফ্রেনিক চোখের প্রিজম খানা যেন সর্বত্রগামী, যেন কোন অবগুন্ঠন আভরণে ঢাকা যাবে না! ছফা ভাই যেন প্রতি তল্লায় সার্ভিলেন্স ক্যামেরা বসিয়ে দিয়েছেন, যা চোখে দেখছেন, আর তাঁর প্রতিক্রিয়া আমাদের ব্যক্ত করছেন ক্ষণে ক্ষণে! এই যেন নীৎশীয় ইভেন্ট! তৈরি করে চলেছেন, প্রতিটি সময়ে প্রতিটি ক্ষণে তিনি নিজের ভেতরকার এনার্জীর সাথে বাইরের এনার্জীর সঙ্গমে একেকটা ইভেন্ট তৈরি করছেন প্রতিনিয়ত! তাঁর এই পর্যবেক্ষণে একটি স্বদেশের বিশাল সংকটের কথা বলে, কিন্তু সকল ডায়ালেকটিক্সে আছে নঞ্চ বোধের স্রোত। মনে হবে স্বাধীনতাকামী মানুষটি এই সকল ব্যাপক অরাজক পরিস্থিতি কেনো প্রত্যক্ষ করছেন? তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জাহিদুল হকের মত স্বেচ্ছাচারীর মত বলবেন হয়ত, ‘তাঁর কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, অন্যান্যের মত মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে সিটি ড্রেনে গড়াগড়ি তো খেতে পারতেন, নিজের নীতি আর বিবেক বিসর্জন দিয়ে কেউ কি আর নেই?’ কিন্তু সেই তর লিঙ্গানন্দে গা ভাসিয়ে না দিয়ে ব্যাতিক্রম হতে পারেন কেউ কেউ, যেমন আহমদ ছফা, জহির রায়হান প্রমুখ চেতনা প্রবাহী মানুষ সকল! ফরাসী দার্শনিক অ্যাঁলা বাদিয়্যূ যা বলেছেন খুব সহজ ভাষায় বললে যা দাঁড়ায় তা হল কোন শ্রমিক’কে যদি কোন প্রতিষ্ঠান ডিস্ক্রিমিনেট করে তাহলে সে অপরাধের শিকার যে ব্যক্তিটির উচিৎ এই অসম সংকট’কে বিচারের দাবীতে ট্রেড ইউনিয়নের চোখে আনা, যাতে তার সততা বা ট্রান্সপারেন্সী সবার দৃষ্টিগোচরিত হয়! ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংকটের ভেতর থেকে একটা স্পষ্ট সততার স্বর ধ্বনিত করতে, সবার দৃষ্টি কাড়তে ট্রেড ইউনিয়নে যাওয়ার মতন কেউ উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, চলচ্চিত্র, সংবাদে তুলে আনতে পারেন ওই বিগ্রহকালের চিত্র। ছফা ভাই এনেছেন কলকাতা অবস্থানকারী একাধিক চরিত্রের কেইস স্টাডি সবার চোখে দৃষ্টিগোচরিত করার ব্জন্যে শুধু নয়, কিন্তু এই বিগ্রহের চিত্রের একটা সমগ্রতা পাওয়ার জন্যে। ছফা ভাই যেন নিজ দায়িত্বে ইতিহাসে দায়মুক্তি ঘটাতে আমাদের সংকট’কে ব্যাখ্যা করতে ফুরসৎ দিয়েছেন! আমেরিকান মার্ক্সিস্ট সাহিত্য দার্শনিক ফ্রেড্রিক জ্যামিসন বলেছেন যে কোন বর্ণনাক্রমে সত্যটা অনুচ্চারিত থাকে, অর্থাৎ ঢাকা থাকে, তা কেবলী ব্যাখ্যায় সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ পায়। অলাতচক্রের কলকাতার রাস্তায় তপ্ত রোদে ঘর্মাক্ত, কোমড় পর্যন্ত বিস্টির পানির সরিয়ে যে শীজোফ্রেনিক অথচ অতিদ্রুত কথন ভঙ্গীতে সে সত্যের বয়ান তার স্রোত বেয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে পারি একটা অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণে! ছফা’র শীজোফ্রেনিক সত্ত্বা আমাদের কি বলে? নেতৃত্বের প্রশ্নে আমরা কি নিরব ভূমিকা নেবো? কলকাতা’র থিয়েটার রোডের সে যুগের নেতৃবৃন্দের নৈরাজ্য আর অজবাব্দিহিতার রাজনীতি কি এখন বিদ্যমান নয়? আমাদের আত্ম-সমালোচনা করার সাবালকত্ব কতো যুগে গেলে পরে দেশের মুক্তি ঘটবে? এর মুক্তি না ঘটলে তো যে কোন পার্টিগত রাজনীতি সহসা হয়ে পড়ে ওলিগার্কির, হয়ে পড়ে ফ্যাসিস্ট! কেন গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতায়ণের অন্যপিঠ কি দূর্বিত্তায়ন?
পহেলা বৈশাখ ও বাঙালী জাতিসত্তা
আলী সিদ্দিকী
সবাইকে বাং লা নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ এলে ঢাকার মঙ্গল শোভাযাত্রায় আওয়ামী ছাত্রলীগ কর্মীদের মেয়েদের উপর হামলা ও বর্বোরচিত শ্লীলতাহানি করার দৃশ্যটি আজো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভিডিও ফুটেজ দেখার পরও অপরাধীদের শনাক্ত করতে না পারার যে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা জাতি দেখেছে- ক্ষমতাবলে যতোই এই ঘায়ের উপর প্রলেপ দেয়া হোক না কেন, সময়ের পাতায় তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনার ”ইলিশ-পান্তা খেলেই বাঙালী হওয়া যায় না” উক্তি, আওয়ামী ওলামা লীগের “মঙ্গল শোভাযাত্রা হিন্দুয়ানী উৎসব” ঘোষণা এবং ছাত্রলীগের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারী নারীদের শ্লীলতাহানি করার ঔদ্ধত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। দঙ্গলবাজদের স্পর্ধা তখুনি সীমাহীন হয়ে ওঠে যখন তাদের মাষ্টার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়।
লা নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ এলে ঢাকার মঙ্গল শোভাযাত্রায় আওয়ামী ছাত্রলীগ কর্মীদের মেয়েদের উপর হামলা ও বর্বোরচিত শ্লীলতাহানি করার দৃশ্যটি আজো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভিডিও ফুটেজ দেখার পরও অপরাধীদের শনাক্ত করতে না পারার যে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা জাতি দেখেছে- ক্ষমতাবলে যতোই এই ঘায়ের উপর প্রলেপ দেয়া হোক না কেন, সময়ের পাতায় তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনার ”ইলিশ-পান্তা খেলেই বাঙালী হওয়া যায় না” উক্তি, আওয়ামী ওলামা লীগের “মঙ্গল শোভাযাত্রা হিন্দুয়ানী উৎসব” ঘোষণা এবং ছাত্রলীগের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারী নারীদের শ্লীলতাহানি করার ঔদ্ধত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। দঙ্গলবাজদের স্পর্ধা তখুনি সীমাহীন হয়ে ওঠে যখন তাদের মাষ্টার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়।
বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতিকে আঘাত করার অপপ্রয়াস নতুন কিছু নয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে (দ্বিজাতি তত্ত্ব- হিন্দুজাতি ও মুসলিম জাতি। যা অবৈজ্ঞানিক ও জবরদস্তিমূলক। ধর্মভিত্তিতে জাতি নয়, সম্প্রদায় হয়। ) বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করে বিজাতীয় পাঞ্জাবী, সিন্ধি ও বেলুচদের অধীনস্থ করে দেয়া হয়। আর তখন থেকেই বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর নানামুখী আক্রমণ শুরু হয়। উর্দু হরফে বাংলা লেখা, রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করা, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা, স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমকে সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষমূলক করে তোলাসহ বিভিন্নভাবে বাঙালী জাতিসত্তার উপর আঘাত নেমে আসে। পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর মতো তৎকালীন মুসলিম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও পাকিস্তানীদের অনুসরণ করতো। কিন্তু মাতৃভাষার অধিকার, বাঙালীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তা রক্ষার্থে গড়ে উঠা আন্দোলনে এবং দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগৃতি রাজনীতিতে মেরুকরণ নিয়ে আসে।
পশ্চিম পাকিস্তানী ভূস্বামী প্রভাবিত ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী জাগরণের ভেতর নিজেদের ভবিষ্যত দেখতে পায়। তারা ভোল পালটে আওয়ামী লীগ নামধারণ করে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী প্রপঞ্চকে রাজনীতির পুঁজিতে পরিণত করে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে বাঙালী জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে স্ফূরণ ঘটে তা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে সূচিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে যায়। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে বেগবান হওয়া উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। প্রথম থেকেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে ও স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ছিলো পূর্ববাংলার বামপ্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ। ভাষা আন্দোলনে তাদের সক্রিয়তা ছিলো প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের পাতিবুর্জোয়া ও উঠতি পুঁজিপতিদের দল দ্রুতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল্ধারায় চলে আসে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো জনপ্রিয় শ্লোগানগুলোকে তাদের মেনিফেস্টোভুক্ত করে নিজেদের গ্রহনযোগ্য করে তোলে। তৎকালীন প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টি দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের সাথে নিয়ে পাকিস্তানী প্রায়উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের নামে মৌলিকভাবে হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে মুসলিম আওয়ামী লীগ ভোল পালটে দ্রুত রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করতে সক্ষম হয়েছিলো।
ফলশ্রুতিতে চুয়ান্ন সালের নির্বাচন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মূলতঃ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে ছিলো না। লক্ষ্য ছিলো, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী দল হিসেবে সর্বপাকিস্তানী সরকারের নেতৃত্ব দেয়া। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও ভূস্বামীরা সামরিক বাহিনীর সাথে আঁতাত করে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে অপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে যায় এবং অপ্রস্তুত বেসামরিক মানুষ পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে বেশুমার হত্যার শিকার হয়। সামগ্রিক জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ হলেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ এককভাবে নিজেদের দখলে রেখে দেয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ যখন ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত জনযুদ্ধে পরিণত হচ্ছিলো এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিলো মুক্তিযুদ্ধের উপর, তখন আওয়ামী পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্ব দ্রুত যুদ্ধের সমাপ্তি টানার সিদ্ধান্ত নেয়। ত্রিশলক্ষ প্রাণ ও দুইলক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক এক রক্তাক্ত সূর্য।
হাজার বছরের ইতিহাসে একটি জাতিরাষ্ট্র বাঙালী জাতির এক অনন্য অর্জন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ হয়ে ওঠে নতুন কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রথমেই চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ যারা মূলতঃ আওয়ামী লীগভুক্ত ছিলো। ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে তারা “বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের” শ্লোগান নিয়ে গণযুদ্ধের ডাক দেয়। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতো তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে প্রচুর তরুণ প্রাণ ঝরে যায় অকালে এবং দেশে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির তৎপরতা বেড়ে যায়। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে সপরিবারে নিহত হন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালীর জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নটি মুখ থুবড়ে পড়লো।
পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও খালেদা জিয়া ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে ঠেলতে ঠেলতে পাকিস্তানী ভাবধারার স্রোতে ফেলে দিলো। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার মূলস্তম্ভের বিকৃতি ঘটানো হলো ইচ্ছাকৃতভাবে। অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো আস্তাকুঁড়ে। স্বাধীনতাবিরোধীরা দখল করে রাষ্ট্রক্ষমতা, বাংলাদেশ পরিণত হয় এক ধর্মরাষ্ট্রে। আঘাতের পর আঘাত করা হলো বাঙালী জাতিসত্তার উপর, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর, অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর, বিকৃত করে ফেলা হলো রক্তমাখা সংবিধান।
আওয়ামী লীগ বরাবরই ক্ষমতার বাইরে থাকাবস্থায় বাঙালী জাতিসত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। সোচ্চার হয়েছে তেয়াত্তরের সংবিধান পুনরুদ্ধারে, লড়াই করেছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে সাথে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আর এই যৌথ লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে। বাঙালী জাতি পঁচাত্তরে মুখ থুবড়ে পড়া স্বপ্নকে নিজেদের ভেতর পুনর্জাগরণ ঘটায় এবং সুতীব্র আকাঙ্খা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে জাতিসত্তার আলোকে ত্রিশলক্ষ শহীদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ গড়ে তোলার।
কিন্তু ক্রমশঃ মানুষের চোখ ছানাবড়া হতে শুরু করলো, ভাঁজপড়া শুরু হলো কপালে, মনের ভেতর ঘাঁই মারতে লাগলো সন্দেহ। প্রথম বড়ো ধাক্কাটি এলো, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখার মাধ্যমে। স্বৈরাচারী এরশাদ সংযুক্ত রাষ্ট্রধর্ম আওয়ামী লীগ বাতিল করবে (এমন প্রতিশ্রুতিও আওয়ামী লীগ দিয়েছিলো ক্ষমতায় যাওয়ার আগে) এটা ছিলো সার্বজনীন প্রত্যাশা। কিন্তু তাতে পানি ঢেলে দেয়া হলো। জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী ছিলো দ্বিতীয় প্রত্যাশা। সেটা নিয়ে নানামুখী ধুম্রজাল রচনা করা হলো। মুখরক্ষার্থে কতিপয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলেও স্বজনপ্রীতির কারণে দাগী যুদ্ধাপরাধীরা পার পেয়ে যায় এবং অপর ধর্মান্ধ দল হেফাজতের সাথে আঁতাত করে দেশকে মদিনা সনদের আলোকে পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহন করে। পাঠ্যক্রমকে ধর্মীয়করণ করে, ওলাম লীগ দিয়ে নারীবিরোধী ফতোয়া দেয়ায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসা নির্যাতনে চোখ বন্ধ করে রাখে, বাউলদের উপর নির্যাতনে নির্বিকার হয়ে থাকে, ৫৭ ধারায় নাগরিক অধিকারে তালা লাগায়, ধর্মীয় কূপমুন্ডকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশব্যাপী উন্মত্ততা সৃষ্টিতে নীরবে ইন্ধন দেয়, বিজ্ঞান শিক্ষককে হেনস্থা করার জন্য বন্দী করে রাখা হয়, ইত্যাদি আওয়ামী লীগের বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনার শক্তির পরিচয়কে যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। তাছাড়া দেশকে পাকাপোক্ত গণতান্ত্রিক শাসন উপহার দেয়ার পরিবর্তে বিনানির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সিভিল স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে মৌলবাদের চর্চাকেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারনের পরিবর্তে পশ্চাদমুখী ধর্মশিক্ষার অন্ধকার গহবরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে।
বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারক হিসেবে বাঙালী জাতি যে রাজনৈতিক দলকে সুদীর্ঘকাল বিশ্বাস করে এসেছে, আস্থা রেখেছে, দেশের-জাতির ভবিষ্যত নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছে বিনা বিচারে-সেই আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী জাতিসত্তার পরিচর্যার পরিবর্তে বায়ান্ন ও একাত্তরের শহীদদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আরবীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে অবাধ করে দিয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার ও থাকার জন্য তারা মুক্তিযুদ্ধকে – বাঙালী জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করেছে কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে বেঈমানি করেছে। তারা পাকিস্তানামলের মুসলিম আওয়ামী লীগের চরিত্রধারণ করে ভেতর থেকে বাঙালী জাতিসত্তার উপাদান বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। তারা এখন ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আস্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় এবং বাংলাদেশকে একটি আরবীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।
এই মুসলিম আওয়ামী লীগের কাছে বাঙালী জাতির এখন আর কোনো প্রত্যাশা থাকতে পারে না এবং আওয়ামী লীগেরও বাঙালী জাতিকে আর কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই। বাঙালিয়ানা চর্চা এখন তাদের শুধুই লোক দেখানো। জাতীয়তাবাদের খোলসে আওয়ামী লীগ এখন আক্ষরিক অর্থে জাতিদ্রোহীদের গোত্রভুক্ত হয়ে গেছে। জাতিসত্তার অস্তিত্বের জন্য বাঙালী জাতিকে বিকল্প শক্তি খুঁজতে হবে।