
গল্পগুলো পাখির ডিমের মতো ভাঙে
ঋতো আহমেদ
আমরা পড়ছিলাম মহামায়াকে। সে ছিল কবি দেবারতি মিত্রের মহামায়া। এবারও আমরা মহামায়াকেই পড়তে পড়তে ঢুকতে চাইবো বাংলা কবিতার আরেকটি অনন্য ভুবনে। আর, এবারের মহামায়া যে কীভাবে স্তম্ভিত করে দেবে আমাদের, আমরা হয়তো টেরও পাবো না। আমাদের চৈতন্যে একটি অদ্ভুত স্পষ্ট অথচ ঘোরাবিষ্ট প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। আমরা দেখতে থাকবো আমাদের চোখের সামনে—
রোদে ভরে আছে দুধ,
নীলাকাশ ব্যেপে আমি ঝুঁকে আছি
মুখপানে চেয়ে—
এই কোলের সীমায় তোরা খেলা কর খোকা, বাছা, সোনা।
পেটে ধরবার সুখ কখনো মেটে না—
কোটি কোটি আয় তোরা— আয় তোরা— আয়, খেলা কর।
:তুই কে রে?
:আমি কুকুরদের আট দিনের খোকা, খেতে পাই না …
:আয় সোনা, সাবধানে গাড়ির তলায় শুয়ে পড়।
: কে রে তুই?
: আমি মানুষের ফুটপাতের খুকু, খেতে পাই না …
: আহা বাছা, সহ্য কর, রাজরানী হবি—
পুরুষের শূল তোর ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়ে আনন্দ করবে—
জয় জয় রক্তে ভাসা গৌরীপীঠ!
রস রক্ত শুক্র নিয়ে জরে আছি—
হঠাৎ উজ্জ্বল আলো! কে বলল: মা, জাগো!
কুকুরকুণ্ডলী থেকে উঠে বসি— স্তম্ভিত বাতাস—
উদরের মধ্য থেকে খাঁ খাঁ শূন্য বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে—
দিগম্বরী নিশি …
খড়ের সন্তানকে আমি অফুরান দুধ দিচ্ছি!— দুধ বয়ে যায়—
দুধ বেড়াল বাচ্চার মতো কাঁদে
আমার সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে ওঠে কান্না
অট্ট অট্ট হেসে মহাকাশে।
(মহামায়া/লাল স্কুলবাড়ি)

আসুন এইবার আমরা মহাকাশ থেকে মাটিতে ফিরে আসি। নেমে আসি বরিশালের গৈলা গ্রামে। কাল প্রবাহের গণনায় ১৯২৬। কী ঘটছিল তখন? বাংলা কবিতার একটি ভবিষ্যৎ নক্ষত্রের উদয় তো হয়েছিলই সেখানে। আর ঠিক তার পরের বছর জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতার বই ‘ঝরা পালক’ হাতে পেলাম আমরা। এরও বছর-তিন পর বাংলা কবিতার প্রবাদ-প্রেমিকা লাবণ্য দাশকে বিয়ে করে ঢাকা থেকে বরিশাল ফিরছিলেন তিনি। তার ঠিক দু’বছর পর ১৯৩২-এ বরিশালের পাশের জেলা চাঁদপুরে জন্ম নিলেন বাংলা কবিতার আরেক ভবিষ্যৎ নক্ষত্র, কাব্য ও গদ্যের গুরু, আমাদের নিহিত পাতাল ছায়া। আবার, জীবনানন্দ যেমন বিয়ের আগে ১৯২৯ এর শেষ দিকটায় আসামে তাঁর প্রথম প্রেম ‘BY (বিওয়াই)’ এর কাছে কাটিয়েছিলেন, তেমনি আমাদের সেই ১৯২৬ এর নক্ষত্র, আমাদের অনন্য ভুবনের এই কবিও তাঁর শৈশবের পর্বটি বরিশালে শেষ করে কৈশোর কাটাতে চলে যান আসামে। তারপর দীর্ঘ এক জীবন। দীর্ঘ জীবন-কবিতা যাপন। আমরা পাঠকেরা সেই কবিতা-জীবনের আকাশে, পরতে পরতে পাখা মেলতে চাই। দেখতে চাই আসমান ও জমিনের অপার সৌন্দর্য। খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়ে আমাদের, আমরা শুনতে পাই—
“একজন দোয়েল কবে গান গাইতে শুরু করেছিল? একজন উদবেরাল কবে সাঁতার কাটতে শুরু করল? একজন মৌমাছি কবে কেমন করে চাক বাঁধতে শিখল? এসব প্রশ্নের উত্তর কি তারা দিতে পারবে? মনে পড়ে চেতনা জাগার পর থেকেই নির্সগ আমাকে দারুণ মুগ্ধ করতো। নির্সগের সৌন্দর্য আমি অনুভব করতে পারতাম— মন কেমন করতো— মন আঁকুবাঁকু করতো। সেই পলায়মান সৌন্দর্যকে আমি মন দিয়ে ধরে রাখতে চাইতাম। অপরিচিত অর্ধপরিচিত যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখ ও আকৃতি আমি বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতাম। তাদের ঐ বাইরের খোলস, নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখে দেখে ক্রমশ আভাস পেতাম তাদের জীবনের, রহস্যের। ক্রমশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু, সময়, মহাকাশ নিয়ে নানা দার্শনিক চিন্তা মাথায় ঢুকল। এই সময় আমার মনে হোতো, আমি হয়তো চিত্রকর এবং ভাবুক। একসময় আর পাঁচটা ছেলের মতো লিবিডো আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। হতে পারে, তারই তাড়নায় আমার কবিতায় মনোনিবেশ। অন্তত আমার প্রথম বই ‘আমরা তিনজন’ সেই কথাই বলে। তারপর একদিন লিবিডো আমাকে দংশন করল। বিষ টেনে নেবার জন্য এই সময় কবিতাই বিষপাথরের কাজ করেছিল। ক্রমে কবিতাই আমার পরম আশ্রয় হলো।” — শিলীন্দ্র ৯৪ সংখ্যায় কমল মুখোপাধ্যায়ের সাথে নিজের কবিতা লেখার সূচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমনই বলছিলেন কবি মণীন্দ্র গুপ্ত। হ্যাঁ, তিনিই আমাদের সেই আলোচ্য নক্ষত্র। তিনি মনে করতেন ‘কবিতা একটি জীবিত প্রক্রিয়ার ফল, এবং সে স্বয়ংও প্রচণ্ডভাবে জীবন্ত।’ কবিতার বীজ কোথা থেকে আসে, এই প্রশ্নে মণীন্দ্র গুপ্তর উত্তরটাও খুব মনে রাখার মতো, ‘এই বীজ, প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক অবস্থায়, আমাদেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে স্মৃতি— অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতি এবং কবিতা যেহেতু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে লেখা যায় না, অর্থাৎ লৌকিক অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না দ্বিতীয় ভুবনের অলৌকিকতায় প্রবেশ করছে ততক্ষণ কবিতার জন্মচক্র সঠিকভাবে আরম্ভ হয় না।’ ক্রমেই আমরা যতোই তাঁর কবিতার গভীরে প্রবেশ করবো, আমরা দেখতে পাবো তিনি কীভাবে চিন্তা আর কল্পনার সাহায্য নিয়ে জীবনের রূপক তৈরি করে যাচ্ছেন একের পর এক। অনেক আশ্চর্য চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে তাঁর বহু কবিতায়, পাওয়া যাবে অসংখ্য সাহসী কল্পনার বিস্তার, অনেক মৌলিক সৃষ্টিশীলতার ঘোষণা আর নৈতিকতা। যদিও দীর্ঘ আলোচনা ছাড়া তাঁর কবিতার বিভিন্ন স্তর বুঝে ওঠা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও। তারপরও আমরা পাঠকেরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে চাইবো তাঁর কবিতায়।
প্রথম দিকের কয়েকটা কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের মনে হতেই পারে জীবনানন্দের কবিতা নতুন ফ্লেভারে পুনর্নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এরপর আস্তে আস্তে যখন আরও গভীরে তলিয়ে যেতে থাকবো, আমাদের মনে হতে থাকবে এ এক অন্য ভুবন। যার সাথে তিরিশ বা পঞ্চাশ থেকে শুরু হওয়া বাংলা কবিতার যে মেজাজ তার কোনো মিলই নেই। একেবারে নতুন এক কাব্যভাষা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।
জীবন দুর্জয় ছিল
ঘরছাড়া যাযাবর বন্য মানুষের।
তাদের সন্তান আমি, আধুনিক এক মানব—
বিবর-বুভুক্ষু আত্মা।
সনাতন সভ্যতার রংচঙে তালি মারা খড়ের পুতুল,
সভ্যতারই তৈরি বেয়নেটে মৃতপ্রায় বিক্ষত শরীর।
(জীবনায়ন/আমরা তিনজন)

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত কবির প্রথম বই ‘আমরা তিনজন’ থেকে পড়তে গিয়ে এই কবিতাটিই নজড়ে এলো প্রথম। অবশ্য তাঁর কবিতাসংগ্রহে (আদম সংস্করণ) এই বইটি গ্রহণ করা হয়নি। একেবারে শেষে কেবল তিনটে কবিতা রাখা হয়েছে। হয়েছে কবির ইচ্ছেতেই। কেননা প্রথম প্রকাশের ভূমিকা পড়তে গিয়ে আমরা জানতে পারি তিনি বলছেন, ‘কারুরই সমস্ত কবিতা উৎকৃষ্ট হয় না। অথচ কোনো-না-কোনো দিক থেকে যে কবিতায় উৎকর্ষ নেই তাকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা অনৈতিক।..অপছন্দের কবিতাগুলো এই সংগ্রহে অগৃহীত থাকল।’ এইভাবে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কবিতাই পরিত্যাক্ত হয়েছে। তাঁর মতে যা বাদ গেছে তা চিরতরেই বাদ গেছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মন কি তা মানে! পাঠক তার মনশ্চোখে খুঁজতে থাকেন কিছু সাধারণ কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর। আর পড়তে গিয়ে পেয়েও যান, কবি নিজের মুখেই বলছেন তাঁর কবিতা লিখতে আসার কার্য-কারণ,— ‘আজ এতদিন পরে কার্য-কারণ আর মনে নেই; তবে স্মরণ করতে পারি, কোনোরকম আবেগ ছাড়াই, নেহাত শখ ও অনুকরণস্পৃহার বশে যখন কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম তখন আমি নিতান্ত বালক। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, এ বিষয়ে হৃদয়াবেগই হয়েছিল আমার চালিকা শক্তি।.. এখন কে আমাকে কবিতা লেখায়? হয়তো অখণ্ড কাল, সর্বব্যাপী জগৎ এবং সর্বত্র স্পন্দিত অগণ্য জলবিম্বের মতো উত্থিত নিমীলিত জীবন। বা এই তিনের সন্নিপাতে তৈরি আলোছায়ার অবর্ণনীয় রহস্য— চিরপরিবর্তনশীল নকশা।’
আমরা ভাবতে থাকি ’৪৯-এর সেই অমোঘ উচ্চারণ, ‘জীবন দুর্জয় ছিল’। ভাবতে থাকি, কার দুর্জয় জীবনের কথা বলা হচ্ছে? ঘরছাড়া যাযাবর বন্য মানুষের? আদিম কালের কথা বলা হলো? জীবন দুর্জয় ছিল’র পরপরই এক নিমেষে তাহলে আমরা মহাকাল পেরিয়ে অনেক পেছনের সেই আদিম যুগে পৌঁছে গেলাম! পৌঁছে গেলাম আমাদের আদি পুরুষদের কাছে। যাদের কোনো ঘরবাড়ি নেই। বন্য পশুর মতোই যাযাবর তারা। ঝড়, জল, রৌদ্র, অমাবস্যায় শিকার করে, বনের অন্য পশুদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে যাদের। মুহূর্তের ভেতর যেন সমগ্র সময়টাই আমার চারদিকে উদ্ভাসিত হয়ে ঘুরতে থাকলো। পর্যায়ক্রমে দেখতে থাকলাম মনুষ্য পৃথিবীর বিবর্তন। আর তার পর-মুহূর্তেই আমার আত্ম-আবিষ্কার— তাদের সন্তান আমি। নিজের পরিচয় জানতে পারা, ইতিহাস জানতে পারা, আপন পরিণতি জানতে পারা— আধুনিক এক মানব আমি। কিন্তু কেমন এই মানব? বিবর-বুভুক্ষু আত্মা বলা হচ্ছে যাকে? একটু আগেই যে পড়ছিলাম, এটা কি সেই মহামায়া’র ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়ে আনন্দ করার একই মানব আত্মা? আধুনিক, অথচ রংচঙে তালি মারা খড়ের পুতুলের মতোই হতভাগ্য। নিজের তৈরি অস্ত্র দিয়ে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করছি। ভয়ানক আত্মবিদ্রুপে জর্জরিত হয়ে যাই যেন।
এইরকম একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে ১৯৪৯ সালে বেরিয়েছিল ‘আমরা তিনজন’। মণীন্দ্রদা বলেন, ‘সবদিক থেকে যাচ্ছেতাই সে লেখা— অসংগত, অশিক্ষিত, প্রথম যৌবনের অবিবেচনা।’ এরপর দীর্ঘ ২০ বছর আমরা আর কোনো বই দেখতে পাই না তাঁর। হয়তো এজন্য যে, সম্পূর্ণ নতুনরূপে আবির্ভূত হবেন আবার। হ্যাঁ, দীর্ঘ আত্মবিস্মৃতির শেষে সেই ঘটনাটি ঘটে যায় ১৯৬৯ এ এসে। আমরা হাতে পাই ‘নীল পাথরের আকাশ’। বিগত সাতাশ বছরে ধীর লয়ে লিখে যাওয়া এইসব কবিতা অন্যরকম জীবন পায় পাঠকের কাছে। আমরা পড়তে থাকি—
বাঁশের ঝাড়ের নিচে খসে পড়া বাঁশের বাকল
শুয়ে থাকে নিরিবিলি।
হলদে ছায়া তালি দেওয়া ফালি জামা গায়ে
দুপুরের রৌদ্র ঘোরে একলা-ছেলের মতো,
হেঁটে যায় বাঁশতলি দিয়ে—
হাওয়া এসে মাঝে মাঝে তার কচি রোমকূপে কেটে যায় বিলি।
নিটোল গভীর ভরা দিন যেন নুয়ে পড়া বেতের লতায় পাকা বেতফল।
(একখণ্ড জমি, একটি দুপুর ও আমার শৈশব/নীল পাথরের আকাশ)
পড়তে থাকি—
জন্মলগ্নে সচিত্র অন্ধকার সঙ্গে করে নিয়ে আসে মানুষের সমস্ত শিশুরা:
গাঢ় পর্দা, পাথরের রেখাঙ্কিত মুখ আর বঙ্কিম জলের ধারা,
পর্দায় অলৌকিক ছবি, তারাদের ছাইচাপা আলো, বহুদূর দিগন্তসরণী,
এ জন্মের পূর্বাভাস, বিগত জন্মের রেশ— অতিপ্রাকৃতিক স্তব্ধ ধ্বনি।
এইসব অন্ধকার অলৌকিক চিত্রশালা বুকে নিয়ে জন্মলগ্নে আমিও এসেছি;
(সচিত্র অন্ধকার/নীল পাথরের আকাশ)

৪৩ বছর বয়সে এসে এমন সব কবিতা নিয়ে হাজির হয়েছেন এই কবি— যেখানে ‘দিনের সীমান্তে শুধু শরণার্থী এসে ভিড় করে’, ‘জন্ম থেকে সে থাকে মুখের দিকে চেয়ে’ কিংবা, ‘যত কাছাকাছি থাকছে, তত তারা চিনতে পারছে না একে অপরকে’র মতো কবিতাগুলো পড়তে পড়তে পারস্পারিক সম্পর্কের মধ্যকার রহস্যগুলো চোখের সামনে দারুণ ভাবে ফুটে উঠতে থাকে।আবার ধরুন ‘ময়লা’ কবিতাটির কথাই—
শরীর থেকে ময়লা তুলতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় না।
সবাই হাসে: ‘তোমার বুঝি ঋতুস্নান?— বছরে ছ দিন!’
আমার কেমন খুব মনে হয়, এসব ময়লা ভালোবাসা।
(ময়লা/আমার রাত্রি)
অবাক হতে হয়, শরীর থেকে ময়লা তুলতে গিয়েও কী আশ্চর্য কবিতার জন্ম হচ্ছে! সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এমন কবিতায় শরীরে ঘামের গন্ধ,মাঠে ফসলের ক্ষেতে পরিশ্রমী যে শরীর আমার, তার রুক্ষ চামড়া ফাটা। যেন আমি এক বৃক্ষ। শরীরে লেগে থাকা এই সবই আমার খুব প্রিয়। হোক সে তোমার চুমু, শিশুর লালা কিংবা গুরুর পদধূলির রজ— চাই যেন সবই আমার সুখ-দুঃখের সাথে জমানো থাক এই শরীরে। পরম মমতা আর ভালোবাসায় জড়িয়ে গিয়ে এদের ছাড়তে চাই না। হ্যাঁ, অবাকই হতে হয়। এইভাবে কি ভেবেছি কখনো? শরীর ঘষে কতো ময়লাই তো তুলেছি গোছলে গিয়ে। কখনো কি শরীরের ওই ময়লার প্রতি এমন ভালোবাসা অনুভব করেছি? আপন ফাটা রুক্ষ শরীরের দিকে তাকিয়ে কখনো মনে হয়েছে নিজেকে বৃক্ষের মতো? তবে কি, লৌকিক অভিজ্ঞতা এখানে দ্বিতীয় ভুবনের অলৌকিকতায় প্রবেশ করছে আর কবিতা হয়ে উঠছে!
ফিরতি ট্রামের গায়ে লেখা ছিল
দৈবাক্ষরে:
এই নদীর পাড়ের সন্ধ্যা চিরদিনকার মতো গেল
— আর কখনো ফিরবে না।
আমি কেঁপে উঠতেই
স্বগত ধরনে গাঢ় রাত
নীল নক্ষত্রের নিচে
স্থির-বলল:
পৃথিবীপারের দেশ
কী সুন্দর!
যে যায়— ফেরে না।
(ত্রিযামা ১/মৌপোকাদের গ্রাম)
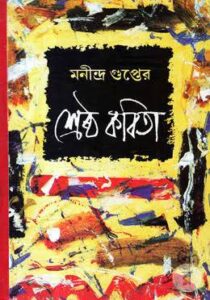
ফিরতি ট্রামের গায়ে লেখা এইসব দৈবাক্ষর কাদের চোখে পড়ে? যাদের চোখ আছে দেখার তারাই তো দেখতে পায়: এই যে নদীর পাড়ের সন্ধ্যা একটু আগেও ছিল এইখানে, এখন নেই, চলে গেল, চলে গেছে কালপ্রবাহের স্রোতে। এই সন্ধ্যাটুকু আর ফিরে আসবে না। সন্ধ্যা মানে তো সময়ই। সময় ফিরে আসে না, আমরা জানি। এই সত্যটুকু অনুধাবন করতেই যেন কেঁপে উঠি আমরা। কোথায় যায় সে? পৃথিবীপারের দেশে। এক ধরনের শূন্যতা আর হাহাকার বোধ বয়ে যায় ভেতরে। তারপর নেমে আসা গাঢ় ওই রাত নীল নক্ষত্রের নিচে স্বগত স্বরে বলে, পৃথিবীপারের দেশ কী সুন্দর! তার এই বলাটাও স্থির। শাশ্বত। যেন এইভাবে, এমনতর নীল নক্ষত্রের রাত সব সময়ই বলে। শুধু আমাদের দেখার চোখের মতো আমাদের শোনার মনও চাই। পৃথিবী পেরিয়ে যে দেশ রয়েছে তা এতোটাই সুন্দর যে, যে ওদেশে যায় সে আর ফিরে আসে না।
মণীন্দ্রদার কবিতাগুলো যেন শুধু কবিতা নয়। গল্প বলার ছলে কবিতা লেখেন তিনি। ছোট ছোট এক একটি ঘটনার গল্প বলতে বলতে শেষে কবিতা হয়ে ওঠে। ‘দেবী ও ভাস্কর’ কবিতায় কবিতাটি শুরু হয় গল্প বলার ভঙ্গিতেই— ‘অনেক দিন আগে, দৈবের বশে কলাভবনের ছাত্রী জয়া আপ্পাস্বামী রুপোর স্তম্ভের মতো উল্লম্ব ইউক্যালিপটাস গাছেদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল’ বলতে বলতে। তারপর একসময় ‘তার রোমকূপের রোম নুয়ে নুয়ে পড়ে। আমি কিন্তু সেসব দেখি নি।’ রামকিঙ্কর জয়ার সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটির যে মূর্তি তৈরি করলেন সেটি শান্তিনিকেতনের সেই ইউক্যালিপটাস বাগানে স্থাপন করা আছে। এমন লাবণ্য ভরা সৌন্দর্য সেই জয়ার যে, ঠিক ঠাহর করা যায় না কখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে। ‘খর দুপুরে, না সন্ধ্যায়, না পূর্ণিমার অন্ধকারে’? আরেকটি গল্পের কথা বলতে খুব লোভ হচ্ছে। গল্প নয়, যেন এক মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্য—
যেদিন শুনলাম, পায়ে হাঁটা পথে আলেকজান্ডার
ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, আর চীন থেকে
সিল্ক রুটের পথে গুটিপোকা—
সেদিন বিশ্বাস হল সবই সম্ভব— পৃথিবী থেকে
মহাপ্রস্থানের পথে হেঁটে হেঁটে স্বর্গে পৌঁছানোও সম্ভব।
রাত্রে শুয়ে মহাপ্রস্থানের কথা ভাবি:
বরফে সাদা হয়ে আছে পর্বতশৃঙ্গ, নীচে পপলারবন,
তারও নীচে দেবদারুবন।
তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে অস্ত্রহীন ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির চলেছেন—
দেহ ঢেকে নিয়েছেন লোমশ পশুর চামড়ায়।
সঙ্গে এক হাড়-জিরজিরে করুণ কুকুর।
তুষারে পথের রেখা মুছে গেছে।
হিমপর্বতমালায় সৎকার-না-হওয়া শব হয়ে
পড়ে আছে ভাইয়েরা আর দ্রৌপদী।
আর পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা উপন্যাসের ধূসর মলাটের
মতো হয়ে আছে যুধিষ্ঠিরের মন।
পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা লিখতে সমস্ত কালি ফুরিয়ে গেছে,
মলাটে লেখা অস্পষ্ট নাম আর পড়া যায় না।
চরাচরে ধূসর— ধূসর— আবছা— এবং আরো আবছা—
যুধিষ্ঠির এবং কুকুরও একটু একটু করে আবছা হচ্ছেন—
তাঁদের যতটুকু আবছা হচ্ছে ততটুকুই স্বর্গে প্রবেশ করছে—
ক্রমশ তাঁরা পুরোই আবছা হয়ে স্বর্গে ঢুকলেন।
(স্বর্গারোহন/অগ্রন্থিত কবিতা)
‘তাঁদের যতটুকু আবছা হচ্ছে ততটুকুই স্বর্গে প্রবেশ করছে— ক্রমশ তাঁরা পুরোই আবছা হয়ে স্বর্গে ঢুকলেন।’ — এই পঙক্তির মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের এই গল্পটি শেষ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি অবাক-করা কবিতা হয়ে উঠেছে। এভাবেই যেন তাঁর এইসব গল্পগুলো পাখির ডিমের মতো ভাঙে আর কবিতা হয়। আমাদের মাথার ভেতর সৃষ্টি করে অলৌকিক ভুবন। আমরা অবাক হই অত্যন্ত সাধারণ কিছু উদাহরণের মাধ্যমে তিনি আমাদের এমন স্বিদ্ধান্তে উপনীত করান যে, আমরাও ভাবতে থাকি, পৃথিবী থেকে মহাপ্রস্থানের পথে হেঁটে হেঁটে স্বর্গে পৌঁছানোও সম্ভব। বুঝতে চেষ্টা করি পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা মহাভারত উপন্যাসের ধূসর মলাটের মতো যুধিষ্ঠিরের মনটাকে। তুষারপাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কী ভাবছিলেন তিনি? কিছু কি ভাবছিলেন? আমরা দেখতে পাই পেছনে হিমপর্বতমালায় সৎকার-না-হওয়া শব হয়ে পড়ে আছে তার ভাইয়েরা আর দ্রৌপদী। আবার যদি ব্যাসদেবের সেই মহাকাব্যের মহাপ্রস্থান পর্বটুকুও পাঠ করতে যাই তো দেখি, পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার শেষ দিকে এসে স্বর্গের পথে এগুচ্ছেন যুধিষ্ঠির তার পরিবার নিয়ে। ধূসর ও আবছা হতে হতে ওই পথ চলে গেছে হিমালয়ের দিকে।—
‘যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ-কে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং যুযুৎসু’র উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে চার ভাই ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানের প্রস্তুতি নেন। এই সময় তাঁদের সাথে ধর্মদেবতাও কুকুররূপে সঙ্গ নেন। পথিমধ্যে চার ভাই ও দ্রৌপদীর পতন ঘটে। এরপর একমাত্র কুকুরকে সঙ্গী করে তিনি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তিনি কুকুরসহ স্বর্গে প্রবেশ করতে দিবেন না। উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভুভক্ত কুকুর ছাড়া স্বর্গে প্রবেশ করলে, তা নির্দয়তা হবে। সুতরাং কুকুর ছাড়া তিনি স্বর্গে প্রবেশ করবেন না। এরপর ধর্ম কুকুরের রূপ পরিত্যাগ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ‘যুধিষ্ঠির তোমার সমান স্বর্গে কেউ নেই।’ স্বর্গে প্রবেশ করে তিনি তাঁর ভাইদের দেখতে চান। দেবদূতরা তখন তাঁকে নরকে নিয়ে যান। সেখানে ভাইদের দেখতে পেয়ে স্বর্গে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালে, ইন্দ্র তাঁকে বলেন যে, যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে দ্রোণাচার্যের সাথে প্রতারণা করেছিলেন বলে, তাঁকে কৌশলে নরক দর্শন করান হলো। এরপর, ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করলেন।’
অভাবিত সুন্দর এই কবিতাটি কেন যে অগ্রন্থিত রয়ে গেল! বড়ো কবিদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমনই হতে দেখেছি আমরা। জীবনানন্দের হাজার হাজার কবিতা অপ্রকাশিত রয়েগিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অপ্রকাশিত এইসব ভাণ্ডারেই খুঁজে পাওয়া যায় রত্ন কবিতাগুলো। আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের কবিতা পড়ি আসুন। এই কবিতাটি পড়তে পড়তে আমরা আবিষ্কার করবো মণীন্দ্রদার দারুণ রসবোধের দিকটিও।
টলিউডের ইন্ডাস্ট্রিতে মস্তিকা চট্টোপাধ্যায়
আজকাল তার দুষ্টবুদ্ধির জন্য খুব সুনাম করেছে।
পুরোনোরা বলেন, ঐ রকম দুষ্টবুদ্ধি ছিল
ম্যাডামের।
সেদিন উদীয়মান নক্ষত্র ঋগ্বেদের সঙ্গে
লিপ-লক চুমু খাবার রোমাঞ্চকর দৃশ্যে নামার আগে
দুটি কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেল মস্তিকা
কত আশা করে এসেছিল ঋদ্বেগ— অ্যাকশনে নেমেই থমকে গেল:
— কাট— কাট— কাট— কাল আবার রিটেক—
পরদিন মেকাপের পর দু টুকরো বোয়াল মাছ ভাজা খেয়ে
ঋদ্বেগে মস্তিকার সন্মুখীন হল।
মস্তিকাও এগিয়ে এল।
এবং এবার সবার চক্ষু ছানাবড়া—
গার্লিক উইদ বোয়াল
রান্না হল একখানা দারুণ!
(কেমিস্ট্রি/অগ্রন্থিত কবিতা)
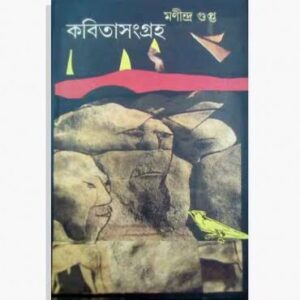
‘ক্রোধের রং কান্না, উল্লাসের রং বিচ্ছেদ, হুল্লোরের রং ঔদাসীন্য। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার ভাষা ও গঠন গদ্যভূমিক চালে চলতে চলতেই ওইসব রঙের বহুস্তর ব্যঞ্জনার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে যায়। পাঠক উপস্থিত হন অভাবনীয় এক জগতে— অনুভব করেন, তাঁর পরিচিত ও আচরিত জীবনছক পালটে অজানিতেই এক নতুন জীবনের অংশীদার হয়ে গিয়েছেন তিনি।’ — কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে যখন বিরতি দিই তখন উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ে কবিতাসংগ্রহের ফ্ল্যাপে এই রকমই কিছু কথা লিখা আছে তাঁর সম্পর্কে। এবং মিলেও যায় কথাগুলো। এমনই তো মনে হচ্ছিল আমাদের। আমরা আবিষ্কার করি তিনি বলছেন, ‘কেবল ভালো লেখাই যে অমর আর খারাপ লেখা জলের রেখার মতো এমন নয়। অনেক দুষ্ট লেখা আছে যা নাভিমূলের মতো কিংবা প্লাস্টিকের মতোই দুর্মর।’
তুমি সহজ পথে ভেতরে ঢুকতে দাও নি
তাই কর্কস্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ভেতরে সেঁধুচ্ছি।
কার বেশি লাগছে?
তোমার না আমার?
মাঝে মাঝে জল খাই,
পিঠের শিরদাঁড়ার ওপর হাত রেখে দেখি, দারুণ ঘেমেছ।
(বলাৎকার/এক শিশি গন্ধহীন ফ্রেইগ্রানস)
যতোই পড়ছি তাঁর কবিতা ততোই অভিভূত হচ্ছি বিস্ময়ে। সচিত্র শিহরণকর বর্ণনায় কখনো হয়ে উঠছি চেতনাঘন। আবার কখনো সংবেদনশীল কিন্তু আলগা। কিছুটা উদাস আর নিস্পৃহ। সময়ের বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ না থেকে কখনো-বা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তিনি সময়াতীত সময়ে।
মেহেরপুরের একশো বছর আগেকার
এক অসাধারণ বৃষ্টির দিন—
আমি দেখি নি, আমার বাবা দেখেছিলেন, যার বয়স তখন বারো।
সহজ গণিত— আজ আমার বয়স একশো বারো হলে
আমিও বাবার পাশে বসে সেই বৃষ্টি দেখতে পেতাম।
বাবা সমবয়সী আমাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে সেই
জলে ভেসে যাওয়া উঠোনে ফেলে দিত,
অথবা হয়তো আমিই তাকে ফেলে দিতাম…
তারপর হাসতে হাসতে হুড়োহুড়ি করতে করতে
দুজনে দিঘিতে গিয়ে পড়তাম।
(বৃষ্টি/টুং টাং শব্দ নিঃশব্দ)
এও এক অভাবিত কবিতা। বাবার প্রতি গভীর ভালোবাসায় বাবাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই কবিতার সৃষ্টি। মনে পড়ছে গত বছর এই রকমই একটি কবিতা পড়ছিলাম কবি Franz Wright এর। ছোট বেলায় বাবাকে কাছে না পাওয়ার বেদনা থেকে উৎসারিত বাবাকে বন্ধু রূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কবিতা ছিল সেটিও। বয়স হওয়ার সাথে সাথে মানুষের অন্তর্জগতের গভীর থেকে উঠে আসে দীর্ঘ আগে হারিয়ে যাওয়া অনেক অপ্রাপ্তির কথাও। ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবনের শেষ দিকে এসে মণীন্দ্রদার তেমনই অনেক কথা কবিতা হয়ে আসছিল। আমরা অবশ্য সব কবিতাকেই ছুঁতে পারি না, সে আমাদের আপন অযোগ্যতাই। তবে, আমাদেরও বয়স আর জীবন অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে আমরাও এগিয়ে যেতে থাকবো মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার আরও গহিনে ছড়িয়ে যেতে।
জীবনের সম্পূর্ণতা নিয়ে মণীন্দ্রদা যখন বলেন, ‘আয়ু যখন সমাপ্ত হয়ে এল জীবনকে তখন সবচেয়ে অসমাপ্ত অপ্রস্তুত বলে মনে হয়— এ এক গভীর প্যারাডক্স। আমার অসমাপ্ত জীবন, আমার অপ্রস্তুত মুখ প্রতিবিম্ব হয়ে আমার কবিতাও অসমাপ্ত আর করুণ হয়ে আছে।’ — তখন আমরা ভাবি, একজন কবির হয়তো নিজের কবিতাজীবন নিয়ে এমনই মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের, মানে সেই কবির কবিতার পাঠকদের কী মনে হয়? কী মনে হয় তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে? পৃথিবীর শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করে জীবন? মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে বয়ে যায় বনমর্মর? আসুন আমরা পড়তে থাকি। আরও গভীরে নেমে যাই।

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*





