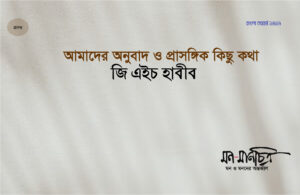শান্তির জন্য যুদ্ধ নাকি শিক্ষা
কামরুল আহসান
“তুমি যদি কাউকে ঘৃণাও করো তবু তুমি তাকে খুন করতে পারো না। কারণ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তুমি তার মতো আরেকটা মানুষ খুঁজে বের করতে পারবে না; ”- কার্ল সাগান।
যে-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাউকে হত্যা করতে হয় সে- বিশ্বাস দিয়ে তুমি কী করবে! যে-বিরুদ্ধ বিশ্বাসকে ধ্বংস করে তুমি নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তুমি কি নিশ্চিত একদিন তোমার পক্ষ থেকেই কেউ তোমার বিরোধী হবে না! যুগ যুগ ধরেই এটা হয়েছে। সমস্ত ধর্মে, সমস্ত রাজনৈতিক দলে। তার মানে কি এই যুদ্ধ যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকবে!
মানবসভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীতে এই পর্যন্ত কতো যুদ্ধ হয়েছে? গুগুলে সার্চ দিয়ে যে-লিস্টটা আমি পেয়েছি তা দেখে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা। খৃস্টপূর্ব ২২৭১ সালের উরুক যুদ্ধ থেকে ২০১১-এর বেঙ্গাজির যুদ্ধ পর্যন্ত সাড়ে আট পয়েন্টে তার তালিকা এ ফোর সাইজের ৬৫ পৃষ্ঠা! সেটা গুণে দেখা অতিমানবিক কাজ। তারপরও আরো যুদ্ধ হয়েছে। এখনো যুদ্ধ চলছে সিরিয়ায়, মিশরে, লেবাননে, ইরাকে, ইউক্রেনে। দুদিন পর পরই যুদ্ধ লেগে যায় ফিলিস্তিন আর ইসরাইলে। মানবসভ্যতার এতোটা সময় পার করে এসেও যখন এখনো এসব সমস্যার সমাধান হয়নি তাহলে আর কবে হবে?
২.
এক বিজয়ী বীর বলেছেন, “আমি যুদ্ধ করি জয় লাভের আনন্দ উপভোগ করার জন্য নয়, বরং যুদ্ধ আমাকে চিন্তার ভার থেকে মুক্তি দিয়েছে” (মিথ অব সিসিফাস, আলবেয়ার ক্যামু)
সত্য কী তাই? যুদ্ধ মানুষকে চিন্তার ভার থেকে মুক্তি দেয়? এই জন্যই সবাই যুদ্ধ করে! কিন্তু, মার্ক্স তো বলেছেন, যুদ্ধ হচ্ছে শ্রেণীদ্বন্ব। শোসক ও শাসিতের লড়াই।
লীগ অব নেশন্স্ থেকে আইনস্টাইনকে অনুরোধ করা হয় তাঁর সময়ের এমন একজন মানুষকে বেছে নেয়ার জন্য যার সাথে আলাপ করে যুদ্ধের ভয়াবহ বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে কি-না তা জানতে এবং জানাতে। আইনস্টাইন বেছে নেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে যোগ্য মানুষটিকেই, ফ্রয়েডকে।
আইনস্টাইন এক দীর্ঘ চিঠি লিখেন ফ্রয়েডকে, “আপনি বিশ্বশান্তির সমস্যাটি আপনার সাম্প্রতিকতম আবিস্কারের আলোকে আমাদের জানান, কারণ এই ধরনের আলোচনা হয়তো এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন ও অধিকতর ফলপ্রসূ কার্যবলীর পথের সন্ধান দিতে পারবে।”
ফ্রয়েড তার উত্তরে সুদীর্ঘ এক চিঠি লিখেন আইনস্টাইনকে। ফ্রয়েড লিখেন, “…যেখানে স্বার্থের বিরোধ ঘটে সেখানে আমরা হিংসার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করি।…সব বিরোধই প্রায় সর্বদা অস্ত্রের সাহায্যেই মীমাংসিত হয়েছে। এই ধরনের যুদ্ধ একপক্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা অন্য দলের জয় ও ক্ষমতাচ্যুতিতে শেষ হয়। …যুদ্ধ নিশ্চিতভাবে তখনই বন্ধ করা সম্ভব হবে যখন মানব-গোষ্ঠী এমন এক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হবে যার হাতে সব রকম বিরোধিতার ন্যায়-বিচারের দায়িত্ব থাকবে।” (এবং মুশায়েরা, ফ্রয়েড সংখ্যা)
পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে-পরিমাণ পারমানবিক বোমা মজুদ আছে তা দিয়ে এই পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা সম্ভব। হয়তো মানুষ কখনো তা বিস্ফোরিত করবে না, অনেকে হয়তো তা বিশ্বাসও করে; কিন্তু, তা মজুদ রাখারই অর্থ কী? অন্যকে ভয় দেখানো! সত্যি বলতে, এটাও একটা বিধ্বংসী প্রবণতা এবং আত্মহত্যার চেয়ে কম ভয়াবহ নয়।
হিটলারের কাছে পারমানবিক বোমা থাকলে কী হতো? আত্মহত্যা করার আগে সে কি পুরো পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিয়ে যেত না! সমগ্র মানবসভ্যতা বেড়ে উঠছে এই আত্মহত্যা-প্রবণতা নিয়েই।
মানুষের সামনে এখন দুটি পথ আছে: প্রচুর রক্তপাত, আরেকটি ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ, রক্তের বন্যা দেখে যদি তার হুশ হয়। আরেকটি তার শিক্ষা।
৩.
পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এ-পর্যন্ত যতোদূর বিকশিত হয়েছে তার আলোকে মানুষের পক্ষে এক প্রকার যৌক্তিক জীবন-যাপন সম্ভব। কিন্তু, তারপরও মানুষের জীবন খুব যৌক্তিক হয়নি। এটা বুঝতে পন্ডিত হতে হয় না। এখনো মানুষের সাথে মানুষের যে তীব্র প্রতিযোগিতা, এতো যুদ্ধ, এতো হানাহানি, এতো রক্তপাত এসব কোনো সুস্থ সমাজের পরিচয় নয়। শুধুমাত্র দুটো চিন্তা, দুটো বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই একটি দেশ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্যই একটি দল আরেকটি দলের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। মানবসভ্যতার এতোটা সময় পার হয়ে এসে এখনো যখন মানুষ খুব বেশি যৌক্তিক হয়নি তাহলে আমরা খুব সহজেই ধরে নিতে পারি আসলে শিক্ষার সঠিক বিকাশ হয়নি।
একজন মানুষ খারাপ বা ভালো না, তার চেয়ে বেশি জরুরি সে সুস্থ কিংবা অসুস্থ কিনা। আসলে তাও নয়, একজন মানুষকে বিচার করা উচিত সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত তা দিয়ে। শিক্ষা মানে আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা বলছি না। শিক্ষা মানে হচ্ছে তার ভাষাজ্ঞান। অর্থাৎ, সমাজের জন্য সার্বজনিন যা মঙ্গলময় তার সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল কিনা। আমি আপনাকে খুন করতে চাইলে আপনিও আমাকে খুন করতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষকে খুন করে ফেলে তাহলে আসলে পুরো মানব স¤প্রদায়ই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে যায়। তারপরও অনেক মানুষ অনেক মানুষকে খুন করে। করে কারণ সে ভাবে খুন করে সে পালাতে পারবে। কিন্তু, সে ভাবে না, সে আসলে পুরো সর্বজনীন একটা আইনকেই হত্যা করল। একটা সর্বজনীন আইনকে হত্যা করা মানে হচ্ছে আসলে সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করে ফেলা। সে ভাবে না কারণ তার ভাষাজ্ঞান নাই। তার ভাষাজ্ঞান নাই মানে হচ্ছে সে অসুস্থ। অসুস্থ মানে সে অশিক্ষিত।
শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারটা আসলে হাস্যকর। কারণ, একজন সচেতন মানুষকে অনিবার্যভাবেই মানবতার সমস্ত দায় কাঁধে বহন করতে হয়।
মানুষের সমস্যাটা বেঁচে থাকা নয়, বরং বেঁচে থাকার জন্য একটা মহত্তর আদর্শ নির্ধারণ করা।
মৃত্যুর আগে জেনে যাওয়া যে, যে-পৃথিবীতে আমি জন্মেছিলাম মানুষের বাসযোগ্যের জন্য পৃথিবীটা সহনশীল ছিল। বা করে তোলার চেষ্টা করেছিলাম।
কোনো সমস্যাই কি আসলে স্বয়ংক্রিয় কিনা, নাকি আরোপিত? যদি আরোপিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই কারো উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মানুষকে শোষণ করার জন্য পুঁজিপতিরা নানা উপায়ই আবিস্কার করেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সমাজে কৃত্রিম উচ্ছৃঙ্খলা চালিয়ে রাখা। যেন সাধারণ মানুষ সব সময় একটা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষকে সচেতন হতে না দেয়া, শিক্ষার সঠিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটানো। যদি তাই হয় তাহলে এটা এখন আমাদের জন্য খুব অনিবার্য হয়ে গেছে যে, আমাদের জীবনের প্রকৃত শিক্ষা কী সেটা খুঁজে বের করতে হবে।
৪.
আপনি অস্ত্রের কারখানা চালু রেখে শান্তির কথা বলতে পারেন না। যখন একটি গুলি আবিষ্কৃত হয় তখন সাথে সাথে একজন মানুষের মৃত্যুও নিশ্চিত হয়। ইরাকে, সিরিয়ায়, ফ্রান্সে, ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে মানুষ মরে, আর পৃথিবীর নানাপ্রান্তে মানুষ গুমড়ায়। যার যার জায়গা থেকে যে যতোটুকু পারে আলোচনা-সমালোচনা করে। আমাদের প্রতিবাদে কি কিছু আসে যায়? সাধারণ মানুষের আর্তনাদ কার কানে পৌঁছায়?
এটা এক ধরণের দায়মুক্ত হওয়ার প্রবণতা। কিন্তু, সত্যিকারার্থে আমরা কি দায়মুক্ত হতে পারি?
এটা ফ্রয়েডের কথাই, যুদ্ধের জন্য সমাজের প্রত্যেকটা মানুষই কোনো না কোনোভাবে দায়গ্রস্ত।
একজন সৈনিক যখন সৈনিকের চাকরি বেছে নেয় তখন সে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধকেই প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কেউ বাধ্য হয় সৈনিকের চাকরি বেছে নিতে। কিন্তু, এ কথাও তো সত্য, যদি সে সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতো তাহলে সৈনিকের চাকরি বেছে না নিয়ে অন্য কিছু করতে পারতো।
জাতি-রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজন। কিন্তু, আভ্যন্তীন নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটে কেন?
প্রথমত, অবশ্যই, সম্পদগত সুষোমবণ্টনের অভাবেই।
দ্বিতীয়ত, মতাদর্শগত বিরোধের কারণে।
আমরা হয়তো সম্পদেরও সুষোম বণ্টন করতে পারি। কার্লমার্কস যে-সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেখানে সম্পদের সুষোম বণ্টন হতে পারে। কিন্তু, পৃথিবী যদি একদিন স্বর্গও হয়ে যায় তবু মতাদর্শগত বিরোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এ আমি বিশ্বাস করি না।
একই মতাদর্শ নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর একই গোত্রের মানুষ আবার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে ভাগ হয়ে গেছে এমন উদাহরণ হাজার হাজার। পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধর্মে, প্রত্যেকটা দর্শনে এটা হয়েছে। আপনি যদি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আপনার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করতে করতে আসেন এবং অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে করতে আসেন তাহলে অন্য প্রান্তে আসতে আসতে দেখবেন পেছনের সব বিশ্বাসই বদলে গেছে এবং তারপর আবার আপনাকে নতুন করে হত্যাকাণ্ড শুরু করতে হবে।
আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে সাতশো কোটি মানুষ, এবং সাতশো কোটি মানুষের সাতশো কোটি মাথা। নানামুণির নানা মত এর চেয়ে চরম সত্য কথা আর কিছু নেই। মতাদর্শগত বিরোধ সম্পূর্ণ ঘুঁচানো না গেলেও একটা মার্জিন লেবেলে সবাই এক হয়। এক হয় বলেই সাধারণ মানুষ পাশাপাশি থাকে। কিন্তু, এই মতাদর্শ বিরোধগুলোই আরো প্রবলভাবে জিইয়ে রাখা হয় ওই সম্পদের একচেটিয়া ক্ষমতাভোগের জন্যই।
সাধারণভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত, যার যার যোগ্যতায় সে সে সম্পদ অর্জন করে। হ্যাঁ, আমি যদি সেই সত্য মেনেও নেই, তবু আমি দ্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, নিজের যোগ্যতা দিয়েও যদি কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করে এবং সেগুলো নিজেই ভোগ করে, তাহলে সে যতেই জ্ঞানী হোক, যতোই ভালো মানুষ হোক তাকে আমি সভ্য মানুষ বলতে নারাজ।
একজন মানুষ যদি পাঁচশো-একহাজার বছর বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো বলতে পারতাম তার একশ-দুইশ কোটি টাকা দরকার। কিন্তু, ষাট-সত্তর বছর আয়ু নিয়ে যে-মানুষটা পৃথিবীতে আসে তার বেঁচে থাকার জন্য কতোটুকু সম্পদের দরকার? কিছু কিছু মানুষ এতো অঢেল সম্পদ আকড়ে ধরে রাখে যেন মনে হয় সে কোনোদিন মরবে না। বেশির ভাগ মানুষই আসলে জীবনটা কী তা নিয়ে খুব গভীরভাবে ভাবে না। জৈবিক লোভ-লালসা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহীত করে।
সক্রেটিস তাঁর জবানবন্দিতে বলছেন, “হে আমার মহান এথেন্সনগরীর বন্ধু! জ্ঞান এবং আত্মার উন্নয়নের প্রতি তোমার লক্ষ্য নিবন্ধ না করে কেবল অর্থ, সম্মান এবং সুখ্যাতির সঞ্চয়ে কি তুমি লজ্জা বোধ কর না?…আমার দৈনন্দিন আলাপনে আমি যেরূপ ন্যায়পরায়ণতা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং অপর সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, তাই হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গলবিধায়ক এবং জিজ্ঞাসাশূন্য জীবন অর্থহীন বই আর কিছু নয়…”(সক্রেটিসের জবানবন্দি, প্লেটোর সংলাপ, অনুবাদ-সরদার ফজলুল করিম)
এই যে একটা পৃথিবীতে আমাদের জন্ম হয়েছে, মনে হয়, এ জীবন তো আমার পাওনাই ছিল! কিন্তু, হঠাৎ করে চেতনায় যখন ধরা দেয়, হোয়াই এ্যাম আই! হোয়াই! বর্তমান পৃথিবীর সাতশো কোটি মানুষের মতো আমিও কি একটা সংখ্যা? আমার আগে পৃথিবীতে কতো শত কোটি কোটি মানুষ আসছে, গেছে। আমার পরেও আসবে, যাবে। এর মধ্যে আমি কেন? এই পৃথিবীতে আমার কর্তব্য কী? বেশির ভাগ মানুষই এইসব প্রশ্নের উত্তর যার যার বিশ্বাস দিয়ে চালিয়ে নেয়। সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীতে এতো বিশ্বাস এবং বিশ্বাসগুলো এতো বৈপরীত্যে ভরা, একটা বিশ্বাসকে আরেকটা বিশ্বাস দিয়ে বাতিল করে দেয়া সম্ভব।
পৃথিবীতে প্রচলিত দুটি প্রধান বিপরীত বিশ্বাস: আস্তিক্য এবং নাস্তিক্য।
নাস্তিক হওয়া আসলে খুব সহজ। যা দেখি না তা মানি না। যদি সমস্ত সৃষ্টিরই কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকেন তাহলে অনিবার্যভাবে সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন। সে কে? সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু হয় তাহলে মানুষের কৃতকর্মের ফলের ভাগীদার কে? আবার তিনি যদি থাকেনই কীরূপে আছেন? এইরকম হাজারো প্রশ্ন আছে। তার ওপর ডারউইনের বিবর্তনবাদ তো আছেই হাতের কাছে। যাতে তিনি বলেছেন মানুষ আসলে বিবর্তনের ফল। মানুষ আর পশুর সাথে কোনো পার্থক্য নেই। দুচারটা বই পড়লেই ঠাঠা নাস্তিক হওয়া যায়।
আস্তিক হওয়া আরো সহজ। বাপ-দাদার ধর্ম। ধর্মকর্ম করলে করলাম না করলে নাই। বিশ্বাস করে বসে থাকলাম। যা ঘটছে তার দায়ভার উপরওয়ালার ওপর চাপিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত।
আস্তিক ও নাস্তিক দুটো হওয়াই খুব সহজ। কঠিন হচ্ছে এই সমস্তসৃষ্টিজগতকে নিজের ভিতর ধারণ করা। নিজেকে এই সৃষ্টির অংশ করে তোলা।
মানুষ একই সাথে বস্তু এবং চৈতন্য।
বস্তুগত যে-দেহধারণ আমরা করি তার প্রতিটি উপাদান এই পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা। খাদ্য যখন সামনে থাকে তখন সেটা একটা বস্তু, খাদ্য যখন আমরা খেয়ে ফেলি তখন সেটা আমার সত্তার অংশ হয়ে যায়। বুকের ভিতর যতক্ষণ বাতাস থাকে ততক্ষণ আমার প্রাণ থাকে। আমরা যতোবার শ্বাস নেই ততোবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হই। চৈতন্যও জাগ্রত হয় বস্তুগত প্রতিফলনের কারণেই। নির্জন অন্ধকারে হঠাৎ একটা শব্দ হলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণীরই কান খাড়া হয়ে যায়, গা ছমছম করে ওঠে। এটা একেবারে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর আদিম বৈশিষ্ট্য। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সতর্কতা থেকেই এটা হয়। কিন্তু, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম ছাড়া চেতনাকে মহাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়ার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কারো নেই।
একমাত্র মানুষই তার বোধবুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে যে-দেহগত জীবন নিয়ে সে এখন আছে একদিন সে এখানে থাকবে না। সে তার পাশের লোকটিকে চলে যেতে দেখে। তার প্রিয়জন, বাবা-মা, দাদাদাদীকে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় জীবিত মানুষের কোনোদিনই তা জানা সম্ভব না। জীবিত মানুষ শুধু এতটুকুই জানে, যে মরে যায় সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না।
মৃত্যুবোধই মানুষের মনে জন্ম দেয় অসীম এক শূন্যতার। এই মহাকালে আমি আর থাকবো না! আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে! ধর্ম মানুষকে অমরত্বের নিশ্চয়তা দেয়। তাই যারা এক কথায় ধর্মকে বাতিল করে দিতে চান স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ক্ষেপে ওঠে, কারণ, তাতে করে তো তাদের জীবনই বিপণ্ন হয়ে যায়। ধর্ম একটা আশ্রয়। পরম আশ্রয়।
কিন্তু, মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়ারই-বা অর্থ কী? এই ভাবনা থেকে নাস্তিক্যবাদী মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন।
পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু, এ নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ কী? ধার্মিকেরা কি মনে করেন কেউ নাস্তিক হয়ে গেলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করে দিবেন? কেউ কি শখ করে নাস্তিক হয়? নাকি নাস্তিকতা কোনো রাজনৈতিক দল? কোনো ফায়দা লোটা যায় তাতে? আসলে তারা ঈশ্বরকে না, প্রতিষ্ঠা করতে চায় নিজেদেরই। তারা নিজেরাই ঈশ্বর হয়ে উঠতে চায়।
নাস্তিকেরাই কেন-বা উঠেপরে পরে লাগে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে বাতিল করে দিতে? নাস্তিকেরা কি মনে করেন কেউ ধর্ম বিশ্বাস করলেই তার জীবন অর্থহীন হয়ে গেল! আসলে তারা ঈশ্বরকে বাতিল করতে চান না, তারা তাদের অহমকে প্রতিষ্ঠা করতে চান।
শেষ পর্যন্ত নাস্তিক-আস্তিকের যে-দ্ব›দ্ব সেখানে ঈশ্বরের কোনো জায়গা নাই, সেটা পুরোটা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত অহম-প্রতিষ্ঠার জায়গা।
এর মূল কারণ, অপরকে বুঝতে না চাওয়ার অপারগতা। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন ধার্মিকের তো বরং একজন নাস্তিকের প্রতি মায়াই হওয়া উচিত, আহারে, না জানি কোন অজ্ঞতার ফলে সে মহান প্রভুর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে! এমনটাই তো ভাবা উচিত। ভালোবেসে তাকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসা যাওয়া যেতে পারে। তার কাছে ঈমানী দাওয়াত পৌঁছে দেয়া যেতে পারে, সে গ্রহণ না করলে কিছু করার নেই। তারও বিরুদ্ধ মত শোনা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।
জোর করে যেমন কারো বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তেম্নি জোর করে কারো বিশ্বাস ভাঙ্গাও যায় না। এটা একেবারেই নিজস্ব শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিকতার কারণে গড়ে ওঠে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের রেষারেষি হাজার বছর ধরেই। একটার ভিত্তি বিশ্বাস আনুগত্য, আরেকটা চায় তাৎক্ষণিক যুক্তি-প্রমাণ। এ-জন্য বারট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝখানে একটা বেওয়ারিশ এলাকা আছে, সেই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করে দর্শন। ধর্মও যেমন দর্শনের অন্তর্গত, তেমনি বিজ্ঞানও। দর্শনের মূল কাজ সমাজে একটা সমতা প্রতিষ্ঠা। দ্ব›দ্ব-সংঘাতের নিরসন। দর্শনও বিতর্কের জন্ম দেয়, বস্তুত দর্শনমাত্রই বিতার্কিক, কিন্তু, তা অহিংসাত্বক। বরং যে-সমাজে সুষ্ঠ বিতর্কের সংস্কৃতি নেই সে-সমাজই অধিকমাত্রায় সহিংস। বিতর্কের সংস্কৃতি নেই মানেই সে সমাজে দর্শনচর্চা অনুপস্থিত। অবিসম্ভাবি সে সমাজের ভাষা হয়ে উঠে অস্ত্রের, সংঘাতের, হানাহানির, রক্তপাতের।
৫.
মানুষের চিন্তা-চেতনা-দর্শন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে কোনো শান্তি আসে নি। বরং দিন দিন অস্থিরতা বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের সাথে মানুষের তীব্র প্রতিযোগিতা। সমগ্র মানবসভ্যতা এখন দাঁড়িয়ে আছে আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে। পৃথিবী এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে-স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে তাকেই অনেকে অভিহীত করেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে। তাহলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারি কীভাবে?
আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিণতি মানে পৃথিবী নির্ঘাত ধবংসের মুখোমুখি হয়ে যাওয়া। বারার্টান্ড রাসেল এ নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করে গেছেন। মানুষের কি কোনো ভবিষ্যত আছে নামক গ্রন্থে তিনি একদম জরিপ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, মানুষের হাতে এ মুহূর্তে যে-পরিমাণ পারমাণবিক বোমা মজুদ আছে তা দিয়ে এই পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা সম্ভব।
মানুষের হাতে মজুদকৃত অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে মানুষের হাতে মজুদকৃত জ্ঞান দিয়েই। তিন হাজার বছরের জ্ঞান দিয়ে যদি মানুষ সভ্য না হয় তাহলে আর কবে হবে!
আবার এ কথাও সত্য, জ্ঞান আসলে মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।
পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কতো কতো মতোবাদ (ইজম) এসেছে, আর কতো কতো ‘বাদ’ বাদ হয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। বুদ্ধবাদ, খৃস্টবাদ, ইহুদিবাদ, মুসলমানবাদ, হিন্দুবাদ, জেনবাদ, সাংখ্যবাদ, যোগবাদ, মায়াবাদ, জৈনবাদ, ভাববাদ, বস্তুবাদ, দাদাবাদ, জাদুবাস্তবতাবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ, সংশয়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, অস্তিত্ববাদ, সেচ্ছাচারিতাবাদ, একত্ববাদ, বহুত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, কলাকৈবল্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সা¤্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, আধুনিকতা বাদ ‘বাদ’ গিয়ে এখন চলছে উত্তরাধুনিকতাবাদ।
এইসব সমস্ত বাদই হচ্ছে একেকটি গোষ্ঠির মতোবাদ। বিশ্বাস। যারা যে-বাদে বিশ্বাসী তারা মনে করেন তাদের মতানুসারী হলেই পৃথিবীটা শান্তিময় হয়ে যায়। এবং অন্য মতোবাদগুলো নিতান্তই অচ্ছুত, কার্যকারণহীন! এই বিশ্বাস নিয়েই লাগে গন্ডগোল। শুধুমাত্র নিজস্ব বাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হয়ে গেছে প্রচুর রক্তপাত, যুদ্ধ’র পর যুদ্ধ। যার যার বাদ (ইজম)-এর পক্ষে লেখা হয়েছে প্রচুর বইপুস্তক । আপনি যদি এক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ইতিহাস পড়েন তাও শেষ করতে পারবেন না।
আবার এ কথাও সত্য, মানুষের কি এতো এতো জ্ঞানের দরকার আছে? ষাট-সত্তর বছরের আয়ু নিয়ে আসে যে-মানুষটি তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় তিন হাজার বছরের জ্ঞান! তাহলে মানুষ জীবনকে যাপন করার যোগ্য হবে কখন?
আমি বলি, জীবনকে, মানুষকে, এই পৃথিবীকে, এই বিশ্বব্রহ্মাÐকে উদারভাবে, নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারলেই আর কোনো সমস্যা হয় না। তার জন্য অবশ্য কিছু জ্ঞান দরকার। জ্ঞান ছাড়া তো ভালোবাসাও সম্ভব না। জ্ঞানই সর্বোচ্চ ভালোবাসা। জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে অসীম এই মহাবিশ্বে নিজের তুচ্ছতাকে অনুভব করা। যখন মানুষ নিজের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখনই এটা অনুভব করে। হামবড়া ভাব তো সে দেখায় যে অন্ধ ও ঘুমন্ত। বেশির ভাগ মানুষই জীবন কাটায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু হয় তার জন্ম হওয়ার আগে। জ্ঞানের পথে পা বাড়ানো মানেই সেই অনাদিকালের ঘুম থেকে জেগে ওঠা। জ্ঞান ছাড়া আর কোনোকিছুই অন্তর থেকে মানুষকে পরিবর্তন করতে পারে না। জ্ঞান ছাড়া আর কোনো বিপ্লব, আইন-আদালত, জোরজবদস্তিতেই আমার আস্থা নাই। মানুষকে মন থেকে ট্রান্সফার হতে হবে। আর তা করতে পারে একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত, জ্ঞানই সর্বোচ্চ জেহাদ, জ্ঞানই একমাত্র বিপ্লব। কথা হচ্ছে জ্ঞান কী? যা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখায় তাই জ্ঞান।
জ্ঞানের নামে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তথ্যের বোঝা। একই বিষয় নিয়ে হাজার বছর ধরে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে অথচ একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই দেখা যাবে তাতে মানবসভ্যতা অগ্রসর হয়নি একপাও। নিছক তথ্য আহরণ জ্ঞান নয়। তথ্য সবাইকে পরিবেশন করা যেতে পারে। জ্ঞান খুব অল্প মানুষই আহরণ করে। জ্ঞান সবার জন্য না। জ্ঞান একমাত্র তার জন্য যে নিজেই নিজের সমুদ্র খুঁড়ে চলে। তথ্য গেলানো যায়। জ্ঞান খাওয়ানো যায় না। জ্ঞান হচ্ছে এমন এক সরোবর যেখানে ডুব দেয়া যায়। ডুব দিয়ে ভেসে উঠার পর যখন পৃথিবীরে এক মায়াবী নদীর পাড়ের দেশ বলে মনে হয় তখনই বলা যায় জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন হলো।
৬
বিরোধ যে শুধু চিন্তার পার্থক্যের কারণেই ঘটে তা না, বিরোধ ঘটে মূলত স্বার্থের কারণে। মূলত স্বার্থই জন্ম দেয় বিরোধীতার। স্বার্থের কারণেই আমরা বুঝতে পারি না অন্যের ভাষা। মানুষ তো প্রথমত পশু– জৈবিক। শারীরিক প্রয়োজনেই তার কিছু আরাম-আয়েশ দরকার। বেশির ভাগ মানুষ জীবনটাকে ক্ষয় করে ফেলে শরীরের ক্ষুধা মেটাতে গিয়েই। এই জন্যই মনীষিরা বলছেন আত্মার মুক্তির কথা। আত্মার মুক্তি মানে জীবন ও জগত সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা। অতিরিক্ত অর্থকরী থাকলে এই জন্যই আত্মার মুক্তি হয় না। বাড়তি অর্থের তো বাড়তি কিছু টেনশন আছে। সেগুলোর প্রতি আলাদা মনোযোগ দিতে হয়। সেগুলোর হিসেবরক্ষার ব্যাপার আছে।
হাফিজের কাছে এসেছেন এক ব্যবসায়ী। বললেন, আমি খোদার সন্ধান চাই।
হাফিজ বললেন, তোমার কী কী সম্পদ আছে তার হিসেব দাও আগে।
ব্যবসায়ী বললেন, বেশি কিছু নেই, আমার ষাটটি উট, দুশটি ভেড়া, ছশটি খেঁজুর গাছ, সাতজন স্ত্রী, আর সাতাশজন ছেলেমেয়ে।
হাফিজ বললেন, এতো কিছু সামলে তুমি খোদাকে ডাকবে কখন!
জীবনকে ভোগ করার নামে শেষ পর্যন্ত কিছু মানুষ জীবনকে ধর্ষণ করে। মানুষ আসলে মানুষ হয়ে উঠে তার চেতনায়। শরীরবৃত্ত থেকে না বেরোলে চেতনার বিকাশ সম্ভব না। প্রত্যেক মানুষই যেহেতু তার তার শরীর নিয়ে বাস করে, তাই শারীরিক প্রয়োজনেই সে স্বার্থপর। ভারী ভারী জ্ঞানের খবর কজন রাখে? সমাজ চলে আসলে ভাসমান জ্ঞানে। শুনে-দেখে জীবন সম্পর্কে মানুষ একটা ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করে। সেগুলো দিয়েই জীবন চালিয়ে দেয়।
সামষ্টিকভাবে একটা সমাজে যে-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাই হচ্ছে সেই সমাজের জ্ঞান। সে সমাজে কতোজন পন্ডিত লোক বাস করে তা দিয়ে সামাজিক জ্ঞানের পরিমাপ হয় না। সমস্যা হচ্ছে সামাজিক এই জ্ঞানও হয় নিয়ন্ত্রিত। শাসনকর্তারা তাদের ইচ্ছে মতো এই জ্ঞান খাওয়ায়।
শিক্ষার সঠিক বিকাশ হয় নাই। জ্ঞান-অর্জনের প্রাথমিক শর্ত ছিল অস্তিত্ব-অন্বেষণ। সেটা হয় নাই। সমাজে-রাষ্ট্রে কিছু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার- কেরানি-সেলসম্যান দরকার। সারা পৃথিবী জুড়েই বিশাল কর্মিবাহিনী তৈরি করা হয়েছে। মানুষ তৈরি করা হয় নাই, যন্ত্রের সমার্থক কিছু রোবট তৈরি করা হয়েছে।
যেহেতু মানবিক জ্ঞানের বিকাশ করা হয় নাই সেই জন্য আমরা দেখি একজন ডাক্তার ডাকাত হয়ে গেছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার চোর হয়ে গেছে। একজন লেখক হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দালাল।
দোষ দেব কাকে?
এটা কোনো ব্যক্তি মানুষের দোষ না, আবার ব্যক্তি দোষমুক্তও না। ব্যক্তি মিলেই তো বৃহত্তর সমাজ।
হোটেলে, বাসে দেখি মানুষ সমাজ-রাষ্ট্রকে সমানে ধুয়ে দিচ্ছে। অনেকে আছেন, ব্যক্তিগত সমালোচনাকে দোষনীয় মনে করেন; কিন্তু, বৃহত্তর সমাজকে সমালোচনা করাও মূলত নিজেকে মহত্তর করাই। বৃহৎ সমাজকে সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমি দায়মুক্ত হলাম এবং নিজেকে সমাজের যে উপরে প্রতিষ্ঠিত করলাম। মাছ ধরলাম কিন্তু পানি ছুঁলাম না।
সমালোচনা অবশ্যই দরকার, কিন্তু তার আগে দরকার এই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা। শুধুমাত্র সমালোচনা করেই দায়মুক্ত হওয়া নয়, বরং দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়ে সমাজকে বদলানোর চেষ্টা করাই মনুষ্যকর্তব্য। অনেকে মনে করেন, আমাদের কথায় কি কিছু আসে যায়? আমাদের কথায় কিছু নড়েও না, চড়েও না। কতো বিখ্যাত সব মানুষজন আসছেন গেছেন তাঁেদর কথাই কেউ শুনছে না। আমাদের আর্তনাদ কার কানে পৌঁছাবে? তারপরও যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যতোটুকু পারি সমাজ-বিকাশে ভূমিকা রাখা উচিত। আপনি যদি শুধু নিজের কথাই ভাবেন, তাহলে শুধু নিজের জন্যই বাঁচলেন। কিন্তু, আপনি যদি সমগ্র মানবতা নিয়ে ভাবেন তাহলে আপনি সমগ্র মানবসভ্যতার অংশ হলেন।
কী এক সমাজ গড়ে উঠল পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এখন প্রত্যেকটা মানুষকে সন্দেহ করে। কী হবে জানি না, কিন্তু, এ কথা আমাদের জানাতে হবে, আমার কাছে তোমার ভয় নাই।
মনে পড়ছে শাহযাদ ফিরদাউসের ’লামেদ ওয়াফ উপন্যাসটির কথা। ইনছান তার বাবা-মা, আত্মিয়-স্বজন, বন্ধু সবাইকে হারিয়ে ফেলে লাভ করে এই পৃথিবীর অসুস্থ আত্মা। রাস্তার এক পাগল তাকে বলেন, এই অসুস্থ পৃথিবীটাকে তোর সুস্থ করে তুলতে হবে। কারণ, তুই একজন লামেদ ওয়াফ। লামেদ ওয়াফ মানে খাঁটি মানুষ। এই পৃথিবীর সবাই একজন খাঁটি মানুষ। কিন্তু, কেউ তা জানে না।