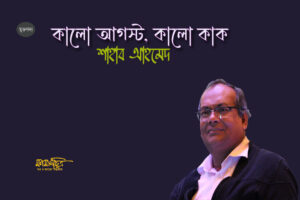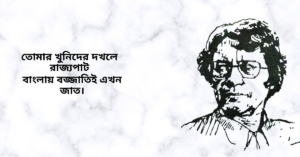তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ‘মেধা’ ও ‘মেদের’ মধ্যে তফাৎ নেই
লাবণী মণ্ডল
গ্রন্থ পর্যালোচনা :: ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রচিত ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’ বইটি শেষ করার মধ্যদিয়ে এটুকু আরও পরিষ্কার হলো যে, জানার কোনো শেষ, শেখারও কোনো শেষ নেই। জীবন মানেই জানা আর শেখা। সেই জানাকে কাজে লাগানোর জন্য, মানুষের জন্য কিছু করার জন্য–মানুষের মধ্যে নিজের জ্ঞানকে বিতরণ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস এ লেখাটি। একই সাথে এ লেখার যে কোনো মতামত আমাকে বিকশিত করবে বলে প্রত্যাশা করছি।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু বই। এখন পর্যন্ত এ সত্যটিকে বিশ্বাস করতে চাই, এ কথাটির উপর আস্থাও রাখতে চাই। একটা বই যে মানুষকে কতটা আন্দোলিত করতে পারে–তা তো আর বলে বুঝানো যাবে না। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, বই আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়। নিজেকে নতুন করে ভাবার জন্য, নতুন করে আবিষ্কার করার জন্য সহযোগিতা করে। যা হোক, ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’ বইটি পড়ে বেশ কিছু প্রশ্ন এরই মধ্যে আমার চিন্তাজগতে প্রবেশ করেছে। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য আরও কিছু বইয়ের দারস্থ হতে হবে। আলোচ্য বইটিতে মোট দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রতিটা প্রবন্ধই চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। অভাব, সংস্কৃতি, চেতনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এ বইটি থেকে।
‘মনুষ্যত্বের শত্রু ও মিত্র’
‘মনুষ্যত্বের শত্রু ও মিত্র’ নতুন করে ‘মনুষ্যত্বে’র সংজ্ঞা দেয়। ‘মানুষ বড়, না কি মনুষ্যত্ব?’ প্রশ্ন করতে দৃঢ়ভাবে সহযোগিতা করে। মানুষ যদি না থাকে, তবে তো মনুষ্যত্বের কথা আসেই না–একই সাথে মানুষের যদি ‘মনুষ্যত্ব’ই না থাকে, তবে কি তাকে ‘মানুষ’ বলা যাবে? আমরা খুব করে বলি, মানুষকে ভালোবাসো। আসলে কোন সে মানুষ, যাকে ভালোবাসবো, যার ভেতরে মনুষ্যত্ব নেই, তাকে কী ভালোবাসবো, সেও তো মানুষই। না কি তাকে ভালোবাসবো না, তাকে আঘাত করবো, তার শ্রেণিকে আঘাত করবো, তার মতাদর্শকে আঘাত করবো–তা না–হলে মানুষের ‘মনুষ্যত্বে’র প্রয়োজনবোধ হবে না। নিজেকে শোধরানোর মানসিকতা জন্ম নেবে না। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে জাগাতে হলে তাকে আঘাত করতে হয়। তাকে দৃঢ়ভাবে বলতে হয়, তুমি ভুল। তোমার মতাদর্শ ‘মানুষের’ জন্য কোনো উপকারে আসছে না। তুমি এই মনুষ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী খুব সহজভাবে এ বিষয়গুলো বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন।
এ মনুষ্যত্বহীন মানুষগুলোকে ‘মানুষ’ করার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। তার জন্যই আঘাত করতে হবে, আঘাতের মধ্যদিয়ে ভালোবাসার বোধ জাগাতে হবে। স্বার্থপর, প্রতারক কেন তৈরি হয় তার পেছনের ইতিহাসটা আমাদের জানতে হবে! মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বকে সুবিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যারা হৃদয়হীন, চেতনাহীন, নিষ্ঠুর–তাদেরকে মানুষ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। এই মানবিকবোধটুকু এ প্রবন্ধটি খুব গুরুত্ব দিয়েই বুঝাতে সক্ষম হয়েছে।
‘ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ’
‘ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ’ প্রবন্ধটি কবি, সাহিত্যিকদের শ্রেণিচরিত্র, সাহিত্যচরিত্র বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবিনসনকে এই ছোট লেখাতে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়বাদের ব্যাপারটিও তুলে আনা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথকে শুধু এর মধ্যেই আটকে রাখতে চাচ্ছি না, আরও পড়তে চাই, জানতে চাই। হয়তো এ প্রবন্ধটি ওই তাগিদটা বাড়িয়েছে। কবি–সাহিত্যিকদের তথাকথিত সামন্তীয় ধ্যান–ধারণা চিন্তা–চেতনা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি স্পষ্ট একটা রূপরেখা টেনেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক স্বাধীনতার বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘সামন্তবাদ সাম্প্রদায়িকতাকে শক্তিশালী করেছে–ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়ে। এবং সামন্তবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদ–বিরোধী হয়েছে তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, যে সন্ত্রাসবাদের মানসপট বঙ্কিমচন্দ্র অনেকাংশে রচনা করে দিয়ে গেছেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের বাইরে যায়নি। বলতে কি, সাহিত্যে প্রতিফলিত জাতীয়তাবাদী চেতনাও সামন্তবাদী এবং সেই কারণে সাম্প্রদায়িক চেহারা নিয়েছে। জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সাহিত্য এর বিরোধিতা করা দূরের কথা, পৃষ্ঠপাষকতাই করল।’ তার প্রতিটি কথা গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করার মতো। তবে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘সামন্তবাদী মূল্যবোধ দূর করতে হলে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বিনষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ পরিবর্তন আনতে হয় ভূমিব্যবস্থায়। জমিদারি জিনিসটা যে অন্যায়, একথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বলেছেন। ‘কালান্তরে’ নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছেন, ‘জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত।’ ১৯৩০–এ রুশ ভ্রমণের পর তার মত দাঁড়িয়েছিল, ‘জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, চাষির।’
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জমিদারি ছেড়ে দেবার প্রসঙ্গ আসলেই তিনি বলতেন, ‘ছাড়বেন তা বটেই, কিন্তু দেবেন কাকে?’ তিনি ভাবতেন, যাকে দেবেন, সেই তো জমিদার হয়ে উঠবে। অর্থাৎ একজন বড় জমিদার চলে যাবে, ছোট ছোট জমিদার গড়ে উঠবে। জমিদার যাবে, আসবে, কিন্তু জমিদারি তো যাবে না। একথাগুলোর অর্থ তিনি আসলেই চাননি–তার জমিদারিব্যবস্থাকে ছাড়তে। আমার রবীন্দ্রনাথপ্রেমী বন্ধুরা আমাকে অনেকবার এই একটি কথা (‘ছাড়বেন তা বটেই, কিন্তু দেবেন কাকে?’) টেনেই আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন। তারা একবার দ্বান্দ্বিকভাবে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, রবীন্দ্রবিদ্বেষী মনোভাব থেকে কোনোকিছু স্পর্ধা আমি বলছি না, তবে তাকে নিয়ে আরও গবেষণা হোক, এটা চাইতেই পারি। তার যতটুকু গ্রহণ করার ঠিক ততটুকুই করুন–তাকে পূজা করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত। এ বইটি হয়তো আপনাদের জন্য কিছু উপাদান দেবে।
‘সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নে’
‘সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নে’ প্রবন্ধটিতে লেখক সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা পাঠকের মন আলোড়িত করে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন–মেধাও অনেক সময় বোঝা হয়, অনেকটা বুঝি মেদের মতো, যদিও মেদ ও মেধায় ব্যবধান চিহ্নিত করার জন্য তার্কিকের দরকার নেই। মেধাকে সঠিকভাবে মানুষের জন্য কাজে লাগাতে না পারলে, তা মনুষ্যসমাজের কোনো উপকারে না আসলে–সে মেধার দরকার কী? মেদের মতো লালন–পালন করার দরকার কী?
আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখন এরকম মেধাবীদের সংখ্যাই দিনদিন বাড়ছে। তা সমাজের সার্বিক চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। যে সমাজে এতো অনিয়ম, বৈষম্য–সে সমাজের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। এই নগণ্যতা থেকেই বোঝা যায় তাদের ‘মেধা’ আর ‘মেদের’ মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই।
‘বিজ্ঞানের ছেঁড়া তার’
‘বিজ্ঞানের ছেঁড়া তার’ প্রবন্ধটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিজ্ঞানের তথাকথিত নিরপেক্ষতার বিষয়টি পরিষ্কার করেছে। লেখক ব্যাখ্যা করেছেন, ‘বিজ্ঞানের তথাকথিত নিরপেক্ষতা অস্ত্রের নিরপেক্ষতা বৈ অন্যকিছু নয়। অস্ত্র তুমি কার? যখন যার হাতে থাকি তখন তার। অথচ বলা তো যেতে পারে, এবং বললে বিশ্বাসযোগ্যও মনে হবে যে, অস্ত্র একেবারে নিরপেক্ষ বন্দী বিজ্ঞান অসহায় হয়ে পড়ে থাকে, অধিপতি শ্রেণির হাতে। সেই শ্রেণি তাকে ব্যবহার করে একাধারে উপভোগের সামগ্রী এবং শোষণের যন্ত্র হিসেবে। একাধারে বাতি জ্বলায় এবং মানুষ মারে। শোষণকারীর হাতে বিজ্ঞানের এ দশা একেবারেই অনিবার্য।’ এ ব্যাখ্যা সত্যিই মুগ্ধকর। তিনি আরও বলেছেন, ‘যে কৃষক দুধ দোয়ায়, অভুক্ত রাখে প্রথমে গরুর শিশুকে এবং তারপর নিজের শিশুকে, সে যখন সেই দুধ তুলে দেয় লঞ্চে–দুধ শহরে যাবে বলে, গিয়ে ধনীদের জন্য মিষ্টি তৈরি করবে বলে, তখন বোঝা যায় লঞ্চের বিজ্ঞানটা কি কাজ করছে। কার সেবা করছে, এবং কাকেই–বা মারছে। কৃষকের ঘর থেকে ধানপাট, মাছ–দুধ কাজের মানুষ সবকিছুই বিজ্ঞান নিয়ে আসে তার দৈত্যের মতো অমিত শক্তিতে। নিয়ে আসে শাসকশ্রেণীর করতলে। তার প্রয়োগ ও তার ব্যবহার ধনী দরিদ্রের বৈষম্য একাধারে বর্ধিত ও সুদৃঢ় করে।…’
এরপর আর শ্রেণিবৈষম্যের বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিজ্ঞানও একটা শ্রেণির সেবা করছে, ওই শ্রেণির শিক্ষা–সংস্কৃতি–চর্চাকে বিকশিত করার জন্য। বিজ্ঞানেরও শ্রেণিচরিত্র আছে!
‘গৃহে গৃহে শিক্ষা’
‘গৃহে গৃহে শিক্ষা’ প্রবন্ধে তিনি যে বিষয়টিতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হলো–শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সন্তানদের আস্থাহীনতা। যদি ছেলেমেয়েদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা থাকতো তবে তো আর ‘গৃহে গৃহে শিক্ষা’ দেওয়ার জন্য শিক্ষক দরকার ছিল না।
শিক্ষকরাও আস্থা হারিয়েছেন সমাজের। আস্থা হারিয়েছেন সম্মানের উপর। নিজের আমিত্বের উপর। যে কারণে সম্মান ধুয়েমুছে খেয়ে এই পুঁজিবাদের দারস্থ হয়েছেন। এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদেরকে শিখিয়েছে আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই!
‘কবিতা, রাজনীতি ও দারিদ্র্য’
‘কবিতা, রাজনীতি ও দারিদ্র্য’ আমাদেরকে স্পষ্টভাবে শেখায়, দারিদ্র্য এ দেশের মানুষের মন থেকে চিন্তার মৌলিকত্ব কেড়ে নিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে সর্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তার উপর! গড়–পড়তা শিক্ষিত বাঙালি চিন্তা করে না, মুখস্থ করে। আমরা এর প্রমাণ পাই–সর্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষার খাতায়।
এ প্রসঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল ইকোনমির প্রফেসর জেমস স্টকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘মানুষের মুক্তি পুঁজি বিনিয়োগে নেই, পুঁজি বিনিয়োগের পূর্বে প্রয়োজন ভূমি–মালিকানার পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ব্যাপক সামাজিক বিপ্লব।’ বিপ্লবী না হয়েও তিনি উপলব্ধি করেছেন–সংস্কৃতির সমস্ত অহমিকা ও অভিমান, রাজনীতিকের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণত ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই কথাটির উপর ভিত্তি করেই আমরা বলতে চাই–সমাজের পিরামিডটাকে উল্টে দিতে হবে!
‘মধ্যবিত্তের জীবন’
‘মধ্যবিত্তের জীবন’ সম্পর্কে খুবই সহজ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনসঙ্গী উদ্বেগ। উচ্চমধ্যবিত্তও এ থেকে মুক্ত নয়। তাদেরও নানান উদ্বেগ নিয়েই দিন–রাত কাটে। হা–হুতাশ তাদের জীবনের আর সব ভাবনাকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। কারণ, এদের বেশিভাগের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অবস্থান, মতাদর্শ, দর্শন পরিষ্কার নয়। তারা নিজেরাও জানে না কি করবে, করা উচিত।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, ‘পেটই প্রধান সমস্যা। বিত্তহীন কৃষক ও শ্রমিকের তো বটেই, মধ্যবিত্তেরও। দরিদ্র খাবার পায় না, নিম্নমধ্যবিত্ত পুষ্টি পায় না। খাদ্য যারা পায় তারা খাদ্য নিয়ে বিলাস করে, মান–অভিমান করে, বাছবিচার করে। এটা খায় না, ওটা খায় না। কোনটা রানের, কোনটা পিঠের, তেল ভাসল কি ভাসল না, খেয়ে হজম হয়েছে কি হয়নি, তা নিয়ে আলোচনায় বিস্তর সময় কাটে। ওদিকে নিম্নবিত্তের গৃহিণীর জীবনের বেশিরভাগ কাটে স্যাঁতসেঁতে অতিসামান্য রান্নাঘরে।’
‘সমাজ ও স্বাধীনতা’
বাঁচার জন্যই স্বাধীনতা চাই, অর্থাৎ মুক্তি চাই। মুক্তি কার হাত থেকে? দারিদ্র্য থেকে, অর্থাৎ শোষণ থেকে। এই মুক্তির জন্যই ছুটছে মুক্তিকামী মানুষ। যে মুক্তিকামী মানুষকে ‘সমাজ ও স্বাধীনতা’ সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে, বোঝাচ্ছে সমাজের চিন্তাশীল মানুষরা।
স্বাধীনতা কেবল মানসিক বোধের ব্যাপার নয়; বস্তুতে অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপার। কিন্তু এই সহজ ব্যাপারটাকে অত সহজভাবে ভাবতে দেয় না, শাসকশ্রেণি। যে শ্রেণিটা এই সহজ বিষয়টিকে জটিল থেকে জটিলতর করে।
‘স্বাধীনতা’র সংজ্ঞা একেক জন একেকভাবে দিয়ে থাকেন, যার যার সুবিধামতো। বিত্তবানেরাও স্বাধীনতা চায়। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন চায় না। মুক্তিকামী জনসাধারণের সাথে এখানেই বিত্তবানদের মূল তফাৎ, শুধু তফাৎ নয় বিরোধও। যে বিরোধ এখন অব্দি রয়েছে। যতদিন এই সমস্যাগুলোর সমাধান না হচ্ছে ততদিন বিরোধ থাকবে।
‘শিশুকে বাঁচাও’
শিশুর মানসিক বিকাশ, শিশুর সাথে মাতৃত্বের গুরুত্ব নিয়েই প্রবন্ধটি। একটি শিশুর বেড়ে উঠার পেছনে যেহেতু মাতৃত্বের গুরুত্বটাই প্রধান সেহেতু সমাজের দৃষ্টিতে মাতৃত্বকে হেয় করার কোনো এখতিয়ার নেই বলেই স্পষ্ট করেছেন লেখক। শিশু এই সমাজের ভবিষ্যৎ ‘পুঁজি’, সেই শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন।
‘শিশুকে বাঁচাও’–এই ধ্বনি আজ আর্তধ্বনি। শিশুকে বাঁচাতে হবে সমাজের হাত থেকে, এই সমাজই তাকে মারছে, ব্যক্তির হাত দিয়ে। দৈহিকভাবে, মানসিকভাবে একটা শিশুকে মেরে ফেলছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। সুতরাং এই শিশুদেরকে বিকশিত করার দায় এই রাষ্ট্র নিতে পারে কি? আমাদেরই এর দায় নেওয়ার জন্য নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিশুকে সৎ, চরিত্রবান, আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে কতটা লাভবান হবো, যদি সমাজটাই বসবাসযোগ্য না হয়!
তাই শিশুকে বাঁচাতে হলে, মানবিক করতে হলে সমাজকে বদলাতে হবে। পরিবেশকে করতে হবে স্ববিরোধিতামুক্ত, সদয়, সহযোগী। কিন্তু সমাজ বদলাবে কেমন করে? কোন উপায়ে, সেকি বদলাবে মুখের কথায়, ধমকে, কিংবা প্রলোভনে–মোটেও না। সমাজ পরিবর্তনে চাই বিপ্লবী সংগঠন, আন্দোলন, সংগ্রাম। বিদ্যমান সমাজ সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রেখে শিশুর যে মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়, সে কথাটাই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলতে চেয়েছেন।
‘মুখোশ ও মুখশ্রী’
‘মুখোশধারী’ মানুষ বলে যে আমরা স্লোগান তুলি, এ লেখায় তা বোঝাটা আরও সহজ হলো। ‘স্টাইল’ ও ‘ফ্যাশনের’ পরিষ্কার একটি পার্থক্য টেনেছে এ প্রবন্ধটি। কয়েকমাস আগে যতীন স্যারের কাছে এ বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়েছিলাম, এই প্রবন্ধটি পড়ে তা আরও স্পষ্ট হলো।
‘স্টাইল’ মানুষের জীবনের অংশ, কিন্তু ‘ফ্যাশন’ আরোপিত। ‘ফ্যাশন’ পুঁজিবাদী সমাজ শেখায়, আর ‘স্টাইল’ শেখায় আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্য। যেমন ছোট্ট উদাহরণ–আমি চুল ছোট রাখবো, প্যান্ট–শার্ট পরবো–এটা যদি আমার পোশাকীয় ‘স্টাইল’ হয়, এটাকে মেনে নিতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়! কিন্তু এই পোশাককে যখন আমি ‘ফ্যাশন’ হিসেবে, কাউকে দেখানোর জন্য, নিজের কোনো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না থাকা সত্ত্বেও পরবো, তখন তা ‘ফ্যাশন’। যে ফ্যাশন মানুষের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। যে ফ্যাশন ‘মানুষ’ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষের চিন্তাশক্তিকে গ্রাস করে–পুঁজিবাদী চিন্তাকে বিকশিত করে।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, ‘ফ্যাশন থাকছে, এবং থাকবেও, যতদিন না তার সামাজিক–সাংস্কৃতিক–অর্থনৈতিক প্রজনন ও লাল–ভূমিটি বিনষ্ট হচ্ছে। ফ্যাশনের মধ্যে যে এক ধরনের বুর্জোয়া চিন্তা–চেতনার ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ–ধারার সংবাদ আছে সেটি কেউ অস্বীকার করবেন না, কিন্তু প্রয়োজন তো বুর্জোয়া ফ্যাশনের নয়, প্রয়োজন বরঞ্চ বুর্জোয়া স্টাইলের, প্রয়োজন বুর্জোয়া স্টাইলকেও পার হয়ে যাবার, একটি সর্বজনীন, এক কথায় সমাজতান্ত্রিক, স্টাইল গড়ে তোলার। কেননা সেখানে এবং কেবলমাত্র সেখানেই, আছে আমাদের মুক্তি। ফ্যাশন সেই স্টাইল গড়তে বাধা দেয়–অপব্যয়ের মধ্য দিয়ে, বাধা দেয় বশ্যতা প্রচারের মধ্যদিয়ে। এ–বশ্যতা আবার ছদ্মবেশ ধরেছে বিদ্রোহের, সেই জন্যেও এ আরো বেশি ক্ষতিকর, কেননা সে আরো বেশি কৌশলী, কুশলী।
‘অনেক রকম মুখোশ আছে সমাজে। মুখোশ মানুষ তখনি পরে যখন ভয় পায় আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ হতে। যখন মতলব থাকে ভেতরে; যখন লজ্জা থাকে মনে, লজ্জা না–বলে অপরাধবোধ বলাই বুঝি সঙ্গত। এই তিন কারণের তিনটিই এক সঙ্গে থাকাও অসম্ভব নয়, আবার থাকতে পারে তারা আলাদা আলাদা হয়ে। আমাদের নানাবিধ সামাজিক মুখোশের মধ্য ফ্যাশন একটি।
‘মুখোশ মুখশ্রীর জন্মশত্রু। বাংলাদেশের মুখের যে অমন হতশ্রী তার পেছনে মুখোশের কারসাজি নেই কে বলবে। করুণ সে ঘটনা, অত্যন্ত আনন্দবিহীন।’
উল্লিখিত আলোচনা থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা, তাই এ প্রসঙ্গে আমার আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে একেবারেই নেই। তবে জানার এবং বোঝার কোনো শেষ নেই। সে কথাটিকে গুরুত্ব দিয়েই ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’ সম্পর্কে লেখাটি শেষ করছি।
আমাদের লড়াইটা শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য আরও জোরদার হোক, এ কাজে ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’ কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতেই পারে বলে মনে করি!